২০২৪ : ডেঙ্গুতে আক্রান্ত জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকির বছর
ড. মিহির কুমার রায় । সূত্র : ভোরের কাগজ, ০৭ জানুয়ারি ২০২৫
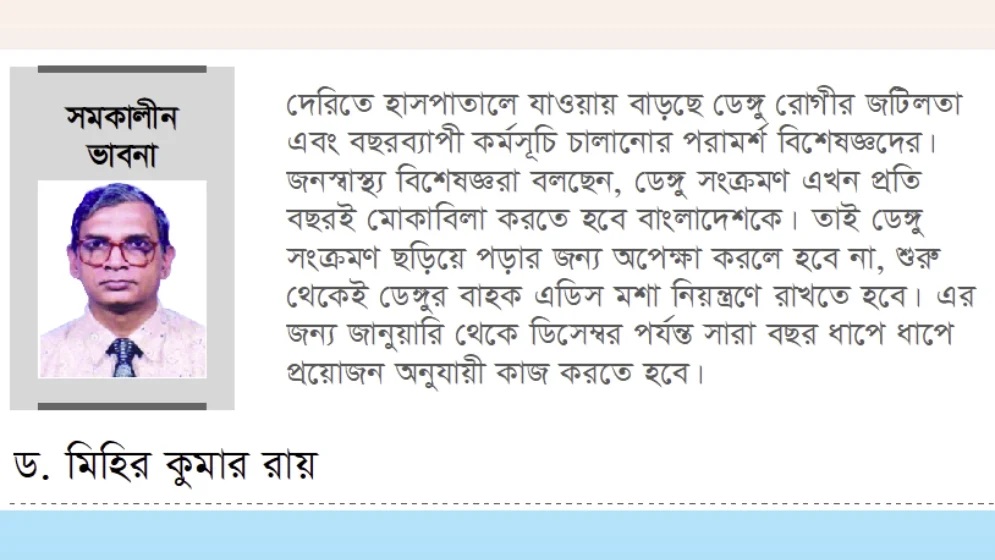
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী, এ বছর ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে যাদের হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিতে হয়েছে তাদের মধ্যে মৃত্যুর হার শূন্য দশমিক ৫৭ শতাংশ। ডেঙ্গুতে আক্রান্তদের মধ্যে চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হওয়ার হার ৯৮ দশমিক ৮৪ শতাংশ। আর বছরের শেষ দিনেও ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৫৯৯ জন। সংক্ষেপে বলা যায় এক নজরে ডেঙ্গু পরিস্থিতি (২০২৪) : বছরজুড়ে আক্রান্ত ১ লাখ ১ হাজার ২১৪, মৃত্যুবরণ করেছেন ৫৭৫, সুস্থ হয়েছেন ১ লাখ ৪০, আক্রান্ত ৬৩ দশমিক ১ শতাংশ পুরুষ ও মহিলা ৩৬ দশমিক ৯৯ শতাংশ, মৃত্যু ৫১ দশমিক ১ শতাংশ নারী ও পুরুষ ৪৮ দশমিক ৯৯ শতাংশ ইত্যাদি।
জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ডেঙ্গু সংক্রমণ এখন প্রতিবছরই মোকাবিলা করতে হবে বাংলাদেশকে। তাই ডেঙ্গু সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার জন্য অপেক্ষা করলে হবে না, শুরু থেকেই ডেঙ্গুর বাহক এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। এর জন্য কাজ জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সারা বছর ধাপে ধাপে প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ করতে হবে। পাশাপাশি চিকুনগুনিয়া ও জিকা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হওয়ায় আরো বেশি সতর্ক হতে হবে।
এবার আসা যাক বছরজুড়ে ডেঙ্গু সংক্রমণের চিত্র; যেখানে পাওয়া যায় ২০২৩ সালের শেষের দিকে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী শনাক্ত ও মৃত্যুর যে ঊর্ধ্বমুখী চিত্র দেখা যায়, তার ধারাবাহিকতা বজায় ছিল চলতি বছরের জানুয়ারিতেও। বছরের শুরুর এই মাসে ১ হাজার ৫৫ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। তাদের মধ্যে মৃত্যু হয় ১৪ জনের। ফেব্রুয়ারি মাস থেকে এ সংখ্যা কমে আসতে থাকে। এ মাসে ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হন ৩৩৯ জন, মৃত্যু হয় তিনজনের। মার্চে দেশে ৩১১ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়, মৃত্যু হয় পাঁচজনের।
এপ্রিলে ৫০৪ জন, মে মাসে ৬৪৪ জন ও জুনে ৭৯৮ জন ডেঙ্গু রোগী বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি হন। এর মধ্যে এপ্রিলে দুজন, মে মাসে ১২ জন ও জুনে আটজনের মৃত্যু হয়। জুলাই মাস থেকে বাড়তে থাকে ডেঙ্গু রোগী। জুনের তুলনায় এ মাসে ডেঙ্গু রোগী ছিল প্রায় সাড়ে তিনগুণ। সব মিলিয়ে জুলাইয়ে ডেঙ্গু রোগী শনাক্ত হন ২ হাজার ৬৬৯ জন। আগস্টে সে সংখ্যা আরো বেড়ে দাঁড়ায় ৬ হাজার ৫২১ জনে। সেপ্টেম্বরে আরো প্রায় তিনগুণ বেড়ে রোগী হয় ১৮ হাজার ৯৭ জন। এর মধ্যে জুলাইয়ে ১২ জন, আগস্টে ২৭ জন ও সেপ্টেম্বরে ডেঙ্গু আক্রান্ত ৮৭ জনের মৃত্যু হয়।
এ বছর ডেঙ্গু সংক্রমণ চূড়ান্ত আকার ধারণ করে অক্টোবরে। এ মাসে বছরের সর্বোচ্চ ৩০ হাজার ৮৭৯ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী হাসপাতালে ভর্তি হন। এর মাঝে ১৩৫ জনের মৃত্যু হয়। নভেম্বরেও ডেঙ্গু সংক্রমণ ছিল কাছাকাছি- ২৯ হাজার ৬৫২ জন। তবে এ মাসে আবার বছরের সর্বোচ্চ ১৭৩ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মারা যান। বছরের শেষ মাস ডিসেম্বরে সংক্রমণ কিছুটা কমে এসেছে। এ মাসে বিভিন্ন হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হয়েছেন ৯ হাজার ৭৪৫ জন। এ মাসে ৮৭ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।
তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, ডেঙ্গুতে মৃত প্রতি ৯ জনের একজন শিশু। এখানে উল্লেখ্য, দেশে এ বছর ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৫৭৫ জনের। এর মধ্যে ৬৪ জনের বয়স ১৫ বছরের নিচে। অর্থাৎ চলতি বছর ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে ৮ দশমিক ৯৮ শতাংশ বা প্রতি ৯ জনের মধ্যে একজন ১৫ বছরের কম বয়সি শিশু। এর মধ্যে শূন্য থেকে পাঁচ বছর বয়সিদের মধ্যে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৫ হাজার ৬১৫ জন। এ বয়সিদের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ২৬ জনের। ৬ থেকে ১০ বছর বয়সিদের মধ্যে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৪ হাজার ৮৬১ জন, মৃত্যু ১৪ জনের।
আর ১১ থেকে ১৫ বছর বয়সিদের মধ্যে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয় ৬ হাজার ১০৬ জন, মৃত্যু হয় ছয়জনের। ডেঙ্গুতে আক্রান্ত বেশি পুরুষ, মৃত্যু বেশি নারীর। এ বছর ডেঙ্গু আক্রান্তদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৬৩ হাজার ৮৮৬ জন, বিপরীতে নারীর সংখ্যা ৩৭ হাজার ৩২৮ জন। অর্থাৎ মোট ডেঙ্গু আক্রান্তদের মধ্যে ৬৩ দশমিক ১ শতাংশ পুরুষ, ৩৬ দশমিক ৯ শতাংশ নারী। সে হিসাবে ডেঙ্গু আক্রান্ত পুরুষের সংখ্যা ডেঙ্গু আক্রান্ত নারীর দেড় গুণেরও বেশি। অন্যদিকে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বেশি হয়েছে নারীদের। সারা বছরের হিসাব বলছে, ডেঙ্গুতে যারা মারা গেছেন তাদের মধ্যে নারী ২৯৪ জন, পুরুষ ২৮১ জন।
অর্থাৎ ডেঙ্গুতে যারা মারা গেছেন তাদের ৫১ দশমিক ১ শতাংশ নারী, ৪৮ দশমিক ৯ শতাংশ পুরুষ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সাধারণভাবে দেশে নারীদের অসুস্থতাকে হালকা করে দেখার যে প্রবণতা রয়েছে, ডেঙ্গু আক্রান্ত নারীদের ক্ষেত্রেও একই ধরনের ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে চিকিৎসা প্রক্রিয়া শুরু করতে দেরি হওয়ার কারণে নারীদের মধ্যে মৃত্যুর হার বেশি হতে পারে। দেরিতে হাসপাতালে যাওয়ায় বাড়ছে ডেঙ্গু রোগীর জটিলতা এবং বছরব্যাপী কর্মসূচি চালানোর পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ডেঙ্গু সংক্রমণ এখন প্রতিবছরই মোকাবিলা করতে হবে বাংলাদেশকে।
তাই ডেঙ্গু সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার জন্য অপেক্ষা করলে হবে না, শুরু থেকেই ডেঙ্গুর বাহক এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। এর কাজ জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সারা বছর ধাপে ধাপে প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ করতে হবে। পাশাপাশি চিকুনগুনিয়া ও জিকা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হওয়ায় আরো বেশি সতর্ক হতে হবে। তাই প্রথমত, চিকিৎসক গবেষকদের যা আছে তা নীতিনির্ধারকদের কাছে তুলে ধরা, বিশেষত দেশের দুটি সিটি করপোরেশনসহ অন্যান্য করপোরেশনের স্বাস্থ্য শাখাগুলোতে যাতে করে এসব পরিস্থিতির মোকাবিলা আগাম নেয়ার সুযোগে থাকে; দ্বিতীয়ত, বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলায় যারা আক্রান্ত হয়েছেন তাদের সঠিক সেবা দিয়ে সুস্থ করে তোলা আর যারা সুস্থ অবস্থায় আক্রান্তদের মধ্যে রয়েছেন তাদের আত্মরক্ষার পথ হিসেবে বাসন্থান কিংবা কর্মস্থান পরিষ্কার রাখা, মশা নিধনের জন্য মশানাশক ওষুধ ছিটানো, বাসা কিংবা অফিসের আবর্জনার স্থানে পানির ব্যবহার না করা ও সর্বোপরি ধর্মীয় অনুশাসনের ভিত্তিতে জীবনকে পরিচালিত করা; তৃতীয়ত, ডেঙ্গু মশা নিধনকারী প্রতিষ্ঠানে বাজেটের সর্বোচ্চ ব্যবহার।
কারণ প্রায়ই এই অভিযোগটি আসে যে সব উপকরণ বিশেষত মানসম্মত ওষুধ, যন্ত্রপাতি, প্রশিক্ষিত জনবল ও সময় উপযোগী আগাম পদক্ষেপ গ্রহণের অধিক অভিযোগ রয়েছে, যা প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে জাতি পেয়ে থাকে। কিন্তু তারপরও অবস্থার কোনো পরিবর্তন লক্ষণ দৃশ্যত চোখে পড়ে না; যার কারণে মহামান্য হাইকোর্টকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে হস্তক্ষেপ করতে হয়। এর সমাধান কখন কীভাবে হবে তা বর্তমানে আলাপচারিতায় কতটুকু সম্ভব হবে তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। যার অবসান জরুরি; চতুর্থত, আরো একটি কথা (গুজব না সত্য) শোনা যাচ্ছে সে মশার কাজ মশা করছে, তাই ডেঙ্গু রোগের এই ভাইরাস নাকি বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে; যাতে মশা না কামড়ালেও ডেঙ্গু হতে পারে।
এখন এই গুজবের সত্যটা কতটুকু, যা নিরসন করবে কে? অবশ্যই স্বাস্থ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশেষত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা ডেঙ্গু বিষয়ে অতীতের গবেষণার ফলাফল যদি থাকে তার ভিত্তিতে কী প্রয়োগিক কর্মসূচি নেয়া যায় এ ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দেবেন। আর যদি কোনো গবেষক না থাকে তবে প্রাধিকার ভিত্তিতে ডেঙ্গুর ওপর গবেষণা করার দাবি রইল। প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা পরিকল্পনায় দেশের অগণিত চিকিৎসক যারা স্নাতকোত্তর পর্যায়ে (এমএস/ এমডি/ এফসিপিস/ পিএইডি) গবেষণারত তাদের ডেঙ্গু বিষয়টিকে গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে বাছাই করা উচিত; পঞ্চমত, ষড়ঋতুর দেশের বর্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ঋতু, যা আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে বিস্তৃত। এটি সবাই জানেন যে, এই বর্ষাতেই বৃষ্টির কারণে ডেঙ্গুর প্রভাবটি বেড়ে যায়। কিন্তু যারা নিয়ন্ত্রক সংস্থা তাদের বাজেট থাকলেও পরিকল্পনামাফিক এর ব্যয় করার যে অনুশীলন তা না করার কারণে কল্পনামাফিক এর ব্যয় করার যে অনুশীলন তা না করার কারণে সঠিক কাজটি সঠিক সময়ে হয় না বিধায় যাও হয় তা মানসম্মত নয়; যা নিয়ে অভিযোগের পাহাড় রয়েছে।
এখন কী ওষুধ ব্যবহার করা হবে, কোন দেশ থেকে ওষুধ আসবে, কোন পদ্ধতিতে টেন্ডার হবে, কীভাবে হবে ইত্যাদি একটি নির্ধারিত ছকে হওয়ার কথা থাকলেও যেসব কর্মকর্তা এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত তাদের সজাগতা কিংবা অসাধুতার কারণে বিঘিœত হয় মূল কাজ আর ক্ষতিগ্রস্ত হয় সমাজ; যা দেশের প্রতিষ্ঠানিক দুর্বলতার একটি সাধারণ চিত্র। এসব বিষয় প্রশাসনিকভাবে মোকাবিলা করতে হবে; ষষ্ঠত, স্বাস্থ্যসেবা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্য প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয় না থাকায় জাতীয় স্বাস্থ্য ঝুঁকি যেমন ডেঙ্গুর মতো বিষয়গুলো যখন ব্যাপকভাবে দেখা দেয় তখন এরই নিয়ন্ত্রণ অনেক ক্ষেত্রে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। যার ফলে জনজীবন বিপন্ন হয়, যা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রায়ই ঘটছে। তার একটি সমাধান খুঁজে বের করা দরকার; সপ্তমত, স্বাস্থ্য বাজেট নিয়ে প্রায়ই সমালোচনা শোনা যায়, যা জাতীয় বাজেটের মাত্র ২ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, যা দিয়ে স্বাস্থসেবা উপকরণ (ওষুধ, যন্ত্রপাতি হাসপাতাল ব্যবস্থপনা) ও স্বাস্থ্য গবেষণা/প্রশিক্ষণের খরচ মেটাতে হয়। তার মধ্যে আবার ডেঙ্গুজনিত রোগ, বন্যাজনিত রোগ, মৌসুমি রোগ ইত্যাদি মোকাবিলার জন্য তেমন কোনো বাজেট বরাদ্দ থাকে না।
তা হলে স্বাস্থ্যসেবার বিনিময়ে প্রাপ্ত ফি (যদিও সরকারি হাসপাতালে কম)-এর টাকা কি বাজেটের ঘাটতি পূরণে সহায়তা করে না? গতানুগতিকভাবেই বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে রাষ্ট্রীয় ব্যয় কম, যা গত এক দশক ধরে বাংলাদেশ গড়ে জিডিপির মাত্র ২ শতাংশ বা তারও কম আর বাজেটের মাত্র ৫ শতাংশ ব্যয় করছে, যা দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বনিম্ন। উন্নত দেশগুলোতে এই হার ১০ থেকে প্রায় ২০ শতাংশ। মাথাপিছু স্বাস্থ্য ব্যয়ের ক্ষেত্রেও দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ সবচেয়ে পিছিয়ে। দক্ষিণ এশিয়ার গড় মাথাপিছু স্বাস্থ্য ব্যয় বাংলাদেশ থেকে ৪ গুণেরও বেশি। জানা গেছে, বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে এবার মোট বরাদ্দ ৩৮ হাজার ৫০ কোটি টাকা। আগের বছর যা ছিল ৩৬ হাজার ৮৬৪ কোটি টাকা। এ হিসাবে টাকার অঙ্কে বরাদ্দ বেড়েছে ১ হাজার ১৮৬ কোটি টাকা। শতকরা হিসাবে যা ৩ শতাংশ।
কিন্তু মোট বাজেটের বিবেচনায় বরাদ্দ কমেছে। এবার বাজেটের আকার ৭ লাখ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ এর ৫ শতাংশ। আগের বছর যা ৫ দশমিক ৪০ শতাংশ ছিল। বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) বলেছে, ২০২৩-২৪ সালে মোট উন্নয়ন বাজেটে স্বাস্থ্য খাতের অংশ ৪১ শতাংশ। আগের বছর যা ছিল ৫১ শতাংশ। এ ছাড়া স্বাস্থ্য খাতে এবার বরাদ্দ জিডিপির শূন্য দশমিক ৭৬ শতাংশ। সিপিডি মনে করে স্বাস্থ্য খাতে এই বরাদ্দ একেবারেই যৌক্তিক নয়। কারণ বাংলাদেশে স্বাস্থ্য খাতে জিডিপির ৫ শতাংশ বরাদ্দ হওয়া উচিত।
সর্বশেষে বলা যায়- সরকার আগামীর বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করছে, যেখানে প্রতিটি জনশক্তি স্মার্ট হবে, সবাই প্রতিটি কাজ অনলাইনে করতে শিখবে, ইকোনমি হবে ই-ইকোনমি, যাতে সম্পূর্ণ অর্থ ব্যবস্থাপনা ডিজিটাল ডিভাইসে করতে হবে, আমাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মযোগ্যতা সবকিছুই ই-গভর্ন্যান্সের মাধ্যমে হবে, ই-এডুকেশন, ই-হেলথসহ সব কিছুতেই ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করা হবে এবং ২০৪১ সাল নাগাদ এগুলো করা সম্ভব হবে এবং সেটা মাথায় রেখেই কাজ চলছে, কিন্তু বাজেটে এর তেমন কোনো প্রতিফলন সেভাবে নেই।
সরকারের বক্তব্য হলো বাজেটের টাকা উন্নয়ন খাতে খরচ করার মতো সক্ষমতা স্বাস্থ্য দপ্তরের নেই। তাই সরকারি চিকিৎসকদের ব্যবসা বন্ধ করে সেবায় মনোনিবেশ করতে হবে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে অধিক সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। তা হলেই দেশের রোগীদের আর অর্থ খরচ করে প্রতিবেশি দেশ ভারতে গমন করতে হবে না এবং দেশের বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে। মনে রাখতে হবে সুস্থ জাতি মানেই সমৃদ্ধ বাংলাদেশ।
ড. মিহির কুমার রায় : কৃষি অর্থনীতিবিদ ও গবেষক।