আরব-ইসরায়েল সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের কারিগর
ইমাদ কে হার্ব | সূত্র : দেশ রূপান্তর, ০৫ জানুয়ারি ২০২৫
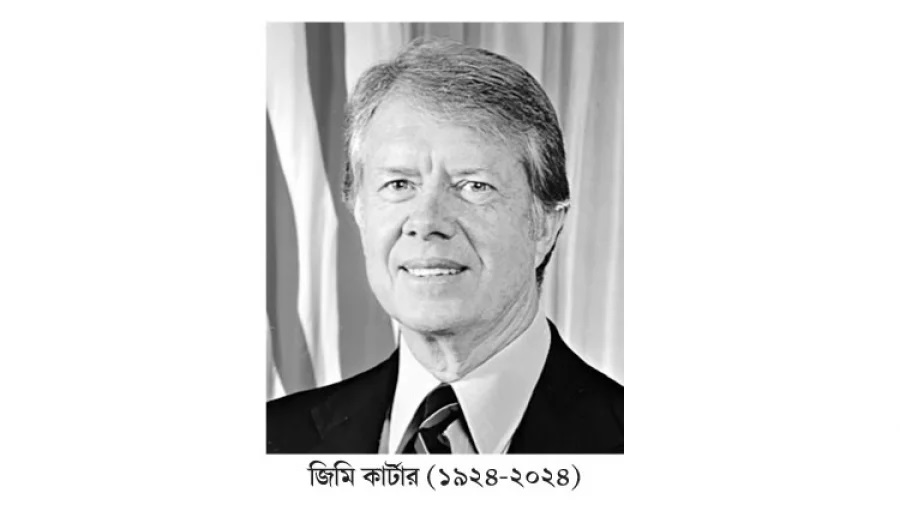
সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার ২৯ ডিসেম্বর ১০০ বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ৩৯তম প্রেসিডেন্ট এবং একজন নাগরিক হিসেবে কার্টার শান্তি প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্র এবং মানবিক ও পরিবেশগত বিভিন্ন উদ্যোগের সমর্থক ছিলেন। তবে মধ্যপ্রাচ্যে তিনি পরিচিত হয়ে থাকবেন আরব-ইসরায়েল সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের জনক হিসেবে। ১৯৭৭ সালে প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেওয়ার পর, মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে কার্টার প্রথম কোনো আরব দেশের সঙ্গে ইসরায়েলের সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের চুক্তির নেপথ্য কারিগর হয়ে ওঠেন।
তিনি আনোয়ার সাদাত ও ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী মেনাহেম বেগিনকে ১৯৭৮ সালের ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি এবং ১৯৭৯ সালের মিসর-ইসরায়েল শান্তিচুক্তি সম্পাদনে সহায়তা করেন, যা দুদেশের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলা বৈরিতা ও যুদ্ধ আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্তি করে। তবে গত চার দশকের ঘটনাপ্রবাহ থেকে দেখা গেছে, এই চুক্তি কিংবা শান্তিচুক্তি মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ও ন্যায়বিচার আনতে ব্যর্থ হয়েছে। ইসরায়েল এখনো পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেম দখল করে রেখেছে এবং গাজা উপত্যকায় যুদ্ধ নামের গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে। ফিলিস্তিনিরা আজও এমন একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি, যার রাজধানী হবে জেরুজালেম। অধিকাংশ আরব জনগণ এখনো ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দিতে কিংবা ইসরায়েলি জনগণের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক রাখতে প্রস্তুত নয়।
কার্টারের মধ্যস্থতায় স্বাক্ষরিত ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি ছিল আরব রাষ্ট্রগুলোর জন্য ফিলিস্তিনি স্বাধিকার আন্দোলনের প্রতি তাদের ঐতিহ্যবাহী সমর্থন থেকে ধীরে ধীরে সরে আসার সূচনা, যদিও সেটা কখনই প্রকাশ্যে বোঝা যায়নি। এটি যুক্তরাষ্ট্রের সেই দীর্ঘমেয়াদি কৌশলেরও অংশ ছিল, যা ফিলিস্তিনি জাতীয় আকাক্সক্ষাকে ধূলিসাৎ করার জন্য পরিকল্পিত। ইতিহাস জিমি কার্টারকে একজন মানবতাবাদী ও শান্তির দূত হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও তার নেতৃত্ব মধ্যপ্রাচ্যে এক গভীর ও বহুমাত্রিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল।
ক্যাম্প ডেভিডের পরে : ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি ছিল মূলত মিসর-ইসরায়েল পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠার একটি রোডম্যাপ। এতে মিসরের পক্ষ থেকে ইসরায়েলকে পূর্ণ স্বীকৃতি এবং আরব অর্থনৈতিক বয়কট থেকে মিসরের বেরিয়ে আসার পথ প্রশস্ত করা হয়েছিল। তবে এটি ফিলিস্তিনিদের নিয়েও কিছু প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করেছিল, যার ভাষা চুক্তির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। চুক্তিতে অধিকৃত অঞ্চলের বাসিন্দাদের জন্য ‘স্বায়ত্তশাসন’ প্রদানের পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করা হয়, মনে হয় যেন ফিলিস্তিনিরা পশ্চিম তীর ও গাজায় বহিরাগত বাসিন্দা।
সে সময় যুক্তরাষ্ট্র ফিলিস্তিনি জনগণের একমাত্র বৈধ প্রতিনিধি হিসেবে প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনকে (পিএলও) স্বীকৃতি দেয়নি। ফলে চুক্তিতে ‘স্বশাসিত কর্র্তৃপক্ষ’ গঠনের জন্য একটি নির্বাচনের আহ্বান জানানো হয়েছিল। তবে এই স্বায়ত্তশাসন এবং নির্বাচিত কর্র্তৃপক্ষকে ইসরায়েল, মিসর ও জর্দানের তত্ত্বাবধানে রাখা হবে বলে উল্লেখ করা হয়, যা স্পষ্টতই ফিলিস্তিনিদের স্বাধীন জাতীয় সরকার গঠনের অধিকারের পরিপন্থি।
১৯৮০-এর দশক জুড়ে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনে ইসরায়েলি আপত্তির কারণে ফিলিস্তিনিদের আরব-ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিন-ইসরায়েল বিরোধ মীমাংসার শান্তি পরিকল্পনায় ভূমিকা রাখতে বাধা দেওয়া হয়। কিন্তু ১৯৮৭ সালে প্রথম ইন্তিফাদা এবং ১৯৮৮ সালে জর্দান পশ্চিম তীর থেকে তার দাবি প্রত্যাহারের পর স্পষ্ট হয় যে, ফিলিস্তিনিদের শান্তি আলোচনা থেকে আর উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। কিন্তু তারপরও দেখা যায় যে, ১৯৯১ সালের মাদ্রিদ সম্মেলনে ফিলিস্তিনিরা জর্দানের প্রতিনিধি দলের অংশ হিসেবে উপস্থিত হতে বাধ্য হয়েছে, অর্থাৎ তাদের জাতীয় পরিচিতিকে উপেক্ষা করা হয়।
যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পরিচালিত অন্যান্য তথাকথিত ‘শান্তি প্রক্রিয়া’র মতো মাদ্রিদের পথও অচলাবস্থার মধ্যে পড়ে। ইসরায়েল ফিলিস্তিনিদের জাতীয় অধিকারের দাবি উপেক্ষা করে এবং তার দখলদারি শেষ করার আলোচনা প্রত্যাখ্যান করে। তবে ১৯৯২ সালের ইসরায়েলি নির্বাচনে লেবার পার্টি ক্ষমতায় আসার পর যুক্তরাষ্ট্র পিএলও ও ইসরায়েলের মধ্যে অসলো চুক্তি করাতে সক্ষম হয়। এই চুক্তির মাধ্যমে ফিলিস্তিনি ন্যাশনাল অথরিটি (পিএনএ) গঠিত হয়।
তবে পিএলওকে ইসরায়েলের অস্তিত্ব স্বীকার করতে বাধ্য করা হয়, যদিও ইসরায়েলের কাছ থেকে ফিলিস্তিনিদের অভিযোগ এবং জাতীয় আকাক্সক্ষার স্বীকৃতি পাওয়ার কোনো আলামতই দেখা যায়নি। মিসরের পর দ্বিতীয় আরব রাষ্ট্র হিসেবে ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য জর্দানকেও ইসরায়েলের সঙ্গে একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করতে হয়। তথাপি জর্দান চেষ্টা করেছিল অন্তত জেরুজালেমের ধর্মীয় স্থাপনাগুলোর অভিভাবকত্ব ধরে রাখতে। যদিও তা শুধু কাগজেই সীমাবদ্ধ বলে মনে হয়, কেননা, বর্তমানে মসজিদে ইসরায়েলি কর্র্তৃপক্ষের ক্রমাগত চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে।
আব্রাহাম চুক্তি : ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির প্রক্রিয়া থেকে শুরু হওয়া তথাকথিত ‘শান্তি প্রক্রিয়া’র ধারাবাহিকতায় যুক্তরাষ্ট্র আরব দেশগুলোকে বোঝানো শুরু করে যে, ফিলিস্তিনিদের স্বার্থ থেকে তাদের নিজেদের স্বার্থ আলাদা। তারা ক্রমাগত আরবদের নিজস্ব স্বার্থ ভাবনায় উৎসাহিত করতে থাকে। আরব রাষ্ট্রপ্রধানরাও ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় ফিলিস্তিনকে ভাবতে থাকে জখমের কাঁটা। ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় এলে তার প্রশাসনের অধীনে এই প্রক্রিয়াটি পূর্ণমাত্রায় একটি প্রচারণায় রূপ নেয়। ট্রাম্প এবং তার সহযোগীরা ইসরায়েলের প্রতি ঐতিহ্যগত মার্কিন পক্ষপাতিত্বকে আরও সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন।
২০২০ সালে ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় তথাকথিত ‘আব্রাহাম চুক্তি’ স্বাক্ষরিত হয়, যা ইসরায়েলের সঙ্গে সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন ও মরক্কোর সম্পর্ক স্বাভাবিক করে। এর পরের বছর সুদানও এই চুক্তিতে যোগ দেয়। যদিও অংশগ্রহণকারী আরব রাষ্ট্রগুলো দাবি করেছিল যে, ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ ফিলিস্তিনিদের জীবনমান উন্নত করতে সাহায্য করবে এবং এটি তাদের ত্যাগ করার মতো পদক্ষেপ নয়, প্রকৃতপক্ষে তারা প্রত্যেকেই ফিলিস্তিনি স্বার্থের প্রতি কোনো গুরুত্ব না দিয়েই ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেওয়ার বিনিময়ে নিজ নিজ স্বার্থে কিছু না কিছু পেয়েছিল। সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইসরায়েলের সম্পর্ক সবচেয়ে দ্রুত ও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। দুই দেশ সামরিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক দ্রুত সম্প্রসারিত করেছে।
বাহরাইন চেয়েছে ইরানের আক্রমণাত্মক অবস্থানের বিরুদ্ধে সুরক্ষার জন্য ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক ব্যবহার করতে। মরক্কো তার বহু প্রত্যাশিত মার্কিন স্বীকৃতি পেয়েছে পশ্চিম সাহারার ওপর সার্বভৌমত্বের ওপর। আর সুদান পেরেছে যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসবাদ সমর্থনকারী রাষ্ট্রের তালিকা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে। আব্রাহাম চুক্তি আসলে এমন একটি লেনদেন, যা ফিলিস্তিনের অধিকার জলাঞ্জলি দেওয়ার বিনিময়ে স্বাক্ষরকারী দেশগুলোর স্বার্থ হাসিল করার সুযোগ করে দিয়েছে এই চুক্তি ইসরায়েলকে তার বর্ণবৈষম্য নীতি আরও গভীর করতে এবং ফিলিস্তিনি ভূমিতে তার দখলদারি আরও জোরালো করতে সহায়তা করেছে। ইসরায়েলে আরও বেশি সীমানা বাড়াতে পেরেছে এবং ফিলিস্তিনকে ঠেলে দিয়েছে আরও অন্ধকারে।
ট্রাম্পের আসন্ন প্রশাসনে আরব দেশগুলোর সঙ্গে ইসরায়েলের সম্পর্ক আরও সম্প্রসারণের স্পষ্ট ইচ্ছা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সৌদি আরবকে এই মানচিত্রে যুক্ত করার পরিকল্পনা দেখা যাচ্ছে। আগের স্বাভাবিকীকরণ চুক্তিগুলোর মতোই, এই নতুন চুক্তিগুলো থেকেও ফিলিস্তিনিরা তেমন কোনো সুফল পাওয়ার আশা করতে পারবে, এমন কোনো সম্ভাবনা খুঁজে বের করার চেষ্টাই হবে বাতুলতা।
মনোভাবের ইতিবাচক পরিবর্তন : প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব শেষ করার পরও জিমি কার্টার ইসরায়েল-ফিলিস্তিন শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। তবে এই প্রক্রিয়ায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেখতে পান যে, যুক্তরাষ্ট্রের ইসরায়েলপ্রীতিমূলক নীতিই আসলে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে বাধা সৃষ্টি করছে। তিনি উপলব্ধি করেন, যুক্তরাষ্ট্রের এই একচোখা সমর্থন ইসরায়েলকে আরও আগ্রাসী করে তুলেছে এবং ফিলিস্তিনিদের অধিকারের প্রতি অন্যায় আচরণকে স্বাভাবিক করে তুলেছে। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ২০০৭ সালে কার্টার তার বিখ্যাত বই চধষবংঃরহব: চবধপব ঘড়ঃ অঢ়ধৎঃযবরফ প্রকাশ করেন। বইয়ে তিনি সাহসিকতার সঙ্গে দাবি করেন যে, অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ইসরায়েলের নীতি ও কর্মকাণ্ড বর্ণবৈষম্যের অপরাধের সমান।
কার্টারের এই দৃষ্টিভঙ্গি মার্কিন রাজনীতির প্রচলিত মূলধারার অবস্থানের বিপরীতে ছিল। তখনকার অধিকাংশ মার্কিন রাজনীতিবিদ এবং জনমত প্রভাবিতকারী ব্যক্তিত্ব ইসরায়েলের নীতিকে সমর্থন করতেন বা সমালোচনা করতে ভয় পেতেন। কিন্তু কার্টার, তার নৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থান থেকে, ইসরায়েলের নীতিকে যথার্থ শব্দে চিহ্নিত করার সাহস দেখান। এই অবস্থান শুধু তার রাজনৈতিক জীবনেরই নয়, বরং পুরো বিশে^র সামনে মানবাধিকারের প্রতি তার দায়বদ্ধতার প্রমাণ। তার বইটি যুক্তরাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তুমুল আলোচনার জন্ম দেয় এবং ইসরায়েল-ফিলিস্তিন বিষয়ে নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে। এই অংশে মূলত কার্টারের প্রেসিডেন্ট-পরবর্তী জীবন এবং ইসরায়েল-ফিলিস্তিন বিষয়ে তার অবস্থানের পরিবর্তনের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। তার বর্ণবৈষম্য নীতির সমালোচনা এবং ফিলিস্তিনিদের অধিকারের পক্ষে অবস্থান তাকে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক অঙ্গনে এক অনন্য উচ্চতায় স্থান দিয়েছে।
আজ যখন মার্কিন জনগণ তার মৃত্যুতে শোকাহত এবং তার উত্তরাধিকারকে স্মরণ করছে, তখন ফিলিস্তিন বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিধ্বংসী নীতির দিকে ফিরে তাকানো জরুরি। গত চার দশকে, ইসরায়েলের দখলদারিত্ব আরও সহিংস হয়ে উঠেছে, যা মূলত যুক্তরাষ্ট্রের শর্তহীন সমর্থনের ফল। সময় এসেছে যুক্তরাষ্ট্রের ইসরায়েল-ফিলিস্তিন নীতিতে পরিবর্তন আনার। এটি এমন একটি পরিবর্তন, যা জিমি কার্টার তার জীবদ্দশায় দেখতে চেয়েছিলেন। গত চার দশক ধরে ইসরায়েলের দখলদারিত্ব ক্রমেই সহিংস হয়েছে, যা মূলত যুক্তরাষ্ট্রের নিঃশর্ত সমর্থনের ফসল। এখন এমন একটি নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন, যা ফিলিস্তিনিদের অধিকারকে যথাযথভাবে স্বীকৃতি দেয় এবং ইসরায়েলের অপরাধের জন্য তাদের দায়বদ্ধ করে।
আলজাজিরা থেকে ভাষান্তর : মনযূরুল হক
লেখক: গবেষণা ও বিশ্লেষণ বিভাগের পরিচালক, আরব সেন্টার ওয়াশিংটন ডিসি