বিদ্যমান সাংবিধানিক কাঠামোয় সংস্কার কতটা সম্ভব
সংবিধান সংস্কারের ক্ষেত্রে অনিবার্য জটিলতা ও সংকট আছে, যা এড়িয়ে যাওয়া নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সংঘর্ষ তৈরি করবে। বিদ্যমান সাংবিধানিক কাঠামোয় এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সম্ভব কি না, তা নিয়ে লিখেছেন- সৌমিত জয়দ্বীপ । সূত্র : প্রথম আলো, ২৭ জানুয়ারি ২০২৫
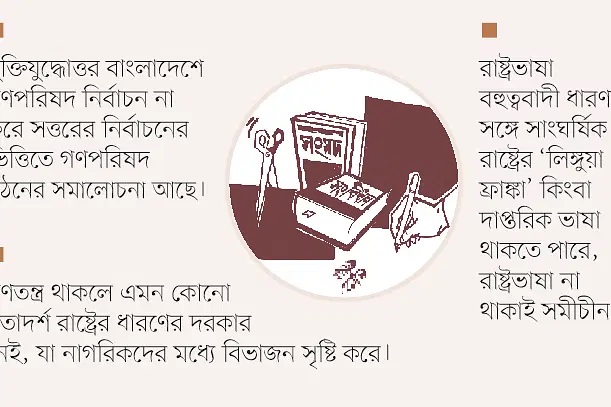
প্রয়াত সিরাজুল আলম খান ১৫ দফা প্রস্তাব দিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধের পরপরই। এগুলোর মধ্যে ফেডারেল রাষ্ট্রব্যবস্থা, জাতীয় সরকার, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ, প্রদেশভিত্তিক রাষ্ট্র গঠন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, স্বাধীন নির্বাচন কমিশন, নির্দলীয় রাষ্ট্রপতি-উপরাষ্ট্রপতিব্যবস্থা অন্যতম। বাহাত্তরের সংবিধানপ্রণেতারাসহ পরবর্তী কোনো সরকারই সেসব আমলে আনেনি।
আশার কথা, সেই ১৫ দফার অনেকগুলোর সঙ্গেই অন্তর্বর্তী সরকার–মনোনীত বেশ কয়েকটি সংস্কার কমিশনের বিভিন্ন প্রস্তাবের স্পিরিট মিলে যায়। গত ৫ আগস্টের পটপরিবর্তনের পর অন্তর্ভুক্তিমূলক, বৈষম্যহীন ও সুশাসনসমৃদ্ধ গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে নানা আলোচনা হয়েছে। ১৯৯০ সালের গণ-অভ্যুত্থানের পরও এ রকম একটি আকাঙ্ক্ষা ও সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যর্থতায় সেই সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়।
সংবিধান সংস্কার কমিশন সংবিধানের বর্তমান প্রস্তাবনাটি পরিমার্জন করে ১৯৭১ ও ২০২৪ সালের স্পিরিটের কথা উল্লেখ করেছে। আশ্চর্যের বিষয়, একাত্তর ও চব্বিশের মাঝে যে একটা নব্বই ঘটিয়ে স্বৈরাচারের পতনের মধ্য দিয়ে দেশকে একাত্তরের গণতান্ত্রিক স্পিরিটের পথে পরিচালিত করার অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছিল, সেটির গণকৃতিত্বকে কমিশন গ্রাহ্য করেনি।
নিঃসন্দেহে কমিশনগুলোর প্রস্তাবই চূড়ান্ত নয়। কিন্তু সংস্কার প্রস্তাব জনগণের সব স্তরের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারল কি না, সেটি আলোচনায় থাকা দরকার।
আদি সংবিধান, মূলনীতি ও সংস্কার প্রস্তাব
জনপরিসরে বাংলাদেশের ‘আদি সংবিধান’ বলতে ১৯৭২ সালের সংবিধানকে সাধারণভাবে (ও ভুলভাবে) গণ্য করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশের আদি সংবিধান আদতে ‘স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র’ বা ‘প্রোক্লেমেশন অব ইনডিপেনডেন্স’। বাহাত্তরের সংবিধান মুখ্যত প্রথম পূর্ণাঙ্গ সংবিধান, যার সম্বন্ধে অ্যান্থনি মাসকারেনহাস তাঁর বহুল আলোচিত বাংলাদেশ: আ লিগ্যাসি অব ব্লাড গ্রন্থে বলেছেন, ‘প্রশাসনিক ব্যর্থতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ এমন একটি সংবিধান প্রণয়ন করেছিল, যা নিয়ে যেকোনো দেশই গৌরব বোধ করতে পারে।’
■ মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে গণপরিষদ নির্বাচন না করে সত্তরের নির্বাচনের ভিত্তিতে গণপরিষদ গঠনের সমালোচনা আছে। ■ গণতন্ত্র থাকলে এমন কোনো মতাদর্শ রাষ্ট্রের ধারণের দরকার নেই, যা নাগরিকদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে। ■ রাষ্ট্রভাষা বহুত্ববাদী ধারণার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। রাষ্ট্রের ‘লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা’ কিংবা দাপ্তরিক ভাষা থাকতে পারে, রাষ্ট্রভাষা না থাকাই সমীচীন।
মাসকারেনহাস এই সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে ‘মাস্টারমাইন্ড’–এর তকমা দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। কিন্তু ইতিহাসের আশ্চর্য নিদান হলো, সারাটা জীবন গণতন্ত্রের জন্য জেল-জুলুম-হুলিয়া সহ্য করা সেই তিনিই তাঁর নেতৃত্বে প্রণীত সংবিধানকে পেছনে ফেলে চতুর্থ সংশোধনীর মধ্য দিয়ে বাকশাল প্রবর্তন করে সদ্য স্বাধীন দেশ থেকে গণতন্ত্রকে বিদায় জানালেন!
শেখ মুজিবের চিন্তার প্রতিফলন তো অবশ্যই সংবিধানে আছে। তবে এর আগেই মুজিব বাহিনী তথা বিএলএফের একাংশ ‘মুজিববাদ’কে ‘বিশ্বের তৃতীয় দর্শন’ হিসেবে প্রচারে এনেছিল। এর কেন্দ্রীয় চিন্তাজগতে ছিল গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র কায়েম, বামপন্থীদের শ্রেণিসংগ্রামের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র কায়েমের বিপরীতে। আর সঙ্গে থাকল ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তানের ‘জিঞ্জিরভেদী নীতি’ হিসেবে বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা।
বাহাত্তরের সংবিধানে এই চারটি যখন মূলনীতিতে অলংকৃত হলো, তখন খুব আড়ালে-আবডালে ব্রাত্য হয়ে গেল প্রবাসী সরকারের সেই লিখিত দলিলের (আদি সংবিধান) সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার। মানে মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল একটি সংগঠনের মতবাদ! ফলে আদি সংবিধান ও প্রথম পূর্ণাঙ্গ সংবিধান—এ দুটির মধ্যে জিইয়ে থাকল একটি নিমজ্জিত দ্বন্দ্ব।
বর্তমান সংবিধান সংস্কার কমিশন কি তাদের প্রস্তাবের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম দুই সংবিধানেরই সমন্বয় সাধন করল? আদিটি থেকে ‘সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার’ (ন্যায়বিচারের স্থলে সুবিচার) এবং প্রথম শাসনতন্ত্র থেকে ‘গণতন্ত্র’কে চয়ন করে নতুন করে শুধু সংযোজন করল ‘বহুত্ববাদ’। যদিও গণতন্ত্র থাকলে বাকি সবই বাগাড়ম্বর ও অপ্রয়োজনীয়, তথাপি ‘জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা’ পারস্পরিকভাবে দ্বান্দ্বিক হওয়ার পরও অটুট ছিল। এগুলো বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে, যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচনা-সমালোচনায় ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’।
ধর্মনিরপেক্ষতা, অসাম্প্রদায়িকতা, নাকি বহুত্ববাদ
সচেতন সমাজের ‘ধর্মনিরপেক্ষতার’ প্রতি উদারনৈতিক (লিবারেল) অবস্থান সাধুবাদযোগ্য হলেও সেটিকে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েও দেখা দরকার। লিবারেলরা (উদারপন্থী) একটি জানালা খোলা রেখে ঘরে হাওয়া ঢুকতে দেবেন, কিন্তু অপর দিকের জানালাটি বন্ধ থাকলে যে হাওয়া বের হতে পারবে না, সেটি চিন্তা করবেন না। এর একটি উদাহরণ হলো খোদ বঙ্গবন্ধুর মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে ‘বাঙালি’ হতে বলার প্রস্তাব। সংবিধানে মূলনীতির প্রশ্নে ‘বাঙালি জাতীয়তাবাদ’–এর বিরোধিতা করেছিলেন এম এন লারমা।
লিবারেলরা কি মনে করেন, এম এন লারমার প্রতি শেখ মুজিবের প্রস্তাবটি অসাম্প্রদায়িক ছিল? তাঁরা কি মানেন, ধর্মনিরপেক্ষতার চেয়ে অসাম্প্রদায়িকতার পরিসর অনেক বিস্তৃত? জাতি-ধর্ম-গোত্র-বর্ণ-শ্রেণি-লিঙ্গ-পেশা-ভাষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বৈষম্য ও আধিপত্যরোধ কি অসাম্প্রদায়িকতা ছাড়া সম্ভব? বাংলাদেশে যে উগ্র জাতিবাদী আধিপত্য আছে, আদিবাসীদের ওপর দীর্ঘকালের সাম্প্রদায়িক নিপীড়ন কি সেটারই বহিঃপ্রকাশ নয়?
সংবিধানের অন্যতম মূলনীতি হিসেবে ‘জাতীয়তাবাদ’, নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে ‘বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালি’ আর আদিবাসীরা ‘উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়’—এসব বিভাজনমূলক কথাবার্তা কি ধর্মনিরপেক্ষতা রোধ করতে পারে? অথচ ধর্মনিরপেক্ষতার চেয়েও গুরুতর প্রশ্ন হলো, বাহাত্তর কি চব্বিশ, অসাম্প্রদায়িকতা কোথায়?
আশ্চর্যই বটে, অসাম্প্রদায়িকের একটি অপ্রচলিত ইংরেজি অর্থ ‘লিবারেল’ হলেও বাংলাদেশের লিবারেলরা অসাম্প্রদায়িকতার সাংবিধানিক ভিত্তি চান না, ধর্মনিরপেক্ষতা চান!
আমরা মনে করি, গণতন্ত্র থাকলে এমন কোনো মতাদর্শ রাষ্ট্রের ধারণের দরকার নেই, যা নাগরিকদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে। বস্তুত, এ ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের সঙ্গে ‘সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার’ থাকাই যথেষ্ট। যদিও কমিশন সম্ভবত ‘অসাম্প্রদায়িকতা’র অর্থেই ‘সর্বজনীন ছাতা’ হিসেবে বহুত্ববাদ সংযুক্ত করেছে, যা সব মত-পথ-রথকে ধারণ করবে।
অবশ্য ‘বহুত্ববাদী’ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রধর্মের ব্যাপারে কিছু জানা না গেলেও বায়ান্নর ঐতিহাসিক উত্তরসূরি হিসেবে রাষ্ট্রভাষা বাংলা রাখা হয়েছে। আপাতনিরীহ হলেও সেটিও বহুত্ববাদী ধারণার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। রাষ্ট্রের ‘লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা’ কিংবা দাপ্তরিক ভাষা থাকতে পারে, রাষ্ট্রভাষা না থাকাই সমীচীন।
প্রদেশ ও উচ্চকক্ষের সম্পর্ক
বাংলাদেশকে প্রদেশে ভাগ করার প্রস্তাব করেছে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন। যদিও তারা স্বীকার করেছে, প্রস্তাবটি সংবিধান সংস্কারের সঙ্গে সম্পর্কিত। সংবিধান ও নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশন উভয়েই দ্বিকক্ষ আইনসভার প্রস্তাব করেছে। তবে তারা প্রদেশ প্রবর্তন তাদের প্রস্তাবে আনেনি। তাহলে কি প্রদেশের প্রতিনিধিত্ব ছাড়াই উচ্চকক্ষ গঠিত হবে?
পৃথিবীর অধিকাংশ দ্বিকক্ষবিশিষ্ট রাষ্ট্রেই প্রদেশের সঙ্গে উচ্চকক্ষের সম্পর্ক আছে। মূলত, প্রাদেশিক পরিষদের হাতে থাকে উচ্চকক্ষের প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষমতা। অনেক দেশে উচ্চকক্ষের নির্বাচন হয় সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতিতে এবং উচ্চকক্ষ কখনোই বিলুপ্ত হয় না।
সংবিধান সংস্কার কমিশন উভয় কক্ষেই প্রতি চার বছর পরপর নির্বাচনের প্রস্তাব করেছে। কমিশন বাংলাদেশের নিম্নকক্ষে (জাতীয় সংসদ) সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রত্যক্ষ ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচন বা ফার্স্ট পাস দ্য পোস্ট (এফপিটিপি) রেখে উচ্চকক্ষের (সিনেট) ক্ষেত্রে প্রপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন (পিআর) নির্বাচন প্রস্তাব করেছে। পিআরের ক্ষেত্রে কমিশন বলেছে, ‘কোনো রাজনৈতিক দলকে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতির ভিত্তিতে উচ্চকক্ষে প্রতিনিধিত্বের যোগ্য হতে হলে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের অন্তত ১ শতাংশ নিশ্চিত করতে হবে।’
উচ্চকক্ষে পিআরের কথা নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনও বলেছে, তবে তারা ৫০ শতাংশ করে দলীয় ও নির্দলীয় প্রতিনিধির মধ্যে বাঁটোয়ারার প্রস্তাব করেছে। এ ছাড়া রাষ্ট্রপতি ও নারী আসনেও নির্বাচনের ক্ষেত্রে উভয় কমিশনের সমন্বয়ের প্রয়োজন আছে।
পিআর পদ্ধতিটি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় এবং এতে করে অন্তত উচ্চকক্ষে ‘বহুদলীয় সংসদীয় গণতন্ত্র’ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হবে। কিন্তু গণতন্ত্রের স্বার্থেই প্রাদেশিক পরিষদের প্রতিনিধিত্বও উচ্চকক্ষে নিশ্চিত করা জরুরি। বাংলাদেশের আয়তন ছোট হতে পারে, কিন্তু জনঘনত্বে পৃথিবীর অন্যতম বড় দেশ। পৃথিবীতে বাংলাদেশের চেয়েও ক্ষুদ্র আয়তন ও জনসংখ্যা নিয়ে অনেক রাষ্ট্রে প্রদেশভিত্তিক ও দ্বিকক্ষবিশিষ্ট শাসনব্যবস্থা আছে। বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের স্বার্থেই প্রদেশভিত্তিক শাসনব্যবস্থা চালু হওয়া প্রয়োজন।
অন্যদিকে প্রদেশের নাম পুরোনো চার বিভাগের (ঢাকা-চট্টগ্রাম-রাজশাহী-খুলনা) নামে করার প্রস্তাব করা মানে বিভাগকেন্দ্রিক নতুন এক বিতর্ক তৈরির সুযোগ করে দেওয়া। প্রদেশ হোক অঞ্চলভিত্তিক—পূর্বাঞ্চল, মধ্যাঞ্চল, উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল এবং দেশের রাজধানী ‘ন্যাশনাল ক্যাপিট্যাল টেরিটরি’ হিসেবে আলাদা প্রাদেশিক মর্যাদা পাক।
সংবিধান সংশোধন ও সংকট
৫ আগস্টের পর কেউ কেউ বাহাত্তরের সংবিধানকে ‘ছুড়ে ফেলা’, ‘নতুন সংবিধান প্রণয়ন’, ‘পুনর্লিখন’ ইত্যাদি প্রসঙ্গ তুলেছিলেন। কিন্তু সংবিধান সংস্কার কমিশন বিভিন্ন ধারা-উপধারার ক্ষেত্রে ‘প্রতিস্থাপন’ বা ‘প্রতিস্থাপিত’ শব্দগুলো ব্যবহার করে আদতে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম দুই সংবিধান এবং বস্তুত বাহাত্তরের সংবিধানকেই ভিত্তি ধরে সংবিধান সংস্কারের প্রস্তাব পেশ করেছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।
কমিশন বলেছে, প্রস্তাবিত সংশোধনী উভয় কক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে পাস হলে তা গণভোটে উপস্থাপিত হবে। সংকট হলো, বর্তমানে আইনসভা বিলুপ্ত, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি নেই। তাহলে প্রস্তাবিত সংশোধনী পাস হবে কীভাবে? গণপরিষদ (কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি) নির্বাচন একটি উত্তম উপায় হতে পারে।
গণপরিষদ নির্বাচন না হলে বিদ্যমান সাংবিধানিক ধারা মান্য করেই সংসদ নির্বাচন হবে। অথচ প্রায় সব দলই বলেছিল, এই সংবিধানের অধীন কোনো অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হওয়া সম্ভব নয়। ফলে এর অধীন এখন নির্বাচনে যাওয়া মানেই জুলাইয়ের স্পিরিটের বিরুদ্ধে যাওয়া। তা ছাড়া নির্বাচিত সরকার এলেই সংবিধান সংস্কার হয়ে যাবে, এটিও একটি প্রথাগত ভাবনা। ধরে নেওয়া যাক, সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে নিম্নকক্ষ হাজির হয়েছে, তাহলে সংবিধান সংশোধন না করে উচ্চকক্ষ গঠন বা গণভোটের ফয়সালা কীভাবে নিষ্পত্তি হবে?
সংবিধান সংস্কারের ক্ষেত্রে অনিবার্য জটিলতা ও সংকট আছে, যা এড়িয়ে যাওয়া নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সংঘর্ষ তৈরি করবে। এই চ্যালেঞ্জ সরকার, কমিশন ও রাজনৈতিক অংশীজনেরা কী করে মোকাবিলা করবেন, সেটিই এখন জরুরি আলোচনার বিষয় হওয়া উচিত।
শেষ কথা
অংশীজনদের মনে রাখা দরকার, মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে গণপরিষদ নির্বাচন না করে সত্তরের নির্বাচনের ভিত্তিতে গণপরিষদ গঠনের সমালোচনা আছে। একই ম্যান্ডেটের শক্তিতে গঠিত বলে সেই সমালোচনা তাহলে প্রবাসী সরকারের ব্যাপারেও চলে আসে এবং সে ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের জনযুদ্ধ চরিত্রটিও প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে।
ঐতিহাসিক এই বাদানুবাদ বাদ দিলেও ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ যদি বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন হতে পারে, তাহলে সবকিছু প্রস্তুত করে সেই নির্বাচনের আলোকেই গণপরিষদ ও জাতীয় সংসদ গঠিত হতে পারত। মুক্তিযুদ্ধের আগে ও অব্যবহিত পরে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সবচেয়ে বড় জনপ্রিয় দল হয়েও সে পথে যায়নি; বরং তারা জনপ্রিয়তা ও সংখ্যাগরিষ্ঠতার আত্মবিশ্বাসে ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর সংবিধান বিল পাস করে মাত্র চার মাসের মাথায় নির্বাচনে গেছে।
আওয়ামী-অধ্যুষিত সেই গণপরিষদে প্রণীত সংবিধানটির যদি ‘মুজিববাদী’ আওয়ামীকরণ হয়ে থাকে, তাহলে ধরে নিতে হয়, ক্ষমতা যার, দলিলও তার পক্ষেই কথা বলে। আশ্চর্য বিষয় হলো, পরবর্তী সব নির্বাচিত-অনির্বাচিত সরকারও ক্ষমতার বলপ্রয়োগে সংবিধানে সেই শক্তিশালীর পক্ষেই ভাষা পুনর্নির্মাণ ও পরিমার্জন করে পরোক্ষে মুজিববাদীই হয়েছে!
এবার যাঁদের হাতে সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা আসবে, তাঁরা যেন ভূতপূর্ব ক্ষমতাবানদের সব ত্রুটিবিচ্যুতি পরিমার্জন করেন এবং অবশ্যই বিভিন্ন সংখ্যাগরিষ্ঠ ও শক্তিশালী বর্গের মনোরঞ্জনের জন্য সংবিধান সংস্কার না করেন। তাহলে তা একাত্তর-নব্বই-চব্বিশের গণতান্ত্রিক স্পিরিটের সঙ্গে প্রতারণা করা হবে।
●ড. সৌমিত জয়দ্বীপ সহকারী অধ্যাপক, স্কুল অব জেনারেল এডুকেশন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়