ফারাক্কা বাঁধের সুবর্ণজয়ন্তী ভারতে বাংলাদেশের চিরস্থায়ী দুঃখ
ফারাক্কা বাঁধ বাংলাদেশের জন্য এক স্থায়ী দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে, যা ধাপে ধাপে কৃষি, মাছ, বন, পানি এবং মানুষের জীবনধারার ওপর ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে এনেছে। এই পরিস্থিতি শুধু একটি নদীর পানি কমে যাওয়ার ফল নয় বরং এটি একটি দীর্ঘস্থায়ী আঞ্চলিক পানি ন্যায্যতা ও বৈষম্যজনিত সমস্যার প্রতিফলন। বাংলাদেশের কোটি মানুষের জীবিকা, পরিবেশ ও ভবিষ্যৎ বাঁচাতে ফারাক্কা ইস্যুতে আন্তর্জাতিক আইন, জাতিসঙ্ঘ পরিবেশ সনদ এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কার্যকর পানি ভাগাভাগির নতুন ব্যবস্থা অপরিহার্য - ড. মো: মিজানুর রহমান [সূত্র : নয়াদিগন্ত, ৩০ মে ২০২৫]
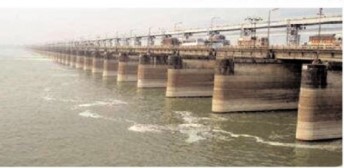
ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা ১৯৫১ সালে শুরু হলেও ১৯৭৫ সালে গঙ্গা নদীর ওপর নির্মিত এই বাঁধটির কার্যক্রম শুরু হয়। অর্থাৎ বাঁধের সুবর্ণজয়ন্তী ভারতের। অথচ গত পাঁচ দশকে বাংলাদেশের জন্য এই বাঁধ স্থায়ী দুঃখের কারণ হয়ে আছে। দুই দশমিক ২৪ কিমি: দৈর্ঘ্যরে বাঁধটিতে রয়েছে ১০৯টি গেটসহ একটি ব্যারাজ যা গঙ্গার পানি নবদ্বীপের দিকে মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ফলে হুগলি নদীর পানিপ্রবাহ বৃদ্ধি পায়।
গঙ্গার প্রবাহ একতরফা নিয়ন্ত্রণ করছে ভারত, যার ফলে বাংলাদেশের পরিবেশ, অর্থনীতি, কৃষি, মৎস্য, জনস্বাস্থ্য এবং নদীভিত্তিক জীবনব্যবস্থায় নেমে এসেছে বিপর্যয়। ভারতের দাবি ছিল, হুগলি নদীর প্রবাহে জলপ্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় কলকাতা বন্দরের গভীরতা কমে যাওয়ার সমস্যা সমাধানের জন্য ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে গঙ্গা নদীর প্রবাহকে পশ্চিমবঙ্গের দিকে ঘুরিয়ে দেয়া হবে। পানিপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণের নামে প্রকল্প শুরু হলেও, প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল এক কৌশলগত ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত।
আন্তর্জাতিক নদী ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ‘নদী বহমান দেশগুলোর মধ্যে যৌথ ব্যবস্থাপনা ও সমবণ্টনের নীতিমালা’ প্রযোজ্য। জাতিসঙ্ঘের ১৯৯৭ সালের আন্তর্জাতিক পানিপ্রবাহ কনভেনশন অনুযায়ী, অভিন্ন নদীর পানি ব্যবহার করতে হলে সব অংশীদার দেশের সম্মতি ও যৌথ আলোচনা আবশ্যক। বাস্তবে বেশির ভাগ শক্তিশালী দেশ এই আইন উপেক্ষা করে। এই বাঁধ নির্মাণের সময় ভারতও বাংলাদেশকে কার্যত উপেক্ষা করে একতরফাভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে। তৎকালীন পাকিস্তানের প্রবল আপত্তি এবং আন্তর্জাতিক মহলের উদ্বেগ সত্ত্বেও ভারতের এই আচরণ ছিল আন্তর্জাতিক আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।
বিশ্বে এ ধরনের বাঁধের নজির
নদীর উজানে বাঁধ নির্মাণ করে ভাটির দেশের পানিপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত করার ঘটনা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা যায়, যা শুধু পরিবেশগত বিপর্যয়ই নয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সঙ্কটও সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের জন্য ফারাক্কা বাঁধও একটি মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। গ্র্যান্ড ইথিওপিয়ান রেনেসাঁ ড্যাম (GERD) প্রকল্পটি ইথিওপিয়া নীল নদের ওপর ২০১১ সালে শুরু করে। ১৯৯৭ সালের জাতিসঙ্ঘের আন্তর্জাতিক অপ্রবহমান পানির আইন’ অনুযায়ী, কোনো উজান দেশ ভাটির দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে একতরফা সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। মিসর এই আইনের আলোকে ইথিওপিয়ার কর্মকাণ্ডকে ‘একতরফা ও অবৈধ’ বলে দাবি করে। ২০২০-২৩ সালের মধ্যে ইথিওপিয়া বাঁধটি চার ধাপে পানি সংরক্ষণ সম্পন্ন করেছে। এখনো ত্রিপক্ষীয় আলোচনা (মিসর, সুদান, ইথিওপিয়া) কার্যকর কোনো চুক্তিতে পৌঁছায়নি। উল্লেখ্য, মিসরের মোট পানির ৯৫ শতাংশ আসে নীল নদ থেকে। এই বাঁধকে তার জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে বিবেচনা করে।
তুরস্ক ইউফ্রেটিস এবং টাইগ্রিস নদীর ওপর বেশ কয়েকটি বড় বাঁধ নির্মাণ করেছে, যার মধ্যে Ataturk Dam সবচেয়ে আলোচিত। ইরাক এবং সিরিয়া অভিযোগ করেছে যে, এতে পানির প্রবাহ বিপর্যস্ত হয়ে কৃষি, শিল্প ও পরিবেশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তুরস্ক ১৯৯৭ সালের UN Convention অনুস্বাক্ষর করেনি, ফলে তারা আন্তর্জাতিক চাপে ততটা প্রতিক্রিয়া জানায়নি। এই বাঁধের ফলে ১৯৭৫ সালের তুলনায় সিরিয়ায় ইউফ্রেটিস নদীর পানির প্রবাহ ৪০% কমেছে (WB, ২০২১)।
চীন মেকং নদীর ওপর ১১টির বেশি বাঁধ নির্মাণ করেছে, যার ফলে থাইল্যান্ড, লাওস, কম্বোডিয়া ও ভিয়েতনাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভিয়েতনামের মেকং ডেল্টা অঞ্চলে ধান উৎপাদন ১৫ শতাংশ কমেছে (MRC, ২০২২)। মেকং নদীর পানির স্তর ২০২০ সালে ছিল গত ৬০ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। চীনের একতরফা পানি নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করে ASEAN দেশগুলো বৈঠক করেছে, তবে চীন তা আমলে নিচ্ছে না।
ফারাক্কা বাঁধ ভারতের লাভ নাকি কৌশল
প্রশ্ন জাগে, ফারাক্কা বাঁধ কি কেবল ভারতের লাভে দিয়েছে নাকি বাংলাদেশবিরোধী কৌশলের জন্য দিয়েছে? আগেই বলেছি, ফারাক্কা বাঁধের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কলকাতা বন্দরের কার্যকারিতা বজায় রাখতে হুগলি নদীতে পানিপ্রবাহ সরবরাহ করে নদীর পলি অপসারণ করা। উল্লেখ্য, কলকাতা বন্দর ভারতের অন্যতম ব্যস্ত বন্দর, যার বার্ষিক পণ্য হ্যান্ডলিং প্রায় ৬৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন (Kolkata Port Trust, ২০২৩)। ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে হুগলি নদীর নাব্যতা ও নৌপথ রক্ষা হয়েছে। কলকাতা শহরের কাছাকাছি এলাকায় নদী দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের কিছু সীমিত সাফল্যও পরিলক্ষিত হয়েছে (Ray et al., ২০২০)।
অথচ, ফারাক্কা বাঁধের কারণে ভারতের গঙ্গার নিম্নপ্রবাহে পলি জমে নদীর গভীরতা হ্রাস পেয়েছে, যার ফলে পশ্চিমবঙ্গের মালদহ ও মুর্শিদাবাদে নদীভাঙনে প্রতি বছর গড়ে আট হাজার হেক্টর জমি বিলীন হচ্ছে (WB, ২০০৫)। নদীর প্রবাহ ব্যাহত হওয়ায় মাছের উৎপাদন কমেছে, জলজপ্রাণীর আবাস ধ্বংস হয়েছে। নদীভাঙনের ফলে হাজার হাজার পরিবার বাস্তুচ্যুত হয়েছে এবং কৃষিজমি হারিয়েছে। শুধুমাত্র মালদহ জেলায় নদীভাঙনের কারণে ১৯৭৫-২০২০ সালের মধ্যে ৩৫ হাজার একর জমি বিলীন হয়েছে (Basu & Das, ২০২১)। এর ফলে, ভারতের কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে পানি ব্যবস্থাপনা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। বিশেষত বন্যার সময় নদীভাঙন ও পানিবণ্টন সমস্যা ঘিরে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হয়।
ফারাক্কা বাঁধের মাধ্যমে ভারত ভূরাজনৈতিকভাবে শক্তির প্রতীক হিসেবে কাজ করেছে। বাংলাদেশের প্রতি একটি প্রভাব বিস্তারকারী হাতিয়ার হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর মাধ্যমে গ্রীষ্মে মাত্র ২০০ কিউসেকের নিচে পানি ছাড়ার ঘটনায় ভারতের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা এবং পানি বণ্টন বিশেষজ্ঞরা প্রশ্ন তুলেছেন; এতে ভারতের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে। এক কথায়, ফারাক্কা বাঁধ হুগলি নদীর নাব্যতা রক্ষার কৌশল হলেও এটি একটি সুপরিকল্পিত বাংলাদেশবিরোধী পানিকৌশলের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।
গত ৫০ বছরে ভারত নিজেও পরিবেশ ও অর্থনীতিতে এর বিপর্যয়কর প্রভাবের সম্মুখীন হয়েছে। তাই একে শুধুমাত্র ভারতের লাভজনক প্রকল্প বলা যাবে না; বরং এটি একটি বিতর্কিত প্রকল্প, যা আঞ্চলিক সহযোগিতা ও পানি-নীতির ন্যায্যতা পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে।
ফারাক্কা বাঁধে বাংলাদেশের দুঃস্বপ্ন
ফারাক্কা বাঁধ চালুর পর থেকে শুষ্ক মৌসুমে (ডিসেম্বর-মে) বাংলাদেশের পদ্মা নদীর প্রবাহ গড়ে ৫০-৬০ শতাংশ কমে গেছে। তথ্য অনুযায়ী, ১৯৭৫ সালে পদ্মায় শুষ্ক মৌসুমে প্রবাহ ছিল প্রায় ৭০,০০০ কিউসেক, যা ২০১০-এর পরে গড়ে ১২,০০০-১৫,০০০ কিউসেকে দাঁড়ায় (BWDB, ২০২০)। পদ্মা নদী, তার শাখা নদীগুলো এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড ভয়াবহ নদী-শুকিয়ে যাওয়া, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, নদীভাঙন এবং কৃষি ও জীববৈচিত্র্যের ধ্বংসের মুখে পড়েছে। এর ফলে বাংলাদেশ বহুমাত্রিক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের শিকার হয়েছে। এই বিষয় এখন আর শুধু রাজনৈতিক বিতর্কের বিষয় নয়; বরং পরিসংখ্যান, গবেষণা ও বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে তা আজ একটি অর্থনৈতিক ও মানবিক সঙ্কট হিসেবে চিহ্নিত।
এই পানির অভাব বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভয়াবহ সেচ সঙ্কট তৈরি করেছে। শুধু রাজশাহী, পাবনা ও কুষ্টিয়ায় ১৯৮০-২০২২ সালের মধ্যে প্রায় সাত লাখ হেক্টর জমি সেচের অভাবে পতিত হয়েছে (IWMI, ২০২৩)। খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) ২০২৩ সালে জানায়, এতে বার্ষিক ২৫-৩০ লাখ টন খাদ্য উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে, যার আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ বছরে প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা।
নদী শুকিয়ে যাওয়ায় দেশের অভ্যন্তরীণ নদী ও জলাশয়ে মাছের প্রজননব্যবস্থা ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, নদীগুলোতে দেশীয় প্রজাতির মাছ উৎপাদন গত ৫০ বছরে গড়ে ৬৫ শতাংশ কমেছে (FRI)। বিশেষ করে ইলিশ মাছের ঐতিহ্যবাহী প্রজননক্ষেত্র পদ্মায় প্রবাহ কমে যাওয়ায় ইলিশ ১৯৭৫ সালে ৭০ হাজার টন থেকে ২০২৩ সালে ১০ হাজার টনে নেমে এসেছে (DoF, ২০২৩)। এমনকি পদ্মা-গড়াই-মধুমতিতে ইলিশ প্রায় বিলুপ্ত। পানির অভাবে গবাদিপশুর খাদ্যের সঙ্কট দেখা দেয়, ফলে দুধ, গোশত ও পশুর স্বাস্থ্য নাজুক হয়ে পড়ে। শুধুমাত্র ২০১০-২০২২ সালের মধ্যে পশ্চিমাঞ্চলের গবাদিপশু উৎপাদনশীলতা ১৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে, যার কারণে বছরে প্রায় ৪০০ কোটি টাকার গোশত ও দুধ উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে (DoE, ২০২৩)।
ফারাক্কার কারণে গঙ্গার স্বাদু পানি সুন্দরবন পর্যন্ত পৌঁছায় না, ফলে সুন্দরবনের পানির লবণাক্ততা বেড়ে ২০-২৫ পিপিটি হয়ে দাঁড়িয়েছে (DoE, ২০২১)। তথ্য মতে, সুন্দরবনের প্রায় ৪৫ শতাংশ এলাকায় সুন্দরী গাছের বৃদ্ধির হার থেমে গেছে এবং বৃক্ষমৃত্যুর হার দ্বিগুণ হয়েছে (BFRI)। সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য থেকে আয়নির্ভর জনগোষ্ঠীর জীবন ও আয় উৎস ভয়ঙ্কর অনিশ্চয়তায় পড়েছে। বনজ সম্পদ সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহকারী প্রায় সাড়ে চার লাখ পরিবার সরাসরি বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে।
লবণাক্ততার কারণে খাবার পানির সঙ্কটে নারী ও শিশুদের প্রতিদিন গড়ে ৩-৫ কিলোমিটার হাঁটতে হয় খাবার পানি সংগ্রহের জন্য। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের অন্তত এক কোটি মানুষ নিরাপদ খাবার পানির অভাবে রয়েছে, কারণ এই ফারাক্কা বাঁধের কারণে। (UNICEF, ২০২১) পদ্মা অববাহিকার ১২ জেলার অন্তত ১ দশমিক ২ কোটি মানুষ এখন কৃষি ও পানিনির্ভর জীবিকা থেকে বঞ্চিত। (BCAS, ২০২২)
ফারাক্কার কারণে নদীভাঙনের ফলে প্রতি বছর প্রায় ৫০ হাজার মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে এবং অভ্যন্তরীণ পরিবেশ উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়, যা দেশের অর্থনীতিতে বছরে প্রায় তিন হাজার কোটি টাকার ক্ষতি ঘটায় (GED, ২০২০–২০২৫)। খুলনা বিভাগে ১৯৮০ সালে যেখানে ৬৮ শতাংশ মানুষ কৃষি ও মৎস্য খাতে নিয়োজিত ছিল, বর্তমানে ফারাক্কার প্রভাবে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৩৯ শতাংশ (BBS)। দারিদ্র্য ও বেকারত্বের হার এই অঞ্চলে গড়ে দেশের তুলনায় দ্বিগুণ (BBS, ২০২৩)। পরিবেশ অধিদফতরের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ফারাক্কা বাঁধের কারণে বছরে গড়ে প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়। ৫০ বছরে এই ক্ষতির পরিমাণ প্রায় আট লাখ কোটি টাকা।
সমাধানের প্রচেষ্টা এবং বাংলাদেশের করণীয়
ফারাক্কা বাঁধ বাংলাদেশের জন্য শুধু একটি কৌশলগত প্রতিবন্ধকতাই নয়, বরং এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক, পরিবেশগত ও কূটনৈতিক সঙ্কটের উৎস। এই বাঁধ ইস্যুতে মাওলানা ভাসানীর গণপ্রতিবাদ, রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কূটনৈতিক তৎপরতা এবং জাতিসাথে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ, সবকিছুই ছিল বাংলাদেশের জল অধিকার রক্ষার অংশ। কিন্তু ৫০ বছর পার হলেও বাংলাদেশ এখনো আন্তর্জাতিক আইনি কাঠামোর বাইরে থেকে এই সঙ্কট মোকাবেলা করে যাচ্ছে।
বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে গঙ্গা নদী নিয়ে ১৯৯৬ সালে ৩০ বছরের জন্য গঙ্গা পানি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। সেই চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশের ন্যায্য হিস্যা ভারত পুরোপুরি দেয়নি, বিশেষ করে শুকনো মৌসুমে ফারাক্কা বাঁধের পানি প্রত্যাহার করার ফলে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে খরা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।
এই পরিস্থিতিতে সমাধানের জন্য প্রথমত, ৫৪টি অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ও বাধ্যতামূলক ইন্দো-বাংলাদেশ জয়েন্ট রিভার কমিশনের (JRC) চুক্তিগত কাঠামো গঠনের জন্য বাংলাদেশকে ভারত সরকারের সাথে উচ্চপর্যায়ের নিয়মিত কূটনৈতিক সংলাপ জোরদার করতে হবে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশকে অবশ্যই জাতিসঙ্ঘের আন্তর্জাতিক পানিবণ্টন আইনের (UN, ১৯৯৭) আলোকে ভারতের কাছে দায়িত্বশীল আচরণের প্রত্যাশা জানাতে হবে। তৃতীয়ত, বৈজ্ঞানিক তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে পানির হিস্যা নির্ধারণে দুই দেশের নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট ও পরিবেশবাদীদের যৌথভাবে কাজ করা উচিত। চতুর্থত, দেশের অভ্যন্তরে বিকল্প পানি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার দিকে মনোযোগী হতে হবে। পঞ্চমত, আঞ্চলিক সংহতির ভিত্তিতে একাধিক দেশ (যেমন নেপাল, ভুটান) কে নিয়ে ‘বেসিন ওয়াইড মডেল’ তৈরির মাধ্যমে ভারতকে বোঝানো যে একতরফা পানিবণ্টন কেবল বাংলাদেশের ক্ষতি নয়, আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্যও হুমকিস্বরূপ। ষষ্ঠত, দেশের জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি, পানিবণ্টন-সংক্রান্ত পরিবেশগত ও মানবিক ক্ষয়ক্ষতির ডকুমেন্টেশন এবং আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় এসব তুলে ধরা ও কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টিতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।
সবশেষে বলা যায়, ফারাক্কা বাঁধ বাংলাদেশের জন্য এক স্থায়ী দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে, যা ধাপে ধাপে কৃষি, মাছ, বন, পানি এবং মানুষের জীবনধারার ওপর ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে এনেছে। এই পরিস্থিতি শুধু একটি নদীর পানি কমে যাওয়ার ফল নয় বরং এটি একটি দীর্ঘস্থায়ী আঞ্চলিক পানি ন্যায্যতা ও বৈষম্যজনিত সমস্যার প্রতিফলন। বাংলাদেশের কোটি মানুষের জীবিকা, পরিবেশ ও ভবিষ্যৎ বাঁচাতে ফারাক্কা ইস্যুতে আন্তর্জাতিক আইন, জাতিসঙ্ঘ পরিবেশ সনদ এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কার্যকর পানি ভাগাভাগির নতুন ব্যবস্থা অপরিহার্য। ভারতের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করেই বাংলাদেশকে শক্তিশালী ও তথ্যনির্ভর ভূমিকা রাখতে হবে, যাতে পানি একতরফাভাবে শক্তির অস্ত্র না হয়ে ওঠে, বরং আঞ্চলিক সহযোগিতার ভিত্তি হিসেবে গড়ে ওঠে।
লেখক : অর্থনীতিবিদ, গবেষক ও কলামিস্ট