গণতন্ত্র, নির্বাচন ও আইনের শাসন
ড. ফরিদুল আলম [সূত্র : প্রতিদিনের বাংলাদেশ, ২৮ অক্টোবর ২০২৪ ]
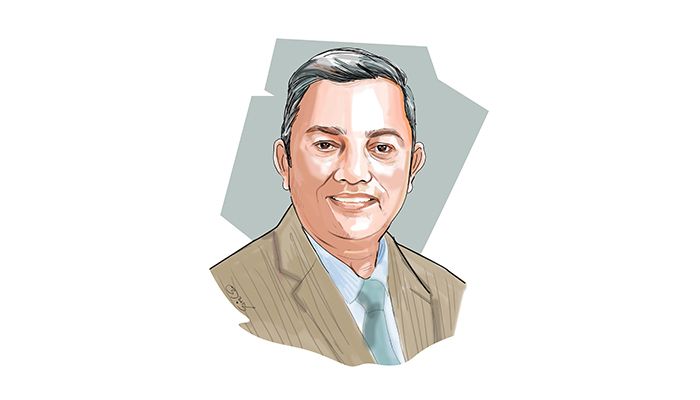
সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের রাজনীতির সবচেয়ে চর্চিত বিষয় রাষ্ট্রপতির অপসারণ বা পদত্যাগ ইস্যু। একজন সাংবাদিকের সঙ্গে আলাপে শেখ হাসিনার পদত্যাগের দালিলিক প্রমাণ নেই—এই মন্তব্য করেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। তার এই মন্তব্যের পর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনসহ কয়েকটি সংগঠন রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবি তোলে। সরকারের তরফ থেকেও একজন উপদেষ্টা ওই ব্ক্তব্যের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি শপথ ভঙ্গ করেছেন মর্মে মন্তব্য করেন। তবে বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করতে হলে যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়, বর্তমান সরকার অন্তর্বর্তীকালীন হওয়ার কারণে আইনগতভাবে সে মোতাবেক তাকে অপসারণ করার সুযোগ নেই। এহেন অবস্থায় রাষ্ট্রপতির পদত্যাগই কেবল একটি সমাধান হতে পারে। অবশ্য সেক্ষেত্রেও বাদ সাধছে আমাদের সংবিধানের কিছু সুস্পষ্ট বিধান। সংবিধানের ৫৪ অনুচ্ছেদে বলা আছে, ‘রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে বা অন্য কোনো কারণে রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ্য হইলে ক্ষেত্রমত রাষ্ট্রপতি নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত কিংবা রাষ্ট্রপতি স্বীয় কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্পিকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করিবেন।’
আমরা জানি, সরকার পরিবর্তনের পর জাতীয় সংসদের স্পিকার তার পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি যদি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে পদত্যাগ করেন, তাহলেও সংবিধানের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সম্ভব নয়। অনেকে অবশ্য এক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করে বলছেন যে, সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক বা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বিধান না থাকা সত্ত্বেও তো একটি অন্তর্বর্তী সরকার বর্তমানে রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালন করছে, যা আপৎকালীন বা ‘ডকট্রিন অব নেসিসিটি’র আলোকে গঠিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে বর্তমান রাষ্ট্রপতির বেলায়ও তো এমনটা হতে পারে। এ ধরনের বক্তব্য যদি জোরালো হয় এবং আপামর মানুষের এতে সমর্থন আছে বলে প্রতীয়মান হয়, তবে বিষয়টি হয়তো সম্ভব। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, আমাদের সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির পদটি যেহেতু আলংকারিক হিসেবে বিবেচিত এবং সরকারের কোনো নীতিগত সিদ্ধান্তে বিরোধ পোষণ করার ক্ষেত্রে তার সুযোগ সীমিত (অন্তর্বর্তী সরকারের ক্ষেত্রে তা একেবারেই নেই), সেক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি সাহাবুদ্দিনের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে থাকা না-থাকার ওপর সরকারের দৈনন্দিন কাজে কোনো ধরনের ব্যাঘাত ঘটার সুযোগ নেই।
সমস্যা হচ্ছেÑ এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের ইচ্ছার পরিবর্তে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবিটি সরকারের ভেতর থেকে এসেছে। এর যুক্তি হিসেবে ৫ আগস্ট দেওয়া জাতির উদ্দেশে তার ভাষণকে উদ্বৃত করা হচ্ছে, যেখানে তিনি বলেছিলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেছেন এবং আমি তা গ্রহণ করেছি।’ আরেকটি যুক্তি হচ্ছে ৮ আগস্ট এই মর্মে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনবিষয়ক সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের কাছে তার পক্ষ থেকে একটি রেফারেন্স চাওয়া। এই বিষয়গুলো প্রমাণ করছে যে, তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে মিথ্যাচার করেছেন, যা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদাধিকারী হিসেবে তিনি করতে পারেন না। তবে এখানে একই সঙ্গে বিভিন্নভাবে এই দাবিটিও উত্থাপিত হচ্ছে যে, শেখ হাসিনা যদি পদত্যাগ করেই থাকেন তাহলে রাষ্ট্রপতির কাছে ব্যক্তিগতভাবে নয়, তার দপ্তরে এর কপি নিশ্চয়ই সুরক্ষিত থাকার কথা, সেই সঙ্গে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, আইন মন্ত্রণালয়সহ সরকারের অপরাপর দপ্তরেও এর অনুলিপি থাকার কথা। সেসব জায়গা থেকেও এ বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়নি। বিষয়টি নিয়ে সরকারর তরফ থেকে সরব হলেও এটি কেবল রাষ্ট্রপতির জন্যই নয়, বর্তমান সরকারের বৈধতার বিষয়টিও প্রশ্নবিদ্ধ করে, কেননা প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের আলোকেই তিনি অন্তর্বর্তী সরকারকে শপথ করিয়েছেন। অনেক সংবিধান বিশেষজ্ঞ অবশ্য এটাও মন্তব্য করেছেন যে, প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ করা বা না করা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নয়, মূল বিষয়টি হচ্ছে ছাত্র-জনতার ব্যাপক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন, যা একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের যুক্তি হিসেবে যথেষ্ট।
আমরা দেখেছি, সরকারের দাবির পর বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের পক্ষ থেকে তার পদত্যাগ দাবি করে ঢাকাসহ সারা দেশে বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছে, এমনকি বঙ্গভবন পর্যন্ত অবরোধ করা হয়েছিল। একপর্যায়ে সরকারের হস্তক্ষেপেই তা বন্ধ হয়। সর্বশেষ উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক শেষে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ প্রশ্নে সরকারের একজন উপদেষ্টা সাংবাদিকদের জানান যে, রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের বিষয়টি নিয়ে তাড়াহুড়া করা হবে না, আবার বিলম্বও করা হবে না, রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনাক্রমে দ্রুতই একটি যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এর ধারাবাহিকতায় ২৬ অক্টোবর বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের একটি দল বিএনপি, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী আন্দোলনসহ কয়েকটি দলের সঙ্গে বৈঠক করে। এ বিষয়ে জামায়াতসহ ইসলামী আন্দোলন এবং অন্যান্য কিছু দল একমত পোষণ করলেও বিএনপি তাদের অবস্থান পরিষ্কার করেনি, দলীয় ফোরামে আলোচনার পর তাদের সিদ্ধান্ত জানাবে বলে জানানো হয়েছে। তবে দলটি ইতঃপূর্বে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনায় তাদের অবস্থান পরিষ্কার করে বলেছিল যে, তারা নতুন করে কোনো সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টি হোক, সেটা চান না। একই দিনে বিএনপির অপর নেতা নজরুল ইসলাম খান ঢাকায় এক সভায় নির্বাচন নিয়ে সরকারের প্রতি দাবি জানিয়ে দ্রুত সংস্কারের কাজ শেষ করতে অনুরোধ জানিয়ে বলেন, এভাবে সময়ক্ষেপণ করতে থাকলে ধীরে ধীরে নানা ব্যক্তি এবং দলের সৃষ্টি হবে, যারা নানা ধরনের দাবি উত্থাপন করতে থাকবে, যার মধ্য দিয়ে দ্রুত নির্বাচনের বিষয়টি আরও অনিশ্চিত হয়ে যাবে।
বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে প্রায় তিন মাস হতে চলল। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সরকারবিরোধী সর্বাত্মক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিগত সরকারের পতনের পর সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দায়িত্ব নেওয়া বর্তমান সরকার এই যাত্রায় কতটুকু এগিয়েছে, জনগণের মধ্যে সরকারের প্রতি সমর্থন অটুট আছে কি না, ঘোষিত রাষ্ট্র সংস্কারের পর যে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা, সেই রাষ্ট্র সংস্কার প্রক্রিয়া কতটুকু অগ্রসর হলো এবং আরও কতটা সময় লাগতে পারে, দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং আইনের শাসন কোন পর্যায়ে ও বহুল আকাঙ্ক্ষিত নির্বাচনটিই-বা কবে নাগাদ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে জনগণের মধ্যে উদ্বেগ কাজ করছে গভীরভাবে। সবচেয়ে বড় কথা হলোÑ দেশে নিয়মিত সরকারের অনুপস্থিতিতে একটি অস্থির অবস্থা সামাল দেওয়ার নিমিত্তে যে সরকারটি এই মুহূর্তে দায়িত্ব পালন করছে, তারা তত দিনই নির্বিঘ্নে এই দায়িত্ব পালন করে যেতে পারবে, যত দিন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সরকারের বিষয়ে ঐক্য বজায় থাকবে। যত দিন যাচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এ নিয়ে ঐক্যের বড়ই অভাব রয়েছে। এই মুহূর্তে সদ্য ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ রাজনীতির মাঠে অনুপস্থিত, সহসাই তারা আবারও রাজনীতিতে ফিরে আসতে পারবে কি না, সেটাও অনিশ্চিত। শুরুতে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে জাতীয় পার্টির অন্তর্ভুক্তি থাকলেও সম্প্রতি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বের সঙ্গে দ্বন্দ্বের জেরে সরকারের সঙ্গে তাদের দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর সর্বশেষ আলোচনায় তারা ডাক পায়নি। সুতরাং বড় দলগুলোর মধ্যে বাকি রইল বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামী। এ কথা এই মুহূর্তে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, রাজনৈতিক দল হিসেবে এবং সমর্থনের দিক দিয়ে বিএনপি এখন পর্যন্ত ঢের এগিয়ে। তারা নির্বাচন চাচ্ছে। সংস্কার নিয়ে সরকারের গঠিত কমিশন এবং তাদের প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে সংস্কারের কার্যক্রম শুরু করা, এসব সময়সাপেক্ষ বিষয়। এ সময় পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করতে রাজি নয়। সেক্ষেত্রে আমাদের ধরে নিতে হবে যে, সরকারের কর্মকাণ্ডে রাজনৈতিক দলগুলো ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারছে না। এটি একটি অন্তর্বর্তী সরকারের বৈধতাকে গভীর প্রশ্নের মাঝে নিপতিত করবে।
সম্প্রতি ঢাকায় এক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংবিধান সংস্কার কমিটির চেয়ারম্যান, সরকারের উপদেষ্টা এবং বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ। তাদের বক্তব্যে তারা জানান যে, ‘শুধু নির্বাচন দিয়ে উৎকৃষ্ট গণতন্ত্রের নিশ্চয়তা বিধান সম্ভব নয়। তারা জোর দিয়ে বলেছেন, গণতন্ত্রে উত্তরণ ঘটাতে হলে সর্বাগ্রে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে মেরামত করতে হবে, যা এক দিনে, এক বছরে বা পাঁচ বছরে সম্ভব না। এর জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক ঐকমত্য। এর অর্থ যদি অনুধাবন করার চেষ্টা করি তাহলে বুঝতে হবে যে, সরকারকে সময় দিতে হবে, তবে কতটা সময়, সেটা নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। তবে রাজনৈতিকভাবে এটা নিয়ে ঐক্যে পৌঁছানো কিন্তু খুবই কঠিন বিষয়। সেই সঙ্গে এটাও স্মরণে রাখা ভালো যে, একটি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যে রাষ্ট্র মেরামতকর্ম সম্পাদিত হবে, সেখানে সব রাজনৈতিক দলের সমান অংশগ্রহণ সাধারণ মানুষের সমর্থনের প্রতিফলন ঘটাবে। এই বিবেচনায় এই সংস্কারের কাজটি যতটা না কঠিন তার চেয়েও কঠিন এর সার্বজনীনতার দিকটি নিশ্চিত করা। দিন শেষে রাজনৈতিক দলই দেশ শাসন করবে, এটাই গণতন্ত্রের ব্যাকরণ। সুতরাং রাজনৈতিক ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে সরকারও যদি হোঁচট খায়, তাহলে সেটা গণতন্ত্রমনা মানুষের জন্য খুবই দুর্ভাগ্যজনক হবে।
- অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়