জি-৭ সম্মেলন এবং বিশ্ব নেতৃত্বের প্রত্যাশা
নিরঞ্জন রায় [সূত্র : সময়ের আলো, ২২ জুন, ২০২৫]
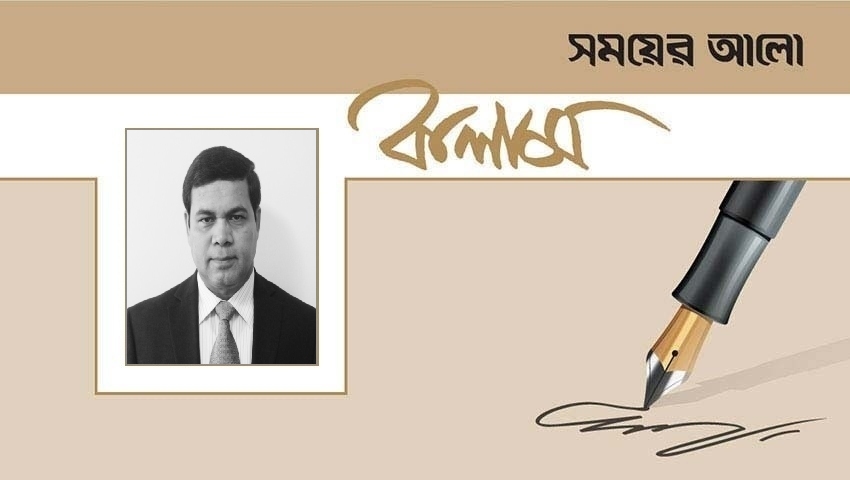
বিশ্ব নেতৃত্ব বিশ্যব্যাপী বাণিজ্যযুদ্ধ প্রশমনে এবং মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ বন্ধে ভালো একটি সিদ্ধান্ত আশা করছিলেন; কিন্তু এই সম্মেলন থেকে তেমন কিছুই দিতে পারেনি। উল্টো আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইসরাইল-ইরানের মধ্যকার যুদ্ধের কারণ দেখিয়ে তড়িঘড়ি করে সম্মেলনে ক্ষান্ত দিয়ে ফিরে গেছেন। অন্যরা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সম্মেলন উপস্থিত থেকে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে গেলেও হতাশ হয়েই ফিরেছেন। বিশ্ব নেতৃত্ব, অর্থনীতিবিদ, আর্থিক খাতের বিশ্লেষক, থিঙ্কট্যাঙ্ক এবং ব্যবসায়ীরা এই সম্মেলনের ফলাফল দেখে হতাশ হয়েছেন।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে বিশ্বে যে রাজনৈতিক মেরুকরণ হয়েছিল তার সঙ্গে সঙ্গে গঠিত হয়েছিল কয়েকটি অর্থনৈতিক জোট। সময়ের আবর্তে অর্থনৈতিক জোট বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বর্তমান বিশ্বে যে কতগুলো অর্থনৈতিক জোট আছে তা হিসাব করে বলা কঠিন। যেমন-গ্রুপ-৭, গ্রুপ-২০, আশিয়ান, বিমসটেক, ইইউ, নাফটা, ওপেক এবং এ রকম আরও অনেক অর্থনৈতিক জোট বিশ্ব কার্যকর আছে। নাফটা অবশ্য পরিবর্তিত এবং সংশোধিত আকারে আছে এবং আগামী বছর এর মেয়াদ শেষ হবে, যদি নবায়ন বা বর্ধিত করা না হয়। বিশ্বে অসংখ্য অর্থনৈতিক জোট কার্যকর থাকলেও দুই-তিনটি জোট সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে গ্রুপ-৭ বা জি-৭ জোট হচ্ছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক জোট। এসব অর্থনৈতিক জোট ক্ষেত্রভেদে এক বা দুই বছর পরপর নিয়মিত সম্মেলন অনুষ্ঠান করে। জি-৭ জোটের শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় প্রতি বছর।
এবারের কানাডায় জি-৭ জোটের শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৬ এবং ১৭ জুন। গ্রুপ-৭ হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে শিল্পোন্নত এবং ধনী দেশগুলোর একটি সংস্থা, যার সদস্য রাষ্ট্র হচ্ছে-আমেরিকা, কানাডা, ব্রিটেন, ইতালি, ফ্রান্স, জার্মানি এবং জাপান। এই সংস্থাকে সংক্ষেপে জি-৭ নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে এবং এই সংক্ষিপ্ত নেমেই এটি বেশি পরিচিত। একসময় রাশিয়ার অন্তর্ভুক্তির কারণে এটি জি-৮ গ্রুপে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু ২০১৩ সালে রাশিয়া ক্রিমিয়াকে নিজেদের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার কারণে রাশিয়াকে আর এই গ্রুপের সম্মেলনে অংশ নিতে দেওয়া হয় না। ফলে এই সংস্থা জি-৭ হিসেবেই রয়ে গেছে। জি-৭ সম্মেলনে সদস্য রাষ্ট্রের পাশাপাশি অন্যান্য বৃহৎ অর্থনীতির দেশও অংশ নিয়ে থাকে সংস্থার প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণে। বর্তমান সম্মেলনের প্রেসিডেন্ট কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির আমন্ত্রণে ভারত, মেক্সিকো এবং অস্ট্রেলিয়াসহ আরও কয়েকটি দেশ অংশ নিয়েছিল।
এবার জি-৭ সম্মেলন এমন একসময় অনুষ্ঠিত হচ্ছিল যখন বিশ্বে এক চরম অস্থিরতা এবং উত্তেজনা বিরাজ করছে। এই উত্তেজনা যেমন আছে রাজনৈতিক অঙ্গনে, তেমনি আছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। ইসরাইল-হামাস যুদ্ধের সমাপ্তি টানার আগে ইসরাইল-ইরান পাল্টাপাল্টি মিসাইল হামলা শুরু হয়ে গেছে। ইসরাইল এবং ইরানের মধ্যকার হামলা এবং পাল্টাহামলা এক ধরনের সম্মুখ যুদ্ধে রূপ নিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের এই নতুন মাত্রা যেকোনো মুহূর্তে সর্বাত্মক যুদ্ধে রূপ নিতে পারে। এদিকে ট্রাম্প তার নির্বাচনি প্রচারে জোর দিয়ে বলেছিলেন যে তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে এক দিনের মধ্যে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করতে সক্ষম হবেন। তিনি অবশ্য চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। যুদ্ধ অব্যাহত আছে এবং রাশিয়া মাঝেমধ্যেই আক্রমণ তীব্র করছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ না হওয়া এবং রাশিয়ার এমন অবস্থানের কারণে পশ্চিম ইউরোপের, বিশেষ করে ন্যাটোভুক্ত দেশগুলো বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছে। তাদের ধারণা যে রাশিয়ার ইউরোপ নিয়ে ভিন্ন চিন্তা থাকতে পারে, যা তাদের জন্য হুমকি হয়ে দেখা দেবে।
রাজনৈতিক উত্তেজনার পাশাপাশি অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তাও সবার উদ্বেগের বিষয় হয়ে আছে। ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে বিশ্বব্যাপী যে বাণিজ্যযুদ্ধ শুরু করেছিলেন তার সন্তোষজনক সুরাহা এখনও হয়নি। ট্রাম্প নির্বিচারে যেসব দেশের ওপর উচ্চ হারে শুল্ক আরোপ শুরু করেছিলেন, তা আপাতত ৯০ দিনের জন্য স্থগিত আছে, যার মেয়াদ আগামী ৯ জুলাই শেষ হবে। ট্রাম্প প্রশাসন এবং অন্যান্য বৃহৎ অর্থনৈতিক দেশগুলোর প্রত্যাশা ছিল যে এই ৯০ দিন যুদ্ধবিরতির মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটি সন্তোষজনক সমাধান হবে এবং বিশ্ববাণিজ্যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে। কিন্তু সে রকম কোনো অগ্রগতি নেই বললে চলে। শুধু যুক্তরাজ্যের সঙ্গে স্বল্প শুল্কের মাধ্যমে বাণিজ্য করার একটা সমঝোতা হয়েছে। আর যে চীনের বিরুদ্ধে উচ্চ শুল্ক হার ধার্যের হুমকি দিয়ে এই বাণিজ্য যুদ্ধের সূচনা, সেই চীনের সঙ্গেই দীর্ঘমেয়াদি বাণিজ্য যুদ্ধবিরতি কার্যকর করে রেখেছে। এর বাইরে আমেরিকার দীর্ঘদিনের মিত্র এবং বৃহৎ অর্থনীতির দেশের সঙ্গে সে রকম কোনো সমঝোতা হয়নি। ফলে বাণিজ্য যুদ্ধের যে দামামা এবং বিশ্ববাণিজ্যে যে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে, তা রয়েই গেছে।
এ রকম একটি সংকটাপন্ন অবস্থায় যখন জি-৭ সম্মেলন অনুস্থিত হচ্ছিল, যেখানে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজে উপস্থিত ছিলেন, তখন সেই সম্মেলন থেকে ভালো কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে এমনটাই সবাই প্রত্যাশা করছিলেন। বিশেষ করে ট্রাম্পের ঘোষিত উচ্চ শুল্ক হারের কারণে সৃষ্ট বাণিজ্যযুদ্ধ নিরসনে এবং মধ্যপ্রাচ্য উত্তেজনা, বিশেষ করে ইসরাইল-ইরান যুদ্ধ বন্ধে কার্যকর কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে বলে বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা ছিল। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল সে রকম কোনো কিছুই এই সম্মেলনে হয়নি। শুল্ক হার নিয়ে আলোচনা সেভাবে হয়নি। ট্রাম্প প্রশাসনের তরফ থেকে এই সমস্যা সমাধানের কোনোরকম উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি। ‘হবে, হচ্ছে’ ধরনের কথার কৌশল অবলম্বন করে বিষয়টি পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়েছে।
ইসরাইল-ইরান যুদ্ধ বন্ধে সে রকম কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। এমনকি বিষয়টি নিয়ে গ্রুপ-৭-এর সদস্য রাষ্ট্রদের মধ্যে কোনোরকম ঐকমত্য দেখা যায়নি। ফ্রান্সসহ অন্যান্য কয়েকটি দেশ চেষ্টা করেছে এই যুদ্ধ বন্ধে একটা কার্যকর ভূমিকা গ্রহণের। কিন্তু আমেরিকা এ ব্যাপারে অনড় থাকায় কোনোরকম অগ্রগতি হয়নি। এমনকি ফ্রান্সের ভূমিকা যুদ্ধ বন্ধের পক্ষে হলেও সে রকম সুনির্দিষ্ট কোনো পদক্ষেপ ছিল বলে মনে হয়নি। একদিকে ইসরাইলকে সমর্থন করেছে, অন্যদিকে ইরানকে সংযত হয়ে যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে। এ রকম দ্বৈত অবস্থান যে যুদ্ধ বন্ধে সে রকম কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। অন্যপক্ষে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তো সরাসরি ইসরাইলকে সমর্থন করে বলেই ফেললেন যে ইসরাইলের নিজেদের রক্ষা করার সব অধিকার আছে।
বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে শক্তিশালী সংস্থা হচ্ছে এই জি-৭, যেখানে আছে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর এবং বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। এসব দেশই বিশ্বকে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। বিশ্বে আজ রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। অবস্থা এমন জটিল আকার ধারণ করছে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে বিশ্ব খুব কমই এ রকম সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। অথচ এই চরম সংকট উত্তরণে জি-৭ কোনোরকম ভূমিকা নিতে পারল না, যা অত্যন্ত হতাশার এবং পরিতাপের। আগামীতে বিশ্ব অর্থনীতি কোনদিকে মোড় নেয়, তা সংশ্লিষ্ট সবার উদ্বেগের বড় কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। যদি ইসরাইল-ইরান হামলা-পাল্টাহামলা সর্বাত্মক যুদ্ধে রূপ নিয়ে দীর্ঘ হয় এবং সেই সঙ্গে বাণিজ্যযুদ্ধ অব্যাহত থাকে, তা হলে বিশ্ব অর্থনীতি মন্দা এবং মহামন্দার কবলে পড়ে যেতে পারে।
এবারের জি-৭ সম্মেলন কোনোরকম ফলপ্রসূ সিদ্ধান্ত নিতে না পারলেও আয়োজক দেশ হিসেবে কানাডা কিছুটা হলেও সুবিধা নিতে পেরেছে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর সময় ভারতের সঙ্গে কানাডার যে তিক্ত সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছিল, তা দূর করে স্বাভাবিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপনে মার্ক কার্নি এই সম্মেলনকে দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছেন। মূল সম্মেলনের পাশে কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে এক আলোচনায় মিলিত হন, যেখানে উভয় নেতাই দুই দেশের মধ্যে স্বাভাবিক কূটনৈতিক কার্যক্রম চালু রাখার ব্যাপারে সম্মত হয়েছেন। মার্ক কার্নি একজন হার্ভার্ড গ্র্যাজুয়েট অর্থনীতিবিদ এবং ছিলেন বিশ্বের দুটো অর্থনীতির দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান। তিনি ভালো করেই জানেন যে আমেরিকার উচ্চ শুল্ক হার থেকে কানাডার অর্থনীতিকে রক্ষা করতে হলে তাকে উদীয়মান অর্থনীতি বা এমার্জিং মার্কেটের দিকে নজর দিতে হবে। আর এমার্জিং মার্কেটের বড় একটি অংশ হচ্ছে ভারত, যা মূলত একশ কোটি ভোক্তার বাজার। মার্ক কার্নি এই বাজার ধারার প্রাথমিক পদক্ষেপ শুরু করতে পেরেছেন এই জি-৭ সম্মেলনের সুযোগ কাজে লাগিয়ে।
এই সম্মেলন থেকে কানাডার আরও একটি প্রাপ্তি আছে, তা হচ্ছে ট্রাম্পের কাছ থেকে সম্মানজনক একটি পরিসমাপ্তি। গত জি-৭ সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কানাডার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোকে প্রকাশ্যে অসৎ এবং দুর্বল নেতা বলে উল্লেখ করেছিলেন। এবারের সম্মেলনে ট্রাম্প কানাডার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নিকে সে রকম অসম্মান করেননি, বরং যথেষ্ট সম্মান দিয়েই সম্মেলন শেষ করেছেন, যা কানাডার জন্য এই মুহূর্তে একটি বড় প্রাপ্তিই বলা যেতে পারে।
যদিও বিশ্ব নেতৃত্ব বিশ্যব্যাপী বাণিজ্যযুদ্ধ প্রশমনে এবং মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ বন্ধে ভালো একটি সিদ্ধান্ত আশা করছিলেন, কিন্তু এই সম্মেলন থেকে তেমন কিছুই দিতে পারেনি। উল্টো আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইসরাইল-ইরানের মধ্যকার যুদ্ধের কারণ দেখিয়ে তড়িঘড়ি করে সম্মেলনে ক্ষান্ত দিয়ে ফিরে গেছেন। অন্যরা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সম্মেলন উপস্থিত থেকে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে গেলেও হতাশ হয়েই ফিরেছেন। বিশ্ব নেতৃত্ব, অর্থনীতিবিদ, আর্থিক খাতের বিশ্লেষক, থিঙ্কট্যাঙ্ক এবং ব্যবসায়ীরা এই সম্মেলনের ফলাফল দেখে হতাশ হয়েছেন। কেননা তাদের প্রত্যাশা ছিল যে অন্তত বাণিজ্য যুদ্ধের একটা সন্তোষজনক সমাধান এবং ইসরাইল-ইরান যুদ্ধ বন্ধের ব্যাপারে ভালো অগ্রগতি হবে। কিন্তু জি-৭-এর শীর্ষ সম্মেলন থেকে তাদের সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি।