কৃষি উৎপাদন : অনেক উৎপাদন বেড়েছে কিন্তু এ উৎপাদন বাড়াতে আমাদের কী কী ক্ষতি হয়েছে তার মূল্যায়ন করতে হবে
আনু মুহাম্মদ [সূত্র : বণিক বার্তা, ১৩ মে ২০২৫]
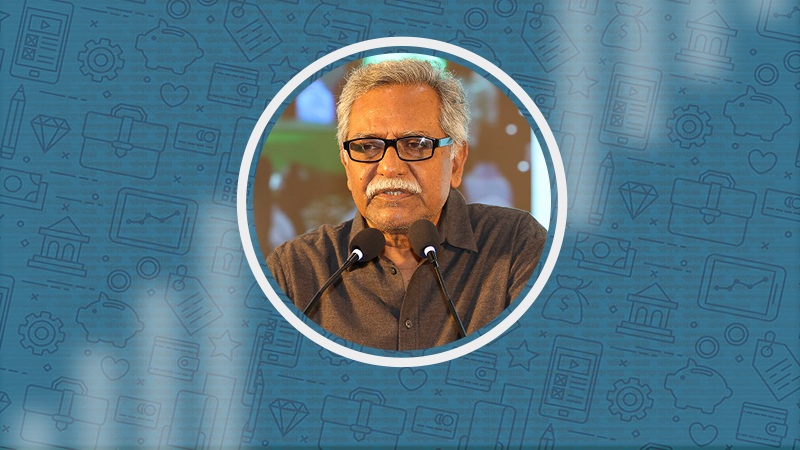
কৃষি আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কারণ আমাদের দেশের বিশাল একটা জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির সঙ্গে সম্পৃক্ত। কৃষি ও কৃষককে নিয়ে বণিক বার্তার যে ধারাবাহিক প্রয়াস তা সত্যি প্রশংসনীয়। আমাদের গণমাধ্যমে বন্যা, খরা, নদীভাঙন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষকের বিপর্যস্ত অবস্থা, ফসলের ন্যায্যমূল্য না পাওয়া কিংবা কৃষিভিত্তিক যে গবেষণা সেগুলো যথাযথ গুরুত্ব পায় না। অথচ আশির দশক পর্যন্ত দেশসেরা গবেষণা প্রতিষ্ঠানসহ সব ক্ষেত্রেই কৃষি কাঠামো, কৃষকের বিভিন্ন সমস্যাকে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে দেখা হতো। এরপর তা কমে যায়। কিন্তু কিছু কিছু বিষয় সামনে আনা দরকার।
আমি দুটি বিশেষ খবরের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রথমটি হলো, গত জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত প্রায় ১৩ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছেন আলুর দাম, পেঁয়াজের দাম ইত্যাদি চাপের কারণে। কেউ কেউ আত্মহত্যা করেছেন সরাসরি জমিতে। আরেকটা খবর হচ্ছে, ক্যান্সার হাসপাতালের সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে রোগীদের মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগ হচ্ছেন কৃষক। কেন কৃষকরাই বেশির ভাগ ক্যান্সার রোগীতে পরিণত হচ্ছে তা গুরুত্বসহকারে দেখা উচিত। আমাদের কাণ্ডজ্ঞান ও গবেষকরাও একমত হবেন যে কৃষি উৎপাদনে এখন যে ধরনের বিষাক্ত রাসায়নিক ব্যবহার করা হচ্ছে তাতেই কৃষক মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।
একদিকে পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাচ্ছেন না, অন্যদিকে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করছেন। পাশাপাশি সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে যে আমরা প্রতিদিন খাবার হিসেবে যা খাচ্ছি তাতে বিভিন্ন বিষাক্ত কেমিক্যালের উপাদান পাওয়া যাচ্ছে। আমরা বারবার নিরাপদ খাদ্য নিয়ে আলোচনা করলেও আমাদের খাদ্য তালিকায় যা আছে তা মোটেও নিরাপদ নয়; আমরা মূলত বিষ খাচ্ছি। আপনারা খেয়াল করলে দেখবেন যে খাদ্য বিষাক্ত হওয়ার সঙ্গে জিডিপি বৃদ্ধির একটা সম্পর্ক আছে।
কেননা অনেক বেশি পরিমাণে কৃষিজাত পণ্য যেমন অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন, গরু মোটাজাতকরণ প্রভৃতি উৎপাদন করতে গিয়ে আমরা বাছ-বিচারহীনভাবে রাসায়নিক ও কীটনাশক ব্যবহার করছি। ফলে উৎপাদন বেড়ে জিডিপি বাড়লেও খাবার হয়ে যাচ্ছে বিষ। আবার এসব বিষাক্ত খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়ে চিকিৎসা নিলেও জিডিপি বাড়ে। তাই আমাদের সব সরকারই যখন জিডিপি বাড়ার ফলে দেশ উন্নত হয়ে যাচ্ছে বলে যে ঢাকঢোল পেটায় সেই উন্নয়নে মানুষের জীবনমানের কোনো অগ্রগতি হয় না। বরং উন্নয়ন যে মানুষের জীবন, জীবিকা ও অস্তিত্ব খর্ব করেও হতে পারে সে দৃষ্টান্ত কিন্তু বারবার সামনে আসছে। এ পরিস্থিতিতে আমরা কৃষি, কৃষক, খাদ্যনিরাপত্তার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে কীভাবে এগিয়ে যেতে পারি তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা দরকার।
বাংলাদেশের সামর্থ্যের আলোকে কৃষি, কৃষক, খাদ্যনিরাপত্তা ও প্রাণ-প্রকৃতির মধ্যে সমন্বয় করে কখনই কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। প্রতিটি দেশের শক্তি ও সীমাবদ্ধতা আলাদা। তেমনি বাংলাদেশের শক্তির জায়গাটা হচ্ছে মাটির উর্বরতা যেখানে বীজ পড়লেই সোনা হয়ে ফুটে। সেই উর্বর ভূমি যদি রাসায়নিক ও কীটনাশক ব্যবহার করে নষ্ট করে ফেলি তাহলে আমাদের পরবর্তী জেনারেশন কোথায় চাষবাস করবে? এখানে ইলোন মাস্ক থাকলে হয়তো বলতেন, মঙ্গল গ্রহে চাষ করা হবে! বর্তমান প্রেক্ষাপটে তা তো আর সম্ভব নয়। তাই আমাদেরকে মাটিতেই চাষ করতে হবে। আমাদের আর একটা শক্তির জায়গা হচ্ছে পানি।
মাটির ওপর পানি, মাটির নিচে পানি; এ পানিসম্পদ আমাদের ঐশ্বর্য যা পৃথিবীর হাতেগোনা কয়েকটা দেশের আছে। তাই আমাদের এ বিশাল পানিসম্পদকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে। আর এ দুই শক্তি নিয়ে হাজার হাজার বছর ধরে কাজ করছে যারা—মানুষ, তারাও বাংলাদেশের অন্যতম শক্তি। আর সীমাবদ্ধতার জায়গা হচ্ছে আমাদের মানুষ বেশি, জমি কম। তাই এ তিন শক্তির সমন্বয়ে সীমাবদ্ধতাকে দূর করে কৃষি, কৃষক ও খাদ্যনিরাপত্তার উন্নয়নে কোনো সম্মিলিত প্রয়াস কখনো নেয়া হয়নি।
পাকিস্তান আমলে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের কৃষি নিয়ে কয়েক ভলিউম গবেষণাপত্র প্রকাশ করে এবং সবুজ বিপ্লব ঘোষণা করে। মূলত সবুজ বিপ্লব ছিল একটি প্যাকেজ যার মধ্যে ছিল উচ্চফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও যান্ত্রিক সেচ ব্যবস্থা। কিন্তু এ প্যাকেজ বাস্তবায়নের পরবর্তী সময়ে কী ধরনের প্রভাব পড়েছে বা এখনো পড়ছে তা নিয়ে কোনো গবেষণা নেই। এটাও সত্য যে আমাদের দেশে আরঅ্যান্ডডি (রিসার্চ ও ডেভেলপমেন্ট) অনেক কম। তাই নিজেদের স্বার্থে স্ব-উদ্যোগে কখনই কোনো গবেষণা হয় না। হ্যাঁ, যদি বিশ্বব্যাংক, ইউএনডিপি বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান উদ্যোগ নেয় তাহলে পরবর্তী সময়ে এ বিষয়ে গবেষণা হতে পারে। এ গবেষণা না হওয়ার ফলে সবুজ বিপ্লবের ফলাফল কী তা জানতে পারিনি। বণিক বার্তার মতো কোনো প্রতিষ্ঠান যদি উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসে তাহলে ভবিষ্যতে এ বিপ্লবের কস্ট-বেনিফিট অ্যানালাইসিস আমরা জানতে পারব।
এটা সত্যি আমাদের অনেক উৎপাদন বেড়েছে কিন্তু এ উৎপাদন বাড়াতে গিয়ে আমাদের কী কী ক্ষতি হয়েছে তার মূল্যায়ন করতে হবে একটি কল্যাণকর ভবিষ্যতের জন্য। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান থেকে আমরা স্বাধীন হলেও পাকিস্তান মডেল থেকে বের হতে পারিনি। সেই সেচ ব্যবস্থা, বন্যা নিয়ন্ত্রণে মাটি ও পানিসম্পদের ওপর চাপ পড়ে। এর ফলে এখানকার মানুষের স্বাস্থ্য ও জীবনমানের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।
বর্তমানে আর একটি আতঙ্কের নাম হচ্ছে শিল্প দূষণ। ঢাকার খুব কাছেই গাবতলী পার হলেই দেখতে পাবেন সেখানকার নদীর পানি কুঁচ কুঁচে কালো-কেমিক্যালযুক্ত দূষিত পানি। আবার এ নদীর পানি চাষাবাদের জন্য ব্যবহার করা হয় যা পরোক্ষভাবে আমাদের শরীরেই প্রবেশ করে মরণব্যাধি ছড়ায়। আমাদের থানা বা জেলাপর্যায়ে যেসব কারখানা আছে সেগুলোও নিয়ন্ত্রণের বাইরে। অর্থাৎ শিল্প আইন, পরিবেশ আইন ও অন্যান্য আইন থাকলেও তার যথাযথ প্রয়োগ নেই। যেমন আইনে আছে, গ্রামাঞ্চলে কৃষিজমিতে কৃষি ব্যতীত অন্য কোনো কিছু করা যাবে না। কিন্তু কৃষিজমি নষ্ট করে বহু ধরনের প্রকল্প হচ্ছে প্রশাসনের নাকের ডগায়।
অনেক গ্রামে কৃষিজমিতে ইটভাটা আছে; এতে ওই জমির মালিক কৃষক হয়তো ইমেডিয়েটলি অনেক বেনিফিটেড হচ্ছে কিন্তু অন্য কৃষক তথা আমদের মারাত্মক ক্ষতির মুখে ফেলে দিচ্ছে। আমাদের শুধু ইনডিভিজুয়াল কস্ট-বেনিফিট চিন্তা করলেই হবে না। সোশ্যাল কস্টও চিন্তা করতে হবে। আর তা করতে হবে রাষ্ট্রকে। ওই ইটভাটার কারণে ও কৃষিজমি, তার আশপাশের জমির ফলন কতটুকু নষ্ট হলো এবং ওই এলাকার অন্যান্য ফসল, শাকসবজি, গাছপালা ও ফল-ফলাদির ওপর কী পরিমাণ বিরূপ প্রভাব পড়ল তা খতিয়ে দেখার দায়িত্ব কিন্তু সরকারের। আবার মানুষের চাহিদার কারণে ইটেরও দরকার আছে কিন্তু এর বিকল্প আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। তা না করে লাইসেন্সবিহীন যত্রতত্র ইটভাটা গড়ে উঠেছে। তাই ইটভাটা ও শিল্প দূষণ আমাদের খাদ্যের বিষের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছে কয়েক গুণ।
আবার কৃষি ও পোলট্রি খাতে কয়েকটি কোম্পানি বীজ ও সারকে নিয়ন্ত্রণ করছে। অর্থাৎ হাতেগোনা কয়েকটি কোম্পানি একচেটিয়া ব্যবসা করছে। কৃষিতে এ অলিগোপলি কে রাশ টেনে ধরবে? যিনি কৃষক ফসল ফলান, তা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। আবার যথাযথভাবে সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় হিমাগারের সুবিধা নেই। অন্যদিকে সরকার যে পন্থায় কৃষিপণ্য কেনে তাতে কৃষকের তেমন লাভ হয় না। কেননা সরকার ক্রয় করে মিল মালিকদের কাছ থেকে আর মিল মালিকরা সংগ্রহ করে কৃষকদের কাছ থেকে। এতে কৃষক পণ্যের ন্যায্য মূল্য না পেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। গ্রামাঞ্চলে কৃষিকে কেন্দ্র করে কৃষি বাণিজ্যের অনেক সম্প্রসারণ হয়েছে কিন্তু কৃষির মূল কারিগর বরাবরই পেরিফেরিতে পড়ে আছে আর বিভিন্ন দেশী-বিদেশী কোম্পানিগুলোই কৃষকদের শোষণ করে লভ্যাংশ হাতিয়ে নিচ্ছে। এ পরিস্থিতি থেকে কৃষককে উদ্ধার করার জন্য সরকারকেই ক্রয় ব্যবস্থা, পরিকল্পনা ও তাদের সুরক্ষা দেয়ার বিষয়টি উদ্যোগ নিতে হবে।
পাশাপাশি সবুজ বিপ্লবের ফলে উৎপাদন হয়তো বেড়েছে কিন্তু তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমাদের স্বাস্থ্য, জীবনমান ও প্রাণ-প্রকৃতির ওপর এক ভয়ানক প্রভাব পড়েছে। আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, ১৯৯৯ সালের পর থেকে আমাদের দেশে জেনেটিক্যাললি মোডিফায়েড (জিএম) কৃষিবীজের সম্প্রসারণ ঘটে এবং ব্যাপক উৎপাদন বাড়ে কিন্তু সরকারকে একটি স্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন এবং যথাযথ নজরদারি করতে হবে যাতে সবুজ বিপ্লবের মতো আত্মঘাতী না হয়। জিএমের মাধ্যমে যে বীজই আসুক না কেন কৃষক ও দেশের সাধারণ মানুষ যেন জানতে পারে যে এ বীজ চাষাবাদের ফলে কী কী নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে এবং তথ্যের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।
আবার আমাদের উন্নয়নে সব সময়ই জনগণের কাছে ভুল ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। জনগণকে বোঝানো হয় যে কৃষিজমি নষ্ট করে কোনো মেগা প্রকল্প নেয়া হবে না, নদীর পানি নষ্ট করে এমন কোনো প্রকল্প নেয়া যাবে না বা দেশের স্বার্থবিরোধী কোনো উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে না। কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন, আমরা সবাই তা জানি। তাই শুধু মুখের বুলি না আওড়িয়ে সেসব প্রকল্পের ক্ষতিকর দিকগুলোর অবসান ঘটিয়ে এবং ভবিষ্যতে যেন আর এ ধরনের প্রকল্প না নেয়া হয়। তার মাধ্যমে নিজেদের সততা প্রমাণ করতে হবে। অন্যথায় কোনো পরিবর্তন হবে না। আজকের যিনি প্রধান অতিথি তিনি এ ব্যাপারে যথেষ্ট ভোকাল এবং তার হাত ধরেই এসব পরিবর্তনের কিছুটা হলেও সূচনা হবে।
আরো একটা উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে বীজে স্বনির্ভরতা হারানো। আমাদের নিজস্ব অনেক বীজ ছিল যা আমাদের আবহাওয়া, মাটি, পানি ও প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু সেই অমূল্য বীজগুলো যথাযথ সংরক্ষণ ও গবেষণার অভাবে হারিয়ে গেছে। এদের ফিরিয়ে আনতে হলে দেশীয় উদ্যোগে সরকার বা বেসরকারিভাবে গবেষণা করতে হবে। কেননা এখানে বিশ্বব্যাংক বা ইউএনডিপি ফান্ডিং করবে না।
পরিশেষে বলতে চাই, কৃষির উন্নয়ন এমনভাবে করতে হবে যেন কৃষক ও সাধারণ ভোক্তা উপকৃত হন। কৃষি ও প্রাণ-প্রকৃতি বাঁচলেই আমরা ভালো থাকতে পারব। আমাদের প্রত্যাশা, কৃষির সামগ্রিক উন্নয়নে অন্তর্বর্তী সরকার একটা শুভসূচনা করবে এবং বণিক বার্তার মতো অন্য অনেক প্রতিষ্ঠানের স্ব-উদ্যোগে এ ব্যাপারে জনমত গড়ে তুলবে।
আনু মুহাম্মদ: অর্থনীতিবিদ ও সাবেক অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
[বণিক বার্তা আয়োজিত কৃষি, খাদ্যনিরাপত্তা ও প্রাণ-প্রকৃতি সম্মেলনের ‘কৃষি উৎপাদন ও প্রাণ-প্রকৃতি’ বিষয়ক অধিবেশনে সম্মানিত অতিথির বক্তব্যে]