নির্বাচনের সিদ্ধান্ত অন্তর্বর্তী সরকারকেই নিতে হবে
রাজনীতি অর্থ রাজনৈতিক কাজকর্ম। রাজকার্য পরিচালনাও রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত। তবে সাধারণ অর্থে আমরা রাজনীতি বলতে বুঝি রাজার নীতি-ইকতেদার আহমেদ। সূত্র : নয়া দিগন্ত, ০৮ এপ্রিল ২০২৫
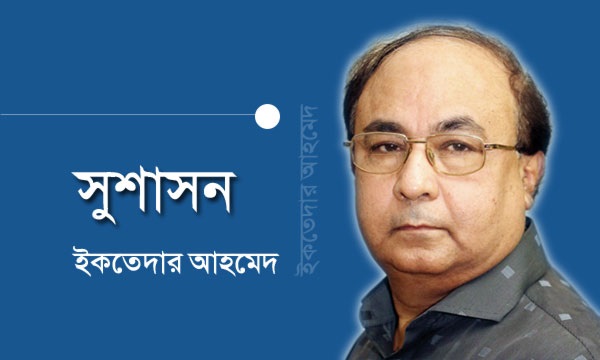
রাজনীতি অর্থ রাজনৈতিক কাজকর্ম। রাজকার্য পরিচালনাও রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত। তবে সাধারণ অর্থে আমরা রাজনীতি বলতে বুঝি রাজার নীতি। ভারত বিভাগ পূর্ববর্তী ঔপনিবেশিক শাসনামলে আমাদের উপমহাদেশের রাজ্যসমূহ বিভিন্ন মহারাজা, রাজা ও সামন্ত রাজা দ্বারা শাসিত হতো। এর আগে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন সম্রাট ও নবাবরা। মূলত উভয়ই মহারাজা বা রাজার সমার্থক। মহারাজা বা রাজা বংশানুক্রমিকভাবে ক্ষমতায় আরোহণ করায় তার প্রতি জনসমর্থন আছে কি না সে বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ভোট গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় না। রাজা দুই ধরনের। একটি হচ্ছে নামমাত্র বা আলঙ্কারিক এবং অপরটি রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী বা শাসনতান্ত্রিক প্রধান। যুক্তরাজ্য, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ডস প্রভৃতি রাষ্ট্রে রাজা নামমাত্র বা আলঙ্কারিক। অপর দিকে সৌদি আরব, জর্দান, মরক্কো, ব্রুনাই প্রভৃতি রাষ্ট্রে রাজা প্রধান নির্বাহী বা শাসনতান্ত্রিক প্রধান।
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতিটি স্বীকৃত রাজনৈতিক দল গঠনতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত হয়। গঠনতন্ত্রে দলের গঠন কাঠামো, অভ্যন্তরীণ নির্বাচনপদ্ধতি, রাজনৈতিক মতাদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রভৃতির উল্লেখ থাকে। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নিজস্ব ঘোষণাপত্র থাকে। ঘোষণাপত্রে রাষ্ট্রের তিনটি প্রধান বিভাগ যথা- আইন, বিচার ও শাসন বিভাগ, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শ্রমনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা, সন্ত্রাস নির্মূল, দারিদ্র্য বিমোচন, জলবায়ু পরিবর্তনে ঝুঁকি মোকাবেলাসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে সবিস্তারে উল্লেখ থাকে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যেসব রাজনৈতিক দল নির্বাচনে প্রতিদ্ব›িদ্বতা করে ওই সব দল সাধারণত নির্বাচনের আগে নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কী ধরনের জনকল্যাণমুখী পদক্ষেপ নিলে সাধারণ জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করা যায় সেটিকে বিবেচনায় নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো নিজ নিজ নির্বাচনী ইশতেহার প্রস্তুত করে থাকে। নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণাপত্রের সমরূপ হয়ে থাকে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে একটি দল নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনপ্রাপ্ত হলে চার-পাঁচ বছরের জন্য রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করে থাকে। প্রকৃত রাজনীতিবিদরা অর্থাৎ পেশাগতভাবে যারা রাজনীতিবিদ তারা তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে ভোট প্রার্থনা করেন। পেশাগত রাজনীতিবিদরা সাধারণত ছাত্র ও যুব সংগঠনের কর্মতৎপরতায় সম্পৃক্ততার মাধ্যমে জাতীয় রাজনীতিতে প্রবেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ধাপ অতিক্রম করেন এবং অতঃপর রাজনৈতিক দলের সদস্য হওয়ার মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজনৈতিক জীবনে পদার্পণ করেন।
রাজনৈতিক নেতা দুই ধরনের। এর একটি হচ্ছে- সাধারণ কর্মী থেকে ধীরে ধীরে যোগ্যতা প্রমাণের মাধ্যমে নেতৃত্বের আসনে আসীন হওয়া এবং অপরটি হচ্ছে- ঘটনার আকস্মিকতায় রাজনৈতিক নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ। পেশাগত রাজনীতিবিদরা যে দলের রাজনৈতিক মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করেন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় তারা আমৃত্যু সে দলের নীতি ও আদর্শের প্রতি অবিচল থাকেন। আমাদের দেশে পেশাগত রাজনীতিবিদদের মধ্যে নানামুখী লোভ, মোহ ও প্রলোভনে পড়ে কিছু কিছু রাজনীতিবিদকে এক বা একাধিকবার দল পরিবর্তন করতে দেখা যায়। আবার অনেকের মধ্যে দেখা যায় যোগ্যতা থাকা সত্তে¡ও দলে সঠিকভাবে মূল্যায়িত না হওয়ার কারণে অথবা অবমূল্যায়িত হওয়ায় দল পরিবর্তন করছেন। এমনও দেখা যায়, দলের শীর্ষ নেতৃত্বের বিরাগভাজন হয়ে দল ত্যাগ করে নতুন দল গঠন করছেন। আমাদের দেশের মতো পাশ্চাত্যে এবং উন্নত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দল ত্যাগের ঘটনা বিরল।
যখন কোনো রাজনৈতিক দল বা রাজনীতিবিদ নিজ দলের নীতি ও আদর্শের আলোকে নির্বাচন-পূর্ববর্তী জনগণের ভোটাধিকারের জন্য আবেদন করে তাকে বলা হয় ‘রাজনীতির জন্য ভোট’। অপর দিকে, কোনো রাজনৈতিক দল বা রাজনীতিবিদ দলের ও নিজের নীতি ও আদর্শের জলাঞ্জলি দিয়ে শুধু ভোটপ্রাপ্তির আশায় যখন কোনো দল বা গোষ্ঠীকে সমর্থন করে তাকে বলা হয় ‘ভোটের জন্য রাজনীতি’। এরূপ সমর্থনের মূল উদ্দেশ্য নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়া।
আমাদের দেশে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী আওয়ামী লীগের প্রতি জনসমর্থন প্রতিদ্ব›দ্বী অন্যান্য দলের তুলনায় অনেক বেশি থাকায় তখন দল ও দলের নেতারা ‘রাজনীতির জন্য ভোট’-এ মূলমন্ত্রে বিশ্বাসী হয়ে জনগণের কাছে ভোট প্রার্থনা করে অভ‚তপূর্ব বিজয় অর্জন করেছিলেন।
বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তী জামায়াতে ইসলামের রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল এবং ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে দেখা গেছে, ইসলামপন্থী দল জামায়াতে ইসলামীর শতভাগ ভোট তৎকালীন প্রধান বিরোধী দল জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) ভোটবাক্সে পড়েছিল। ১৯৭৯ সালে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচনে দেখা যায়, বিএনপি তার অনুগত দলের সমর্থন নিয়ে দুই-তৃতীয়াংশের অধিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল এবং সে নির্বাচনে মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বনকারী মুসলিম লীগ ও জামায়াতে ইসলামের সমর্থনপুষ্ট ইসলামী ডেমোক্র্যাটিক লীগ ২০টি আসন লাভ করেছিল। দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচনকালীন ১৯৭৯ সালে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর অস্তিত্ব ছিল না।
১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচন এবং বাংলাদেশ অভ্যুদয়-পরবর্তী ১৯৭৩ ও ১৯৭৯ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী ও বিজিত দলগুলো আক্ষরিক অর্থে ‘রাজনীতির জন্য ভোট’- এটিকে মুখ্য বিবেচনায় নিজ নিজ দলের নীতি ও আদর্শ জনগণের সামনে উপস্থাপন করে ভোট প্রার্থনা করেছিলেন।
১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তৎকালীন প্রধান বিরোধী দল বিএনপি অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে। এ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ১৫৩টি ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ৭৬টি আসন লাভ করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তী সর্বপ্রথম বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী নিজ দল পরিচয়ে তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ১০টি আসন লাভ করে। চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেশের প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী অংশগ্রহণ না করায় এ নির্বাচন অনেকটা একতরফা ছিল এবং জন আকাক্সক্ষার প্রতিফলনে এ সংসদ গঠিত না হওয়ায় নির্ধারিত মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার অনেক আগেই এ সংসদকে অবলুপ্ত করতে হয়েছিল।
১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ ও ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম ও নবম সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যথাক্রমে ৮৮, ১৪৬, ৬২ ও ২৩০টি আসন পেয়েছিল। উপরোক্ত চারটি নির্বাচনে বিএনপি যথাক্রমে- ১৪০, ১১৬, ১৯৩ ও ৩০টি আসন পেয়েছিল। এ চারটি নির্বাচনে জাতীয় পার্টির প্রাপ্ত আসনসংখ্যা ছিল যথাক্রমে- ৩৫, ৩২, ১৪ ও ২৭টি। অপরদিকে, ওই চারটি নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের প্রাপ্ত আসনসংখ্যা ছিল যথাক্রমে- ১৮, ০৩, ১৭ ও দু’টি।
১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ ও ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম ও নবম সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মোট প্রদত্ত ভোটের ৩০.০৮, ৩৭.৪৪, ৪০.১৩ ও ৪৮.০৪ শতাংশ ভোট প্রাপ্ত হয়েছিল।
উপরোক্ত চারটি নির্বাচনে বিএনপির ভোট প্রাপ্তির হার ছিল ৩০.৮১, ৩৩.৬০, ৪০.৯৭ ও ৩২.৫০ শতাংশ। এ চারটি নির্বাচনে জাতীয় পার্টির ভোট প্রাপ্তির হার ছিল ১১.৯২, ১৬.৪০, ০৭.২৫ ও ০৭.০৪ শতাংশ। ওই চারটি নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ভোটপ্রাপ্তির হার ছিল ১২.১৩, ০৮.৬১, ০৪.২৮ ও ০৪.৭০ শতাংশ।
উপরোক্ত চারটি নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায়- অষ্টম ও নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ও জামায়াতের ভোটপ্রাপ্তি বহুলাংশে হ্রাস পায়। শেষোক্ত দু’টি নির্বাচনে জামায়াত ৩১টি ও ৩৯টি আসনে প্রতিদ্ব›িদ্বতা করেছিল এবং অবশিষ্ট আসনে জামায়াত বিএনপিকে সমর্থন দিয়েছিল। বিশ্লেষকদের মতে, শেষোক্ত দু’টি নির্বাচনে জামায়াতের শতকরা ভোট প্রাপ্তির হার হ্রাসের এটিই মূল কারণ। অনুরূপভাবে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ৪৯টি আসনে প্রতিদ্ব›িদ্বতা করে এবং অবশিষ্ট আসনে তারা আওয়ামী লীগকে সমর্থন দেয়। বিশ্লেষকরা সীমিত আসনে প্রতিদ্ব›িদ্বতাকে জাতীয় পার্টির ভোট প্রাপ্তির হ্রাসের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন।
আলোচ্য চারটি নির্বাচনের প্রতিটিতে দেখা গেছে, সামগ্রিক জনমতের ওপর জামায়াতের নির্দিষ্ট সমর্থনের হার দেশের বৃহৎ দু’টি রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির জন্য নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে জামায়াত একবার আওয়ামী লীগের সাথে সহাবস্থান করে বিএনপির বিরুদ্ধে আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়ে নির্দলীয় তত্ত¡াবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাস্তবায়নে অগ্রণী ভ‚মিকা রাখে। অপর তিনটি নির্বাচনের একটিতে জামায়াত বিএনপির সাথে জোটবদ্ধ না হলেও আওয়ামী লীগকে ঠেকানোর মানসে যেসব আসনে তাদের প্রার্থীর বিজয় অনিশ্চিত ছিল সেসব আসনে নির্বাচনের শেষ মুহূর্তে বিএনপির প্রার্থীদের পক্ষে ভোট দিয়ে বিএনপিকে সর্বাধিক আসন প্রাপ্তিতে সহায়তা করে।
বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, জামায়াত কখনো দেশের দু’টি বৃহৎ দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মিত্র আবার কখনো বা শত্রু। কোনো কোনো নির্বাচনে দেখা গেছে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোট জামায়াতের ভোটের চেয়ে বেশি, আবার কোনো কোনো নির্বাচনে জামায়াতের ভোটের চেয়ে কম।
আওয়ামী লীগ ও বিএনপির গঠনতন্ত্র, ঘোষণাপত্র ও নির্বাচনী ইশতেহারের সাথে অনেক ক্ষেত্রেই জামায়াতের বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু উভয় দলকে দেখা গেছে, নির্বাচনে নিজেদের বিজয় নিশ্চিত করার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জামায়াতের সাথে একটি সমঝোতায় উপনীত হয়েছে। শুধু নির্বাচনে বিজয় নিশ্চিত করে ক্ষমতাসীন হওয়ার জন্য এ ধরনের সমঝোতা ‘ভোটের জন্য রাজনীতি’ হিসেবে বিবেচিত।
বাংলাদেশের রাজনীতিতে হেফাজতে ইসলাম নামক একটি অরাজনৈতিক সংগঠন ২০১৩ সালে ঢাকায় নানামুখী প্রতিক‚লতা সত্তে¡ও বাংলাদেশের স্মরণকালের ইতিহাসে বৃহত্তম গণসমাবেশ করায় ওই সংগঠনটির জনসমর্থনকে মাথায় রেখে নতুন করে হিসাব-নিকাশ শুরু হয়েছিল। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারণা ছিল, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হলে সম্মিলিতভাবে জামায়াত ও হেফাজতে ইসলামের সমর্থন যেকোনো দলের বিজয় নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে অপরিহার্য হিসেবে দেখা দেবে। আর এ কারণে হেফাজতে ইসলামকে নিয়ে নতুন ভাবনা ছিল। হেফাজতে ইসলামের সমর্থন পাওয়ার দৌড়ে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির সাথে জাতীয় পার্টিও পিছিয়ে ছিল না। হেফাজতে ইসলাম যে ১৩ দফা সরকারের কাছে দিয়েছিল তার সাথে আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির আদর্শিক রাজনীতির কোনো মিল ছিল না। কিন্তু মিল এখানে গৌণ, মুখ্য হচ্ছে- নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন। তাই অতীতের মতো আবারো দেখা গেল, ‘রাজনীতির জন্য ভোট’ নয়, ‘ভোটের জন্য রাজনীতি’। আর ‘ভোটের জন্য রাজনীতি’র এ ধারা অব্যাহত থাকলে এ দেশে সুষ্ঠু রাজনীতির বিকাশ ঘটবে কি-না সে সংশয় থেকেই যায়।
হেফাজতের আন্দোলন সামাল দেয়ার পর ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪-এ বিগত ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ তিনটি বিতর্কিত জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে অনেকটা একতরফা বিজয় হাসিল করে জনমতের বিপরীতে অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছিল। সরকারের কিছু সহায়ক বাহিনী এবং পার্শ্ববর্তী একটি রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা তাদের শাসনকালকে দীর্ঘায়িত করে। অবশেষে চাকরির কোটা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, পেশাজীবী সংগঠন এবং ছাত্র-জনতা একতাবদ্ধ হয়ে যে আন্দোলন শুরু করে তার চূড়ান্ত পরিণতিতে বিগত ক্ষমতাসীন প্রধান দেশত্যাগে বাধ্য হলে রাষ্ট্রক্ষমতায় বর্তমানে যে অন্তর্বর্তী সরকারের আগমন ঘটেছে এর পথ দুরূহ ও কঠিন। আর তাই এ সরকারটি দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনার মাধ্যমে যত শিগগির দেশের পরিচালনা ও নির্বাচন অনুষ্ঠান বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে- তাতেই নিহিত রয়েছে প্রকৃত মঙ্গল ও কল্যাণ। এর অন্যথায় অনেক কিছুই হতে পারে যা দেশের জন্য কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক হবে নাকি অকল্যাণকর ও অমঙ্গলজনক হবে- তা আগাম অনুধাবন করে বলা কঠিন।
লেখক : সাবেক জজ, সংবিধান, রাজনীতি ও অর্থনীতি বিশ্লেষক