নতুন বিশ্বব্যবস্থায় গ্লোবাল সাউথের ভূমিকা
এম এ হোসাইন [সূত্র : সময়ের আলো, ১৩ মে ২০২৫]
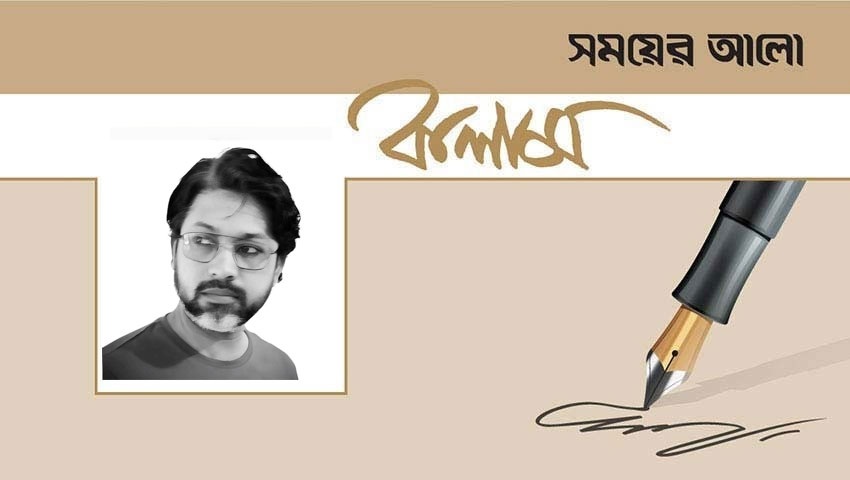
গত ৯ মে মস্কোতে পালিত হলো সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ের ৮০তম বার্ষিকী। এটি কেবল একটি ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান ছিল না; বরং এটি একটি ভূরাজনৈতিক বার্তা বহন করেছে, যার তাৎপর্য নিছক প্রতীকীর বাইরে গিয়ে বিস্তৃত। এই আয়োজনে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের উপস্থিতি এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে তার দ্বিপক্ষীয় সাক্ষাৎ। বর্তমান বৈশ্বিক রাজনীতির একটি পুনর্গঠনের আভাস দেয়- একটি পরিবর্তন, যা গ্লোবাল সাউথের আকাক্সক্ষার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠছে।
এ ধরনের অনুষ্ঠানকে খোলা চোখে অনেকে কূটনৈতিক প্রদর্শন বা পুরোনো মিত্রতার প্রতি নস্টালজিয়া বলে উড়িয়ে দিতে পারেন। কিন্তু এটি ভাবলে আসলে বর্তমান বাস্তবতা সম্পর্কে গুরুতর ভুল ব্যাখ্যা করা হবে। শি ও পুতিনের যৌথ বিবৃতিগুলো যা কৌশলগত সমন্বয়, আন্তর্জাতিক আইন ও বহুপক্ষীয়তাকে গুরুত্ব দেয়। এগুলো কেবল বক্তব্য নয়, বরং একটি গভীরতর অসন্তোষ ও সংস্কারের আহ্বান তুলে ধরে। একটি বিশ্বব্যবস্থা, যা দীর্ঘদিন ধরে শক্তিকে নীতির ওপরে এবং অন্তর্ভুক্তির বদলে বর্জনকে প্রাধান্য দিয়েছে, সেটিকে চ্যালেঞ্জ জানানো হচ্ছে।
এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া দরকার- চীন ও রাশিয়া নিখুঁত ন্যায়বিচারের ধারক নয়। তাদের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতিও যথেষ্ট সমালোচিত। কিন্তু এখানে যে প্রক্রিয়াটি চলছে তা কোনো নৈতিকতার দ্বন্দ্ব নয়, বরং একটি শক্তির ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, যেখানে ১৯৪৫ পরবর্তী বিশ্বব্যবস্থার বৈধতা সংকটের প্রতিকারে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে তাদের যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়ার প্রয়াস চলছে।
বাস্তবতা বিবেচনা করলে, গত এক দশকে যুক্তরাষ্ট্র, যাকে উদারপন্থি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার প্রধান স্থপতি ধরা হয়, তারা নিজেরাই বারবার এই ব্যবস্থাকে দুর্বল করেছে।
প্যারিস জলবায়ু চুক্তি, ইরান পারমাণবিক চুক্তি এবং ইউনেস্কোর মতো বহুপক্ষীয় কাঠামো থেকে পরপর সরকারগুলো সরে এসেছে। জাতিসংঘ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং এমনকি ন্যাটোর প্রতিও আমেরিকার সন্দেহভাব তৈরি হয়েছে, যার ফলে একটি শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে। সেই শূন্যতায় এখন বিশ্বের বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গিগুলোর প্রবেশ ঘটছে।
এই শূন্যতা গ্লোবাল সাউথের দৃষ্টিসীমার বাইরে নয়। আক্রা থেকে জাকার্তা পর্যন্ত নীতিনির্ধারকরা এখন এক পশ্চিমা নৈতিক কর্তৃত্বকে প্রশ্ন করছেন, যারা গণতন্ত্রের কথা বলে কিন্তু বাস্তবে কৌশলগত দ্বিচারিতা চালায়। একতরফাভাবে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা বা নির্বাচিতভাবে প্রয়োগ করা তথাকথিত ‘নিয়মভিত্তিক’ ব্যবস্থা- এসব বাস্তবতা দেখায় যে প্রতিষ্ঠানগুলো আন্তর্জাতিক ন্যায্যতা নিশ্চিত করার জন্য গঠিত হয়েছিল, সেগুলো প্রভাবশালীদের সুবিধায় অপব্যবহৃত হয়ে আসছে।
মস্কো থেকে ঘোষিত যৌথ বিবৃতিগুলো এই অসন্তোষের কেন্দ্রে আঘাত করে। সেগুলো জাতিসংঘের কেন্দ্রীয় ভূমিকাকে পুনঃনিশ্চিত করে, সার্বভৌম সমতার গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেয় এবং আন্তর্জাতিক আইনের অখণ্ডতা রক্ষার অঙ্গীকার করে- যেসব নীতি গভীরভাবে গুরুত্বপূর্ণ তাদের জন্য, যারা ইতিহাসজুড়ে ঔপনিবেশিক শাসন, বলপ্রয়োগ অথবা অবমূল্যায়নের শিকার হয়েছে। এই দেশগুলো বৈশ্বিক ব্যবস্থাকে উল্টে দিতে চায় না; তারা শুধু চায় সেই ন্যায্য স্থানটি, যা তাদের প্রাপ্য।
আমরা যেন এটিকে পুরোনো শীতল যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি ভেবে ভুল না করি। এটি অতীতের আদর্শিক মুখোমুখি অবস্থান নয়। আজ যা আমরা প্রত্যক্ষ করছি, তা হলো এক বহুমেরুকেন্দ্রিক সংশোধন- একটি প্রয়াস, যা বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক ও বহুধারায় সমৃদ্ধ করতে চায়। ব্রিকস, সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা কিংবা আঞ্চলিক উন্নয়ন ব্যাংকগুলোর উত্থান কোনো বিদ্রোহ নয়, বরং সময়ের দাবি। যদি প্রচলিত প্রতিষ্ঠানগুলো বৈশ্বিক শক্তির পরিবর্তনশীল বাস্তবতা ধারণে অক্ষম হয়, তবে বিকল্প কাঠামো গড়ে উঠবেই। এটি তখন কোন বিদ্রোহ নয়, বরং প্রাকৃতিক বিবর্তন।
চীনের নিজস্ব বৈশ্বিক কৌশল যেমন- বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ, গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনে সক্রিয় ভূমিকা একটি যৌথ সমৃদ্ধির দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে। এই প্রচেষ্টা নিখুঁত না-ও হতে পারে, তবে মূল ধারণার সঙ্গে দ্বিমত করা কঠিন, তা হলো আধুনিকায়ন কিছু নির্বাচিত দেশের জন্মগত অধিকার নয়, বরং এটি সব জাতির ন্যায্য আকাক্সক্ষা।
গ্লোবাল সাউথ এই বাস্তবতাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করে। চীনের অবকাঠামো উন্নয়ন, বাণিজ্যিক অংশীদারত্ব ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে অনেক দেশ বাস্তব উপকার পেয়েছে। তারা চীনের প্রতি পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গির মতো দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে না। তারা চীনকে দেখে এমন এক অংশীদার হিসেবে, যে পারস্পরিক সম্মানের ভিত্তিতে আলোচনায় প্রস্তুত- যেখানে শাসন পরিবর্তন, মতাদর্শ চাপানো কিংবা কৌশলগত অধীনতা কোনো শর্ত নয়।
নিশ্চয়ই সমালোচকরা চীনের অভ্যন্তরীণ নীতি, রাশিয়ার সামরিক কৌশল এবং উভয় দেশের কর্তৃত্ববাদী প্রবণতাকে তুলে ধরবেন। এসব উদ্বেগ যুক্তিসঙ্গত এবং খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। কিন্তু একইভাবে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে পশ্চিমা দেশগুলোর দ্বৈতনীতিও বাস্তবতা। স্বৈরশাসকদের সঙ্গে অস্ত্র চুক্তি, সার্বভৌম রাষ্ট্রে ড্রোন হামলা, অথবা সহায়তার নামে অর্থনৈতিক চাপ- এসব পশ্চিমের নৈতিক অবস্থানকে দুর্বল করে।
যদি গ্লোবাল সাউথের সামনে দুটি পথ থাকে একটি কর্তৃত্ববাদী বিশ্বব্যবস্থা, যা বিনা প্রশ্নে আনুগত্য চায় আর অন্যটি বহুমেরু বিশ্বব্যবস্থা, যা সংলাপ ও সম্মানের প্রতিশ্রুতি দেয় তবে পছন্দটা স্পষ্ট। আর এই সিদ্ধান্ত কোনো সহজ-সরল আবেগের কারণে নয়; এটি এসেছে অভিজ্ঞতার কঠোর বাস্তবতা থেকে।
এখানেই ইতিহাসের প্রেক্ষাপট গুরুত্বপূর্ণ। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ক্ষমতাধরদের খেয়ালখুশির খেলার মাঠ হিসেবে নয়, বরং একতরফা আধিপত্য রোধ করার গ্যারান্টি হিসেবে। সনদে বলা হয়েছে, কোনো জাতি যদি তারা অতি ক্ষমতাশালী হয় অন্যের ওপর ইচ্ছামতো কর্তৃত্ব করতে পারে না। আজ সেই নীতিই ক্ষয়ের মুখে, আনুষ্ঠানিক পুনর্বিবেচনার মাধ্যমে নয়, বরং অনানুষ্ঠানিকভাবে। শি ও পুতিনের বার্তা- তা সঠিক হোক বা ভুল এটিই যে এই ক্ষয় তার শেষ সীমানা অতিক্রম করেছে।
এটি কোনো তাত্ত্বিক বিতর্ক নয়। আমরা এমন এক যুগে আছি, যেখানে প্রযুক্তিগত অস্ত্র প্রতিযোগিতা, সম্পদের প্রবাহের দ্বন্দ্ব এবং পুনরুত্থিত মতাদর্শিক বিভাজন বাস্তবতা। সামরিক ঘাঁটির বিস্তার, একতরফা অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, এমনকি মহাকাশের সামরিকীকরণ পর্যন্ত ইঙ্গিত দেয় বর্তমান নিরাপত্তা কাঠামো চাপে রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে, একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ন্যায্য বিশ্বব্যবস্থা শুধু কাম্য নয় এটি অপরিহার্য।
চীন ও রাশিয়া একা নয় এই পরিবর্তনের পক্ষে। ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত, ইন্দোনেশিয়াসহ আরও অনেক দেশ এখন বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থার সংস্কার চাচ্ছে। তারা আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের নীতিনির্ধারণে অংশ নিতে চায়। তারা জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ চায়। তারা চায় আন্তর্জাতিক আইন যেন সমভাবে প্রযোজ্য হয়Ñচাই তা পূর্ব ইউরোপে হোক কিংবা মধ্যপ্রাচ্যে।
এই বৃহত্তর অঙ্গনে গ্লোবাল সাউথ আর কোনো নীরব দর্শক নয়। এটি এখন একটি সক্রিয় পক্ষ, যা কোনো মতাদর্শিক মিলের ভিত্তিতে নয়, বরং মর্যাদা, ন্যায্যতা ও কর্তৃত্বের যৌথ দাবি নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। পশ্চিমা নীতিনির্ধারকদের উচিত এটিকে হুমকি নয়, বরং নিজেদের মূল মূল্যবোধের একটি পুনরায় স্বীকৃতি হিসেবে দেখা।
এটি এক ধরনের নৈতিক বিপর্যয় যেখানে যারা গণতন্ত্রের সবচেয়ে জোরালো প্রবক্তা, তারাই বৈশ্বিক ব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণে বাধা দেয়। যদি পশ্চিমা বিশ্ব তার প্রভাব ধরে রাখতে চায়, তা হলে তারা যা প্রচার করে, সেগুলো নিজেদেরও অনুশীলন করতে হবে। এর অর্থ হলো বহুপক্ষীয়তার প্রতি নতুন করে আস্থা রাখা, উন্নয়নের একাধিক মডেলকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং আধিপত্য নয়, বরং সম্মানকে একুশ শতকের বিনিময় মুদ্রা হিসেবে মেনে নেওয়া।
প্রেসিডেন্ট শি যথার্থই বলেছেন, ইতিহাস একটি আয়না। সেই আয়নায় প্রতিফলিত হয় বিজয়ও-ভুলও। বিশ শতকের সবচেয়ে বড় দুঃখজনক ঘটনা ছিল, ক্ষমতা ভাগাভাগি না করার ব্যর্থতা। একবিংশ শতাব্দীর সুযোগ হলো সেই ভুল না করা।
মস্কোর স্মরণানুষ্ঠানটি ছিল একটি সতর্ক বার্তা যে, কী ভয়াবহ পরিণতি হতে পারে যখন বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। এর প্রেক্ষিতে যে বিবৃতিগুলো স্বাক্ষরিত হয়েছে, সেগুলো একটি প্রস্তাবনা- এই ব্যবস্থাকে নতুন করে গড়ে তোলার, একক আধিপত্যের ভিত্তিতে নয়, বরং বৈচিত্র্যময় অংশীদারত্বের ভিত্তিতে।
আর এই বৈচিত্র্যময় কাঠামোয়, গ্লোবাল সাউথকে আর প্রান্তে ঠেলে রাখা চলবে না। তাদের স্থান হতে হবে আলোচনার টেবিলে, অতিথি হিসেবে নয়, বরং পূর্ণাঙ্গ অংশীদার হিসেবে। এটিই সেই ভবিষ্যৎ, যার জন্য লড়াই করা সার্থক এবং এটিই একমাত্র পথ, যাতে করে যে শান্তি অতীতের বিপুল ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছিল, তা আর কখনো অহংকারের বিভ্রমে হারিয়ে না যায়।
লখেক: রাজনৈতিক বিশ্লেষক এম এ হোসাইন