অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে হবে
ড. মো. আবদুল বাকী চৌধুরী নবাব । সূত্র : সময়ের আলো, ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
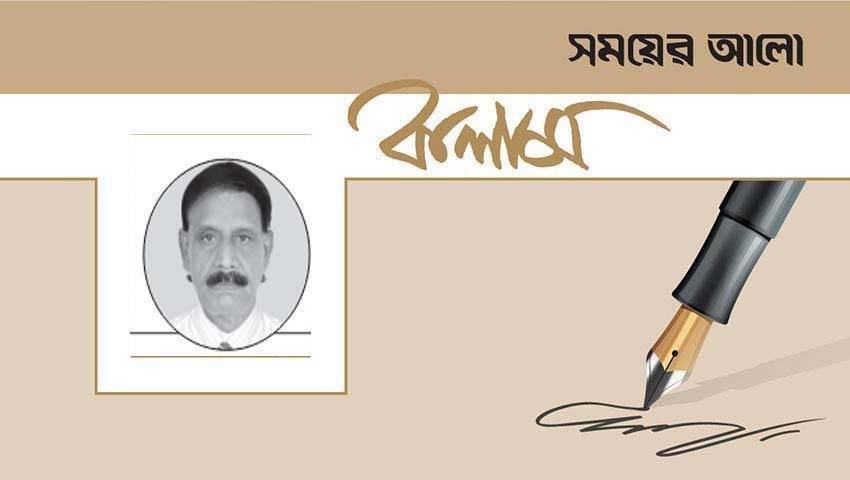
অর্থনীতির ভাষায় মূল্যস্ফীতি মেনে নেওয়া গেলেও মুদ্রা সংকোচন গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা মুদ্রা সংকোচন হলে অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়ে। এমন কোনো দেশ নেই যে, সেখানে মূল্যস্ফীতি নেই। আর অনেক ক্ষেত্রে মূল্যস্ফীতি গতিশীলতা আনে। তবে বর্ডার লাইন পার হলেই বিপদ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু বৈষম্যবিরোধী গণঅভ্যুত্থানের পরে বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতির পাশাপাশি অর্থনীতি দিনে দিনে স্থবির হয়ে পড়ছে। বর্তমান প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস হাল ধরে বিভিন্ন আঙ্গিকে তৎপর হলেও, তেমন সহযোগিতা পাচ্ছেন না; বরং নানা দাবি-দাওয়া নিয়ে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। বিশ্ব বরেণ্য এই অর্থনীতিবিদকে পেছনের দিকে টেনে ধরেছে। যখন কোনো দেশের অর্থের জোগান উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর তুলনায় অধিক হয়, তখন মূল্যস্তর বৃদ্ধি পায় এবং এ মূল্য বৃদ্ধিকেই ‘মূল্যস্ফীতি’ বলা হয়।
বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ মূল্যস্ফীতির বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। পক্ষান্তরে ‘মুদ্রা সংকোচন’ মূল্যস্ফীতির ঠিক বিপরীত অবস্থাকে বোঝায়। দেশে যখন দ্রব্যের জোগান অপেক্ষা মুদ্রার জোগান কম হয়, তখন মূল্যস্তর স্বাভাবিক অবস্থা থেকে নিম্নগতি ধারণ করে। মুদ্রা সংকোচনের সময় মূল্যস্তর, কর্মনিয়োগ ও জাতীয় আয় ক্রমশ হ্রাস পায়। এভাবে একটি দুষ্ট চক্রাকার-প্রবাহ সব অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মকে ক্রমশ নিম্নদিকে টানতে থাকে এবং প্রকারান্তরে অর্থনৈতিক প্যারামিটার স্থবির হয়ে পড়ে। যখন কোনো দেশে দ্রব্যের জোগান অপেক্ষা মুদ্রার জোগান কম হয় এবং মূল্যস্তরের ক্রমাবনতি ঘটে; তখন তাকে মুদ্রা সংকোচন বলা হয় এবং এর ফলশ্রুতিতে অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়ে।
মূল্যস্ফীতির কালে স্থবিরতা তেমন থাকে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো যে, বাংলাদেশে সেটাই দেখা যাচ্ছে। তাই স্ট্যাগফ্লেশনের কথা উঠে এসেছে। মূলত মূল্যস্ফীতি ও স্থবিরতা এই দুটি শব্দকে এক করে বলা হয় স্ট্যাগফ্লেশন। এর জনক ছিলেন একজন রাজনীতিবিদ এবং যুক্তরাজ্যের কনজারভেটিভ পার্টির সদস্য ইয়াইন ম্যাকলাও; যিনি ১৯৬৫ সালে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণনা করতে গিয়ে স্ট্যাগফ্লেশন কথাটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন। স্ট্যাগফ্লেশন হচ্ছে এমন এক অর্থনীতি, যেখানে নিম্ন প্রবৃদ্ধি, উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং বেকারত্ব একই সঙ্গে বিরাজ করে।
৫৭ বছর পর অর্থাৎ ২০২২ সালে রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণের পরে বিশ্ব অর্থনীতিতে সংকট দেখা দিলে আবারও আলোচনায় আসে স্ট্যাগফ্লেশন। সেই রাহু থেকে বিশ্ব অর্থনীতি বের হতে পারলেও বাংলাদেশ পারেনি; বলতে গেলে স্ট্যাগফ্লেশনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশ জনসংখ্যার সুবর্ণ ধাপে চলমান। আর এটি জাতির জীবনে একবারই আসে। তাই যদি স্ট্যাগফ্লেশনের মধ্যে তলিয়ে যাই; তা হলে লাতিন আমেরিকার কতিপয় দেশের মতো জাতিকে চরম খেসারত দিতে হবে।
অন্তর্বর্তী সরকার উচ্চ মূল্যস্ফীতি সাবেক সরকার থেকে ‘উত্তরাধিকার’ সূত্রেই পেয়েছে। আর এই উচ্চ মূল্যস্ফীতির যাত্রা শুরু হয়েছিল ২০২২ সাল থেকেই। সে সময় বিশ্বের অধিকাংশ দেশ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণকে প্রথম অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনায় নিলেও কর্তৃত্ববাদী সাবেক সরকার করেছিলেন উল্টোটা। সুদের হার নিয়ে নয়-ছয় অব্যাহত ছিল এবং জ্বালানি তেলের দাম একবারেই বাড়ানো হয়েছিল ৫১ শতাংশ। তাছাড়া নির্দেশ মতো কেন্দ্রীয় ব্যাংক টাকা ছাপিয়ে সরকারকে ঋণ দেওয়া অব্যাহত রাখে, বাজারেও ছিল না কার্যকর। শুধু তাই নয়, ছিল না নজরদারি, কেবল লম্বা লম্বা মতলববাজি কথা; যেমন রোল মডেল ও ডিজিটাল বাংলাদেশসহ উন্নয়নের চটকদারি উক্তি।
তা ছাড়া বিপর্যস্ত হয় সরবরাহ ব্যবস্থা। সরকার আশীর্বাদপুষ্ট কতিপয় প্রভাবশালী ব্যবসায়ীর দৌরাত্ম্য এতটাই বাড়ে যে, রেকর্ড পরিমাণ ঋণখেলাপি হয় এবং লাখ লাখ টাকা অবাধে পাচার হয়। সত্যিকার অর্থে সাবেক সরকারের একের পর এক ভুল নীতির ফলেই হয়েছিল উচ্চ মূল্যস্ফীতি। এদিকে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার গত ৮ আগস্ট (২০২৪) যখন দায়িত্ব নেয়। তখন দেশে মূল্যস্ফীতি ছিল ১১ দশমিক ৬৬ শতাংশ। এর মধ্যে ছয় মাসের বেশি সময় চলে গিয়েছে। সেই মূল্যস্ফীতি সামান্য কমে হয়েছে ১০ দশমিক ৮৯ শতাংশ। কিন্তু অর্থনীতির স্বার্থে আরও কমানো সমীচীন ছিল।
করোনাকালে দেশের মোট দেশজ উৎপাদনে গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ৬ দশমিক ৭১ শতাংশ। সে সময়ও বেসরকারি বিনিয়োগের হার প্রায় এক জায়গাতেই আটকে ছিল। যেমন ২০১১-১২ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) বেসরকারি বিনিয়োগের অংশ ছিল ২২ দশমিক ৫০ শতাংশ। আর ২০২৩-২৪ অর্থবছরে তা মাত্র ১ শতাংশ বেড়ে হয় ২৩ দশমিক ৫১ শতাংশ। এই পুরো সময়টা ছিল কর্মসংস্থানহীনসহ তথাকথিত প্রবৃদ্ধির বড় একটা উদাহরণ। এদিকে মেগা প্রকল্পসহ সরকারি ব্যয় বাড়িয়ে উন্নয়নের চটকদার কথা বলা হলেও এ সময়ে আয়বৈষম্য বেড়েছে সবচেয়ে বেশি।
তা ছাড়া কিছু কিছু মেগা প্রকল্প আমাদের আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে অনুকূল ছিল না বিধায় অযথা খরচ বাড়িয়ে মূল্যস্ফীতির দিকে কয়েক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে। মূলত উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে সবচেয়ে দুরবস্থা বলতে গেলে সেই অপরিণামদর্শী বিনিয়োগের কারণে হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। এদিকে চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসের (জুলাই-ডিসেম্বর) জন্য বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছিল ৯ দশমিক ৮ শতাংশ।
অথচ বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ২০২৪ সালের নভেম্বরে এই প্রবৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ৭ দশমিক ৬৬ শতাংশ। বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির এই হার গত সাড়ে তিন বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। সাবেক সরকারের ছত্রছায়ায় যথেচ্ছাচার লুট হওয়ায় ব্যাংকগুলো একদিকে যেমন অর্থসংকটে ঋণ দিতে পারছে না, অন্যদিকে আস্থার অভাবে বেসরকারি খাতও অনেকটা হাত গুটিয়ে চুপচাপ বসে আছে। ফলে বিনিয়োগ মোটেও বাড়ছে না।
উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো শৃঙ্খলা এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীলসহ এর প্রয়োগ। আইন ও শৃঙ্খলার প্রতি মনোযোগী হওয়া সমীচীন এবং যুগপৎ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সুষ্ঠু প্ল্যাটফর্ম তৈরিপূর্বক আস্থা আনার দিকে নজর দেওয়া উচিত। সামাজিকমাধ্যমে অপপ্রচার তুঙ্গে। শুধু দেশে নয়। ষড়যন্ত্রের আড়ালে এই অপপ্রচার দেশের বাইরে থেকেও করা হচ্ছে। কথায় কথায় দাবির টর্নেডো আঘাত হানছে। শুধু তাই নয়, ভোট তথা নতুন নির্বাচিত সরকারের ব্যাপারে নানামুখী কথা বলা হচ্ছে। এদিকে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা পূর্বের ন্যায় বহাল তবিয়তে আছে। তাই এতদিক থেকে আসা চাপ সরকারের পক্ষে সামলাতে হচ্ছে।
জুলাই-নভেম্বর সময়ে বিনিয়োগের জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ পুঁজি যন্ত্রপাতির আমদানি কমেছে ২৯ দশমিক ২০ শতাংশ। আরও খারাপ চিত্র নভেম্বর পর্যন্ত। মূলত মূলধনি যন্ত্রপাতি আমদানি কমার অর্থই হচ্ছে, দেশে নতুন বিনিয়োগ নিম্নমুখী। তবে বস্ত্র খাত সম্পর্কিত বিভিন্ন পণ্যের আমদানি বেড়েছে, যার প্রভাব দেখা যাচ্ছে পোশাক রফতানিতে। এদিকে কেবল বেসরকারি বিনিয়োগই নয়, কমে গেছে সরকারি বিনিয়োগও। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য অনুযায়ী ২০২২ সালের জানুয়ারির পর থেকে ২০২৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতি মাসেই মূল্যস্ফীতির তুলনায় মজুরি বৃদ্ধির হার ছিল কম অর্থাৎ টানা তিন বছর দেশের মানুষের প্রকৃত আয় কমছে।
নতুন বিনিয়োগ হচ্ছে না বলে নতুন কর্মসংস্থানও সৃষ্টি হচ্ছে না। এতে বাড়ছে না প্রকৃত আয়। এর প্রভাব পড়ছে অর্থনীতির সার্বিক প্রবৃদ্ধিতে। মূলত রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ব্যবসা-বাণিজ্যে শ্লথগতির কারণে প্রবৃদ্ধি কমেছে। কেবল সুখবর পরিলক্ষিত হচ্ছে রফতানি ও প্রবাসী আয়সহ বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ বা রিজার্ভের ক্ষেত্রে। বিগত সরকার থেকে পাওয়া রিজার্ভের অব্যাহত ধস ঠেকানো সম্ভব হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে প্রবাসী আয়ে প্রবৃদ্ধি প্রায় ২৬ শতাংশ এবং রফতানি আয়ে প্রবৃদ্ধি ১০ শতাংশের বেশি। এদিকে বিনিময় হার বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। দুর্নীতি ও অর্থ পাচারের অভিযোগে বড় বড় কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া তথাকথিত পরিবারসহ ১১টি বড় প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম তদন্তের জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। যদিও পাচার করা অর্থ ফেরত আনা সময়সাপেক্ষ। এই কর্মকাণ্ডের জন্য ইউনূস সরকার প্রশংসা পাওয়ার দাবিদার।
এর মধ্যে বেশ কিছু বড় প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি শ্লথ হয়ে পড়েছে। অনেক প্রকল্প নতুন করে যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। তাছাড়া বাজার তদারকির অভাব এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের ছন্দপতন আরেক বিড়ম্বনা। এ অবস্থায় সরকার গঠিত শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি লিখিতভাবে অর্থনীতি স্থিতিশীল করার পরিকল্পনাসহ সাত দফা সুপারিশ করেছিলেন। অথচ জানা যায় যে, কমিটির কোনো সুপারিশই নাকি আমলে নেওয়া হয়নি। আমাদের দেশের কাঁচা শাকসবজির একটি কালচার বিদ্যমান। অনেক সময় দেখা যায় কাঁচা শাকসবজির দাম অগ্নিমূল্য। কিন্তু ভরা মৌসুমের সময় এত দাম কমে যায় যে, উৎপাদন খরচও উঠে আসে না, যা ভালো দিক নয়। এতে কৃষকরা নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েন এবং পরবর্তী বছরে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।
এদিকে চাল উৎপাদনের সবচেয়ে বড় মৌসুমে বোরো আবাদে মাঠে নেমেছেন কৃষক। বোরো থেকে আসে দেশের ৬০ শতাংশ চালের জোগান। ক্রমবর্ধমান উৎপাদন খরচের কারণে ধান আবাদ টিকিয়ে রাখা দরিদ্র কৃষকের কাছে দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, বোরো মৌসুমে কৃষিতে বাড়তি মনোযোগ না দিলে কৃষি অর্থনীতিতে দেখা দিতে পারে দুই ধরনের সংকট। উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ায় কৃষকের ন্যায্য দাম পাওয়া নিয়ে এক ধরনের চাপ তৈরি হতে পারে। আবার বাজারে চালের দাম বাড়লে দরিদ্র ও সীমিত আয়ের মানুষের খরচ বাড়বে। কারণ ‘দিন আনে দিন খায়’ মানুষের আয়ের বড় অংশ খরচ হয় চালের পেছনে, যা মূল্যস্ফীতিকে উসকে দিয়ে থাকে।
যেভাবেই বলি না কেন, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পরে গঠিত সরকারের ওপর সবারই প্রত্যাশা ছিল ব্যাপক। যে নীতিগুলো নেওয়া হবে, তা সবার সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে হবে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে থাকবে স্বচ্ছতা, সূক্ষ্ম নজরদারি করা হবে বাজারের ওপর, কমবে মূল্যস্ফীতি, কমে যাবে দুর্নীতির প্রকোপ, উন্নতি হবে আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি, কমবে দখল ও চাঁদাবাজি। তাই সেই আদলে একবার যদি স্ট্যাগফ্লেশন শেকড় গেড়ে বসে, তা হলে তাকে উপড়িয়ে ফেলা অতটা সহজসাধ্য নয়।
দেশ ভালো অবস্থায় আনার ব্যাপারে সরকারের সদিচ্ছার অভাব নেই। দেশের প্রায় ১৮ কোটি লোকের ব্যক্তিস্বার্থ ভুলে গিয়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে এগিয়ে আসতে হবে। নতুবা এর ফলাফল আমাদের ওপর এসে ভর করবে। বর্তমানে এমন অবস্থায় দাঁড়িয়েছে যে, জিডিপি ও প্রবৃদ্ধির সঙ্গে কেবল অর্থনৈতিক সূচক সংশ্লিষ্ট নয়। এর সঙ্গে পরোক্ষভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক সূচকও জড়িত। তাই কোনো কিছুই খাটো করে দেখার অবকাশ নেই।
লেখক : সাবেক শিক্ষক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়