প্রসঙ্গ : পণ্যের শুল্ক বাড়ানো
শাহ মো. জিয়াউদ্দিন । সূত্র : ভোরের কাগজ
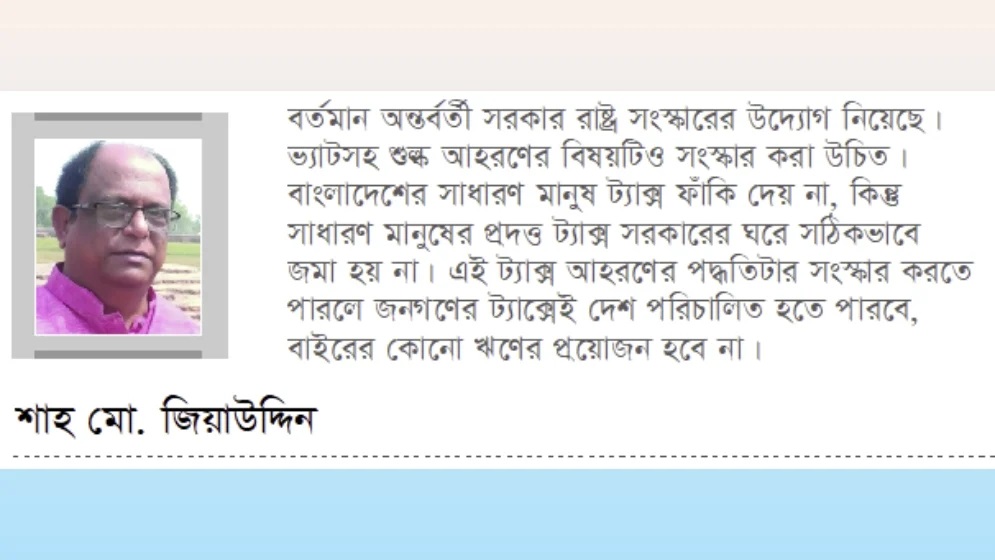
সরকার বিভিন্ন পণ্য ও সেবার ওপর ভ্যাট-ট্যাক্স বাড়িয়েছে। গত ৯ জানুয়ারি রাতে শুল্ক বাড়ানো সংক্রান্ত দুটি অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে। এই অধ্যাদেশের একটি হলো মূল্য সংযোজন কর ও অন্যটি সম্পূরক শুল্ক অধ্যাদেশ, যা দি এক্সাইজ অ্যান্ড সল্ট (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০২৫। এই দুটি অধ্যাদেশ জারির পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) ভ্যাট বিভাগ এ-সংক্রান্ত একটি নির্দেশনা জারি করে, ফলে সরকারের শুল্ক আদায়ের পরিবর্তন করা বিষয়গুলো কার্যকর হয়ে গেল। বর্তমানে জাতীয় সংসদ নেই, তাই অধ্যাদেশ দিয়েই শুল্ক বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।
এই শুল্ক বৃদ্ধিটা হয়েছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফের চাপে। আইএমএফ বাংলাদেশকে ৪৭০ কোটি ডলার ঋণ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আর এই ঋণের পরিপ্রেক্ষিতে আইএমএফ শুল্ক বাড়ানোর শর্ত প্রদান করে। তাই সরকার অর্থবছরের মাঝপথে এসে ১০০টি পণ্য ও সেবার ওপর শুল্ক কর বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়। দেশে বর্তমানে চলছে উচ্চ মূল্যস্ফীতি। বর্তমানে খাদ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতির হার দুই অঙ্কের উপরে। যা অতীতের অনেক রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে।
এই সময়টায় শুল্ক বাড়ানোটা মূল্যস্ফীতির হার বাড়ানোর ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। অর্থাৎ ক্রমবর্ধমান পণ্যের মূল্য আরো বেড়ে যাবে। দেশে জিনিসপত্রের দাম বাড়ার কারণে প্রান্তিক আয়ের মানুষ শুধু নয়, মধ্যবিত্তরা সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছে। আর নতুন করে কর বাড়ানোটা অনেকটা গোদের ওপর বিষফোড়া ওঠার মতো।
সরকার পোশাক শিল্পের ৭.৫ হারের শুল্ক বৃদ্ধি করে নির্ধারণ করেছে ১৫ শতাংশ। রেস্তোরাঁর ভ্যাট ৫ শতাংশ বাড়িয়ে করা হয়েছে ১৫ শতাংশ। মিষ্টির ওপর ৭.৫ শতাংশ কর বাড়িয়ে করা হয়েছে ১৫ শতাংশ। টিস্যুর ওপর ৭.৫ ভ্যাট বাড়িয়ে করা হয়েছে ১৫, এলপি গ্যাসের ৫ শতাংশ বাড়িয়ে করা হলো ৭.৫, আচার চাটনি ৫ শতাংশ বাড়িয়ে করা হলো ৭.৫, বিস্কুটের ৫ শতাংশ বাড়িয়ে করা হলো ১৫ শতাংশ। এর সঙ্গে সরকার ভ্রমণ কর বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, দেশের অভ্যন্তরে ৫০০ টাকা বাড়িয়ে ৭০০ টাকা, সার্কভুক্ত দেশগুলোর ক্ষেত্রে ৫০০ টাকা বাড়িয়ে করা হলো ১ হাজার, এশিয়ার দেশগুলোর জন্য ২ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ২ হাজার ৫০০, বিশ্বের অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে ৩ হাজার থেকে ৪ হাজার টাকা।
দেশের বর্তমান আর্থিক প্রেক্ষাপটে এই শুল্ক বাড়ানোটা কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে তা ভাববার বিষয়। কারণ দেশের প্রান্তিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির কোনো প্রকার আয় বাড়েনি। যে কোনো কর আরোপ করা হোক না কেন, করের যে করাঘাত তার বোঝাটা টানতে হয় দেশের প্রান্তিক মানুষের। আইএমএফের ৪৭০ কোটি ডলার ঋণে দেশের উৎপাদন কতটা বাড়বে। যদি বাড়ে, এই বাড়ার সুফলটা প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষ কতটা পাবে তা ভেবে দেখার প্রয়োজন। যদি প্রান্তিক মানুষ তার ফল ভোগ করতে না পারে তাহলে এভাবে কর বৃদ্ধি করাটা ঠিক হয়নি।
দেশের আধুনিক কর আদায়ের পদ্ধতি হলো ভ্যাট। এই ভ্যাটের আওতায় দেশের একজন ভিক্ষুকও সরকারকে শুল্ক দিচ্ছেন। কিন্তু তার প্রদত্ত শুল্কটা কতটা সরকারের ঘরে জমা হচ্ছে তা কি মনিটরিং করা হয়। একজন ভিক্ষুক তার গায়ে পরার জন্য একটি স্যান্ডু গেঞ্জি কিনলেন একজন বিক্রেতার কাছ থেকে, ওই বিক্রেতা ভিক্ষুকের কাছ থেকে ভ্যাটসহ গেঞ্জির মূল্যটা নেন, কিন্তু ভ্যাটের সিøপ ভিক্ষুক পান না। ভিক্ষুক আদৌ জানলেন না তার প্রদত্ত ভ্যাট সরকারের ঘরে জমা হলো কিনা। এই ভিক্ষুকের সংসারের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য তেল, চিনি, লবণসহ অন্যান্য পণ্যেরও ভ্যাট তিনি প্রদান করেন।
এত শুল্ক দেয়ার পরও তিনি রাষ্ট্রের কাছ থেকে কতটুকু সেবা পেয়ে থাকেন তা পরিমাপ করা দরকার। শুধু ভিক্ষুক নন, রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কর দিয়ে থাকেন। জনগণের প্রদত্ত করে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালিত হয়। অথচ সরকারি প্রতিষ্ঠানে গেলে জনগণ প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের কাছ থেকে যে ব্যবহারটা পান, তার আর বর্ণনা না দিলাম।
নিজেদের সরকারি কর্মকর্তা দাবি করে ঘরের ভেতরে প্রয়োজনে যাওয়া লোকদের ঢুকতে দেয় না। তা ছাড়া মাঠ পর্যায়ে ভ্যাট আদায় বিষয়টি অত্যন্ত জটিল ও কঠিন বিষয়। যেমন রেস্তোরাঁর ক্ষেত্রে ভ্যাট ৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে করা হলো ১৫ শতাংশ। দেশের কয়টি রেস্তোরাঁয় মূসক সংবলিত যন্ত্রের মাধ্যমে ভোক্তাকে ক্যাশমেমো দেয়া হয়? এর একটি পরিসংখ্যান থাকা দরকার। কারণ সারাদেশে কয়েক লাখ রেস্তোরাঁ রয়েছে, তার ১০ শতাংশেরই মূসক সংযোজন করা স্বয়ংক্রিয় ক্যাশমেমো দেয়ার মেশিন নেই। কোথাও কোথাও দেখা যায় কাগজের রসিদের ভোক্তাকে ক্যাশমেমো প্রদান করা হয়।
এই মেমোতে ঠিকই ভ্যাট নেয়া হয়। এই ভ্যাটটা কি সরকারের তহবিলে জমা পড়ে? মাঠ পর্যায়ের ভ্যাট আদায়বিষয়ক কিছু পরিদর্শক কাজ করেন, যাদের এতদ বিষয়েও তেমন একটা ধারণা নেই। শোনা গেছে এই মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শকরা দোকানের দৈনিক বিক্রির গড় হিসাব করে দোকান ভেদে ভ্যাট নির্ধারণ করে দেন। এই বিষয়টা কতটা যৌক্তিক হচ্ছে। এভাবে কর আদায়ের বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন দোকানিকে বলাবলি করতেও শোনা যায়, ভ্যাট পরিদর্শককে কিছু দিলে মাসিক ভ্যাটটাও কম নির্ধারণ করা যায়। সারাদেশে যে পরিমাণে ভ্যাট আদায় হয় তার সবটাই কি সরকারি কোষাগারে জমা হয়?
এখানে মধ্যস্বত্বভোগী কাজ করে। মধ্যস্বত্বভোগী যেমন কৃষকের উৎপাদিত পণ্যে ভাগ বসায় ঠিক তেমনি জনগণের প্রদেয় ভ্যাটটাও এনবিআরের কর্মীদের পকেটস্থ হয়। যেমন মানিকগঞ্জে কৃষকের কাছ থেকে কেনা ৪০ টাকার লাউ ঢাকায় এসে ১০০ টাকা বিক্রি হয়, ঠিক তেমনি সাধারণ মানুষের দেয়া কোটি কোটি টাকার একটি ক্ষুদ্র অংশ সরকারের কোষাগার পায়। ভ্যাট ও শুল্ক নিয়ে অসাধুতার বিষয়টি দেখা যায় ফ্যাসিবাদী হাসিনা সরকারের আমলে এনবিআরের কর্মকর্তার ছাগলকাণ্ডের পর। তখন নানা অনিয়মের কথা গণমাধ্যমে প্রচার হয়েছে।
দেশের মানুষ কষ্ট করে ভ্যাট দেন আর এই ভ্যাট নিয়ে এ ধরনের খেলাটা বন্ধ করা দরকার। রাজশাহীতে জনৈক ভ্যাট কর্মকর্তার বিষয়ে শোনা যায়, তিনি ইটভাটাগুলোকে কত ভ্যাট দিতে হবে তা নির্ধারণ করে দেন। এই ক্ষেত্রে ভ্যাটের পরিমাণটা নির্ভর করে তার সঙ্গে ভাটা মালিকের কতটা সখ্যতা আছে তার ওপর। প্রতিটি ইট বিক্রি হলে ইটভাটা ক্রেতার কাছ থেকে ভ্যাটের নির্ধারিত টাকাটা নেবেন, অবিক্রীত ইটের ওপর তো তার ভ্যাট দেয়ার কথা না, তাহলে কী করে মাসিক বা একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকার ভ্যাট ভাটার মালিকের ওপর আরোপিত হবে।
বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো নির্মাণকারী সরকারি ঠিকাদাররা সরকারকে ভ্যাট প্রদান করেন। এদের ভ্যাট প্রদান অনেকটা এক মুরগিকে দুবার জবাই করার মতো। যেমন ঠিকাদার যখন রড, সিমেন্ট, ইট, বালি কেনেন তখন তিনি ভ্যাট দিয়ে এই সামগ্রী কিনে থাকেন। তারপর যখন সরকারের কাছ থেকে তিনি বিল নেয়ার জন্য বিল জমা দেন তখনো তার কাছ থেকে ভ্যাট কাটা হয়। তাই দেখা যায় একজন ঠিকাদার একটি ইটের ওপর দুবার ভ্যাট দেন, প্রথমবার দেন ভাটা থেকে কেনার সময়, আরেকবার দেন তার বিল সরকারের কাছ থেকে নেয়ার সময়। ঠিক তেমনিভাবে রড, সিমেন্ট, রং ও অন্যান্য নির্মাণসামগ্রীর বেলায়ও এই ঘটনাটি ঘটছে। পদ্ধতিগত কিছু বিষয়ের কারণে ঠিকাদাররাও অসাধু হয়ে ওঠে।
বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার রাষ্ট্র সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে। ভ্যাটসহ শুল্ক আহরণের বিষয়টিও সংস্কার করা উচিত। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ ট্যাক্স ফাঁকি দেয় না, কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রদত্ত ট্যাক্স সরকারের ঘরে সঠিকভাবে জমা হয় না। এই ট্যাক্স আহরণের পদ্ধতিটার সংস্কার করতে পারলে জনগণের ট্যাক্সেই দেশ পরিচালিত হতে পারবে, বাইরের কোনো ঋণের প্রয়োজন হবে না।
শাহ মো. জিয়াউদ্দিন : কলাম লেখক।