সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও বাংলাদেশ
ড. মাহফুজ পারভেজ [প্রকাশ : যুগান্তর, ১৮ আগস্ট ২০২৫]
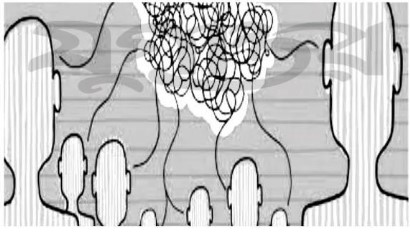
সাংস্কৃতিক আগ্রাসন (Cultural Aggression) বলতে বোঝায় এমন একটি পরিস্থিতি, যেখানে একটি শক্তিশালী বা প্রভাবশালী সংস্কৃতি অন্য একটি দুর্বল সংস্কৃতির ওপর তার প্রভাব চাপিয়ে দেয় বা তা প্রতিস্থাপনের চেষ্টা করে। এটি সরাসরি দখলদারত্বের মাধ্যমে হতে পারে অথবা পরোক্ষভাবে; যেমন-গণমাধ্যম, শিক্ষাব্যবস্থা, পণ্যসংস্কৃতি (Consumer Culture), প্রযুক্তি বা রাজনৈতিক প্রভাবের মাধ্যমে হতে পারে। ফলে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন বলতে বোঝায় এক দেশের সংস্কৃতি বা জীবনধারা অন্য দেশের শক্তি বা সংস্কৃতির প্রভাবে ধ্বংস, প্রভাবিত বা বিকৃত করার প্রক্রিয়া। এটি সাধারণত মিডিয়া, বিনোদন, ফ্যাশন, ভাষা, শিক্ষা ও প্রযুক্তির মাধ্যমে ঘটে থাকে। সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নীতি ও কৌশলের মাধ্যমেও আগ্রাসন হতে পারে।
ঢালাওভাবে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন নিয়ে কথা বলার আগে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মূল তত্ত্ব ও ধারণা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার দরকার।
সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ : এ তত্ত্ব অনুযায়ী, পশ্চিমা বিশ্বের (বিশেষ করে আমেরিকার) সংস্কৃতি গ্লোবাল মিডিয়া, ফ্যাশন, সিনেমা, খাদ্য সংস্কৃতি ও প্রযুক্তির মাধ্যমে পৃথিবীর অন্য দেশগুলোতে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর মূল তাত্ত্বিক Herbert Schiller। তিনি বলেন, গ্লোবাল মিডিয়া পশ্চিমা শক্তির হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ভিত্তি তৈরি করে।
গ্রামশির হেজেমনি তত্ত্ব : গ্রামশি মনে করেন, একটি শক্তিশালী শ্রেণি বা রাষ্ট্র অন্য শ্রেণি বা রাষ্ট্রের ওপর প্রভুত্ব স্থাপন করে থাকে ‘সাংস্কৃতিক হেজেমনি’র মাধ্যমে। এটি কেবল রাজনৈতিক নয়, বরং সাংস্কৃতিকভাবে ‘সহমত’ তৈরির মাধ্যমে ঘটে। যেমন-পশ্চিমা জীবনধারাকে ‘আধুনিকতা’ হিসাবে উপস্থাপন করে অন্য সংস্কৃতিকে ‘পিছিয়ে পড়া’ হিসাবে দেখানোর বিষয়টি আগ্রাসন ছাড়া আর কিছু নয়।
উপনিবেশ-পরবর্তী তত্ত্ব : এ তত্ত্ব অনুসারে, উপনিবেশের যুগ শেষ হলেও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে সাবেক ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো এখনো প্রভাব বিস্তার করছে। পণ্ডিত Edward Said তার বিশ্বখ্যাত ‘Orientalism’ বইয়ে দেখিয়েছেন কীভাবে পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গি প্রাচ্যকে ‘অন্য’ হিসাবে তুলে ধরে। যার ভিত্তিতে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন নব্য উপনিবেশবাদের (Neocolonialism) অংশ হিসাবে আবির্ভূত হয়।
সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মূল হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয় মিডিয়াকে। চলচ্চিত্র, নাটক, টিভি, ওয়েভসিরিজ, সোশ্যাল মিডিয়া, বিজ্ঞাপন ইত্যাদির মাধ্যমে ধীরে ধীরে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালিয়ে একটি জাতি বা জনগোষ্ঠীর চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, অভ্যাস-এসব বদলে দেওয়া হয়। একইভাবে ভোগ্যপণ্য; যেমন-ফ্যাশন ব্র্যান্ড, খাদ্য সংস্কৃতি (ফাস্টফুড) ইত্যাদির মাধ্যমে জীবনাচরণের মৌলিক বদল ঘটানো হয়। শিক্ষাব্যবস্থা সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে। শিক্ষার মাধ্যমে উপনিবেশিক ধ্যান-ধারণার প্রসার ঘটানো হলে জাতিগত পরিসরে ও নাগরিক পর্যায়ে অবদমিত ও নতজানু মানসিকতার বিস্তার ঘটে। এতে শিক্ষার হাত ধরে বিদেশি ভাষা ও সংস্কৃতির আধিপত্যে মাতৃভাষা ও নিজস্ব সংস্কৃতির অবমূল্যায়ন সাধিত হয়।
সাংস্কৃতিক আগ্রাসন একটি সূক্ষ্ম, কিন্তু গভীর প্রক্রিয়া; যা দীর্ঘমেয়াদে একটি জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয়কে ক্ষুণ্ন করতে পারে। এটি কেবল বাহ্যিক প্রভাব নয়, বরং একটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক কৌশলও বটে।
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের রূপ ও চরিত্র নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। এখানে ভাষাগত আগ্রাসন, পোশাক ও জীবনধারায় বিকৃতি, মিডিয়া ও বিনোদন জগতের কাজ-কারবার ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের পথ মসৃণ করছে এবং জাতীয় সংস্কৃতির হানি ঘটাচ্ছে। পরিবর্তিত খাদ্য সংস্কৃতিও বাংলাদেশের লোকজ খাদ্যাভ্যাসকে বিপন্ন করে তুলেছে। এর ফলে জাতীয় পরিচয়ের সংকট সৃষ্টি হচ্ছে। নাগরিকদের, বিশেষত তরুণ প্রজন্মের মূল্যবোধ ও আচার-আচরণে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বিভ্রান্তি ও অনুকরণপ্রবণতা ব্যাপক আকারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। একইসঙ্গে সাংস্কৃতিক ও জাতীয় আচরণের মধ্যে বিকৃতি এবং জাতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির অবমূল্যায়ন ঘটছে।
এ ধরনের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন প্রতিরোধে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ও নিজস্বতা রক্ষায় জনগণকে সচেতন করা অত্যন্ত জরুরি। জাতীয় সংস্কৃতির অংশ লোকসংগীত, নাটক, সাহিত্য, উৎসব ইত্যাদিকে উৎসাহিত করা দরকার। শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠ্যবইয়ে নিজস্ব ইতিহাস ও সংস্কৃতি আরও বেশি তুলে ধরা অপরিহার্য। তদুপরি, মিডিয়াকে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিষয়ে সতর্ক থাকবে হবে এবং দেশীয় সংস্কৃতিভিত্তিক কনটেন্ট তৈরি ও প্রচারে বেশি মনোযোগী হতে হবে। যাতে নাগরিক সমাজ, বিশেষত তরুণদের মধ্যে নৈতিকতা, জাতীয়তা ও সাংস্কৃতিক অহংবোধ পরিগঠিত হয়।
সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন ও সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা সবিশেষ জরুরি। পরিবারে, ঘরে, পাড়ায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনমূলক কার্যকলাপের পথ রুদ্ধ করা সবার নৈতিক দায়িত্বের অংশ। পাশাপাশি জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতির বিকাশের স্বার্থে নিজস্ব অনুষ্ঠান প্রচলন ও এর ভিত্তিতে মানুষকে যুক্ত করে সামাজিক আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়া আবশ্যক। বস্তুতপক্ষে, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন মোকাবিলায় সবাইকে সচেতন হতে হবে এবং দায়িত্বশীল ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।
ব্যক্তির পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় সংস্কৃতি রক্ষায় সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব যেমন আছে, তেমনি দায়িত্ব রয়েছে রেডিও-টিভি চ্যানেলগুলোর এবং বাংলা একাডেমি, শিল্পকলা একাডেমি, এফডিসি-এ ধরনের সংস্থার। এসব সংস্থা এক্ষেত্রে কতটুকু কাজ করছে, তা না বলাই ভালো। ফ্যাসিবাদী আমলের মানসিকতা ও জনবিচ্ছিন্ন আমলাতান্ত্রিক বিচ্ছিন্নতা থেকে অনেক সংস্থা এখনো বের হতেই পারেনি। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন যে বর্তমান বিশ্বে একটি নীরব ও কৌশলগত যুদ্ধ, এ বোধটুকুও অনেক সংস্থার কর্তাব্যক্তিদের নেই। এটি গোলাবারুদ দিয়ে নয়, বরং বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তিতে মোকাবিলা করার বিষয়, তা অনুধাবন করার মতো দূরদর্শিতা সংস্থাগুলোর শীর্ষে অবস্থানকারীদের মাথায় অনুপস্থিত।
প্রতিনিয়ত মিডিয়া, ফ্যাশন, সিনেমা, শিক্ষা ও বিনোদনের মাধ্যমে জাতির চিন্তা-চেতনা, জীবনধারা, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও জাতীয় ঐতিহ্যকে আক্রমণ করার ঘটনাগুলো থেকে অনুধাবণ করা যায়, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মুখে কত অসহায়। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন কেবল আন্তর্জাতিক দিক থেকেই ধেয়ে আসছে না, আঞ্চলিক ক্ষেত্র থেকেও অবিরাম আঘাত আসছে। বাংলাদেশের মতো একটি স্বাধীন, শান্তিপূর্ণ ও ঐতিহ্যভিত্তিক মূল্যবোধসম্পন্ন দেশে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন বিশেষভাবে উদ্বেগজনক ঘটনা। এ আগ্রাসনের প্রতিরোধে বাংলাদেশকে আত্মপরিচয়ের আলোকে মূল্যবোধ ও বিশ্বাস থেকে, দেশপ্রেম ও ঐতিহ্যের গৌরবে উজ্জীবিত হয়ে সামনের দিকে পরিচালিত করা সম্ভব হচ্ছে। সম্ভব হচ্ছে না আগ্রাসনের বিপরীতে একটি আত্মনির্ভর, আত্মপরিচয়সম্পন্ন বাংলাদেশের স্বপ্নকে বেগবান করা।
কেন হচ্ছে না, সে কারণ কারও অজানা নয়। বাংলাদেশের সমগ্র নেতৃত্ব বর্তমানে মশগুল নির্বাচন ও সংস্কার নিয়ে। সবার দৃষ্টি কেন্দ্রভূত ক্ষমতার চৌকাঠে। মতাদর্শভিত্তিক ক্ষেত্র থেকে শিল্প, সংস্কৃতি, সমাজ নিয়ে ভাবার অবকাশ অনেকেরই নেই। জাতির মনন ও সংস্কৃতির পুষ্টি সাধন ও আগ্রাসন থামানোর বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার ফুসরত পাচ্ছেন না নেতারা।
এর ফলে রাজনৈতিক দামামা ও ক্ষমতা ঢংকায় দেশের নিজস্ব সংস্কৃতি দুর্বল হচ্ছে। ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের অবক্ষয় হচ্ছে, যে ধারা অব্যাহত থাকলে জাতির আত্মপরিচয় সংকটের সম্মুখীন হতে পারে। এছাড়া, সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের কারণে সামাজিক অস্থিরতা, অপরাধপ্রবণতা এবং মানসিক বৈকল্য সর্বত্র নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এ কথা মনে রাখা দরকার, যখন একটি শক্তিশালী সংস্কৃতির প্রভাব একটি দুর্বল সংস্কৃতির ওপর পড়ে, তখন সেই দুর্বল সংস্কৃতির নিজস্ব ঐতিহ্য, রীতিনীতি এবং মূল্যবোধগুলো ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে থাকে। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের শিকার হয়ে মানুষ নিজের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য থেকে দূরে সরে যেতে পারে। বিশেষত, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন অনেক সময় রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের একটি মাধ্যম হিসাবেও কাজ করে, যা স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে। অতএব, এমন একটি জরুরি বিষয়ে উদাসীন থাকা শুধু বেদনাদায়কই নয়, বিপজ্জনকও বটে।
সবচেয়ে মারাত্মক যে বিপদ সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের কারণে হতে পারে, তা হলো রাজনৈতিক ক্ষতি। কারণ, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন কেবল একটি সমাজের ভাষা, পোশাক বা জীবনধারাকে প্রভাবিত করে না-এটি ধীরে ধীরে জাতীয় রাজনীতি, নীতি-নৈতিকতা ও শাসনব্যবস্থারও অবক্ষয় ঘটাতে পারে। কীভাবে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রাজনৈতিক অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে যেতে পারে, তা অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন-জাতীয় চেতনার দুর্বলতা ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের দুর্বলতা। যখন একটি জাতি সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ফলে নিজের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও আত্মপরিচয় ভুলে যেতে থাকে, তখন জাতীয়তাবাদী চেতনা দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে রাজনীতিকদের মধ্যে দেশপ্রেম ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা কমে যায়। এতে দেশে রাষ্ট্রনায়ক নয়, সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদ জন্ম নেন।
সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের কারণে নীতি-নৈতিকতার অবক্ষয় ঘটে। এতে পশ্চিমা সংস্কৃতির ভোগবাদী ও আত্মকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি রাজনীতিতে প্রবেশ করে রাজনীতি একটি মূল্যবোধহীন ক্ষমতার খেলায় পরিণত হয়। এ কারণে সেবামূলক নেতৃত্বের পরিবর্তে স্বার্থনির্ভর নেতৃত্ব গড়ে ওঠে। পাশাপাশি দুর্নীতির স্বাভাবিকীকরণ, নৈতিক বিচ্যুতি, ক্ষমতার অপব্যবহার চলতে থাকে।
সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ফলে যখন নেতা ও জনগণ ভোগবাদী ও নির্লিপ্ত হয়ে ওঠে, তখন তারা রাজনৈতিক সচেতনতা হারায়। ফলে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে। এসব মৌলিক বিষয়ে খেয়াল করার অবস্থা নেতাদের থাকে না। এতে রাজনীতিতে একনায়কতন্ত্র বা ছদ্মগণতন্ত্রের উত্থান ঘটে।
সাংস্কৃতিক আগ্রাসন বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষাব্যবস্থায় পরাধীনতার উদ্ভব ঘটায়। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ফলে শিক্ষাব্যবস্থা ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণি অনেক সময় বিদেশি চিন্তাধারার অনুকরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে নিজস্বতা ও জাতীয় স্বার্থ ত্যাগ করে। তারা দেশীয় বাস্তবতা ও সমস্যার সমাধান না করে বিদেশি মডেল কপি করতে থাকে। ফলে দেশীয় সমস্যার যথাযথ সমাধান হয় না, রাজনীতিতে বুদ্ধিবৃত্তিক দিশাহীনতা তৈরি হয়। পরনির্ভরশীলতা ও বিদেশের প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধি পায়।
নৈতিক নেতৃত্বের সংকট তীব্রতর হয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের কারণে। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন যেহেতু মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটায়, তাই সমাজ থেকে নৈতিক ও আদর্শনিষ্ঠ নেতৃত্ব হারিয়ে যায়। এর বদলে জনপ্রিয়তা বা মিডিয়া ইমেজই হয়ে ওঠে রাজনৈতিক যোগ্যতার মানদণ্ড এবং ফলস্বরূপ শুদ্ধ রাজনীতির বদলে পপুলিজমের (জনগণের আবেগ নিয়ে খেলা) রাজনীতির বিস্তার ঘটে; যা দেশ ও জনগণের জন্য কল্যাণকর হয় না।
সামগ্রিক বিবেচনায় সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের কারণে সৃষ্ট ক্ষতির অন্ত নেই। রাজনীতি থেকে শুরু করে সমাজ এবং ব্যক্তি পর্যন্ত এ কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জাতীয় ঐতিহ্য ও স্বার্থ ভূলুণ্ঠিত হয়। বস্তুত সমৃদ্ধ অর্থনীতি, সুশাসন এবং টেকসই গণতন্ত্রের চর্চা-এসব ক্ষেত্রে ঘাটতি দেখা দিলে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মাত্রা তীব্র আকার ধারণ করতে পারে। অতএব, চলমান সংকুল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নির্বাচন ও সংস্কারের সমান্তরালে বিদেশনির্ভরতা, পরমুখাপেক্ষিতা তথা সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিষয়েও সর্বোচ্চ সচেতনতা ও মনোযোগ দেওয়ার বিষয়টি সংশ্লিষ্টদের এড়িয়ে যাওয়া মোটেই সমীচীন হবে না।
প্রফেসর ড. মাহফুজ পারভেজ : চেয়ারম্যান, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়