স্থিতিশীল রাজনৈতিক কাঠামো জরুরি
ড. মো. শামসুল আলম । সূত্র : প্রতিদিনের বাংলাদেশ, ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
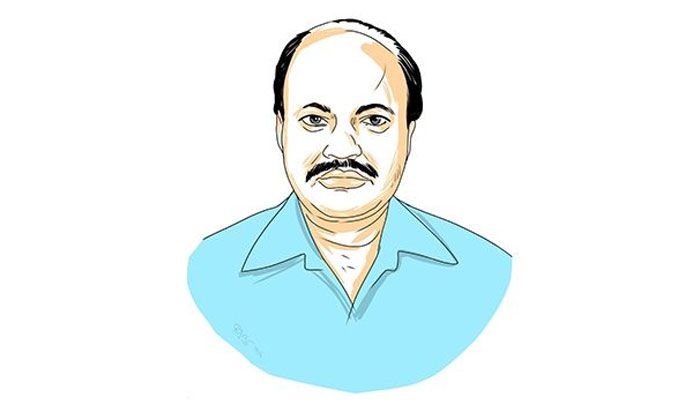
জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থঅন পরবর্তী রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর চারদিকে শুধু দাবি আর দাবি। দীর্ঘদিন বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছে, এখন আর নয়; যেন এটাই হয়ে উঠেছে দেশের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও জনজীবনের নিত্যদিনের চিত্র। সবারই কিছু না কিছু চাই এবং প্রতিটি দাবিই গুরুত্বপূর্ণ। এত দাবির ফলে অর্থনীতি অনিশ্চয়তার পথে ধুঁকছে। সম্প্রতি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিতে রাজধানীর মহাখালীর তিতুমীর কলেজের শিক্ষার্থীদের অবরোধ ও অনশন কার্যক্রমে সারা দেশেই দুর্ভোগ ও ভোগান্তি বাড়ে। যেহেতু দেশে যাতায়াতের মাধ্যম সীমিত এবং রেলওয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ গণপরিবহন অবরোধের কারণে বন্ধ ছিল, তাই স্বাভাবিকভাবেই জনদুর্ভোগ বেড়েছে।
অন্তর্বর্তী সরকার চাকরিজীবী, পেশাজীবী, ব্যবসায়ী, শ্রমজীবীসহ নানা স্তরের মানুষের বিভিন্ন দাবির মুখে রয়েছে। নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর নিজ নিজ দাবি আদায়ে রাস্তায় নামে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে সচিবালয়, প্রেস ক্লাব, শাহবাগ ও প্রধান উপদেষ্টার বাসভবনের আশপাশ ঘিরে বিভিন্ন কর্মসূচি থাকায় এসব এলাকায় পথচারী এবং যানবাহন চলাচল ব্যাহত হয়। নানা প্রয়োজনে রাজধানীতে ছুটে চলা মানুষকে এক ধরনের ভোগান্তির মধ্যে ফেলে দিয়ে দাবি আদায়ের চেষ্টা করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষ আকস্মিকভাবে অবরোধ বা যানজটের মধ্যে পড়ছে। অনেক সময় এসব পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে আটকে যাচ্ছে মরণাপন্ন রোগী বহনকারী অ্যাম্বুলেন্সসহ জরুরি সেবার যানবাহনও। বিভিন্ন দাবির আন্দোলনে ক্লান্ত রাজধানী। অবস্থাটা এমন যে, রাজধানী যেন এখন আর এ আন্দোলনের ভার বহন করতে পারছে না।
বিদায়ি আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে জনসাধারণ তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও রাজনৈতিক আতঙ্কের মুখে ছিল। কিন্তু পটপরিবর্তনের পর দীর্ঘদিনের চাপা অস্বস্তি থেকে মানুষ মুক্তি পেয়েছে। গত বছর ৫ আগস্ট সরকারের পতনের পর দেশে সংস্কারের লক্ষ্যে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেয়। এ সংস্কার রাষ্ট্রের অসঙ্গতি দূর করে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামো সুগঠিত করে একটি দৃষ্টান্তমূলক নির্বাচন আয়োজনের মাধ্যমে জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেÑ এ প্রত্যাশা এখনও সবার মনে। সঙ্গে নির্বাচন আয়োজনের আগে প্রত্যাশিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার কার্যক্রমের বাস্তবায়ন। কিন্তু দীর্ঘদিন রাষ্ট্রকাঠামোয় জেঁকে বসা অসঙ্গতি দূর করার জন্য স্থিতিশীল রাজনৈতিক কাঠামো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
যদি তা নিশ্চিত না করা যায়, তাহলে সংকট উত্তরণের পথ নেই। বরং তাতে ক্রমেই জটিলতা বাড়ে যেমনটি রাজধানীতে দেখা যাচ্ছে। জননিরাপত্তাজনিত নানা সমস্যার পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে দাবিদাওয়া ও বিক্ষোভ সামাল দেওয়ার কাজ করতে হচ্ছে। এসব নানাভাবে সরকারের কাজের গতিতেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এমন সময়ে দেশের রাজনৈতিক দলগুলো মানুষকে আশ্বস্ত করতে পারে। কিন্তু তেমনটিও খুব মোটা দাগে দেখা যাচ্ছে না। বরং দেশের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলোকে নানা সমীকরণের হিসাবনিকাশেই ব্যস্ত থাকতে দেখা যাচ্ছে।
ভুলে গেলে চলবে না, অন্তর্বর্তী সরকার কোনো রাজনৈতিক সরকার নয়। তারপরও নানারকম দাবির মুখে তাদের ওপর রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের চাপ ক্রমেই বাড়ছে। যে প্রেক্ষাপটে এ সরকার দায়িত্ব নিয়েছে, সেখানে ঢালাওভাবে যে ধরনের দাবির আন্দোলন চলছে তার অধিকাংশই যৌক্তিক নয়। সামাজিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণে এসব স্বাভাবিকও নয়। একই সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারেরও দুর্বলতা বোঝা যাচ্ছে। যেমন এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা অটোপাসের দাবি নিয়ে আন্দোলন শুরু করলেন, তারা সচিবালয়ে গেলেন, সরকারও তাদের দাবি সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিল। এর পর থেকে আরও বিভিন্ন খাতের লোকজন আন্দোলনে নামল, তাদেরও কারও কারও দাবি মেনে নেওয়া হলো। এভাবে যারা মনে মনে চিন্তা করছিলেন, তারাও দাবির আন্দোলনে নামছেন।
এসব মিলিয়ে এখানে সরকারের বিচক্ষণতা, দক্ষতা ও সমন্বয়ের যথেষ্ট অভাব দেখা যাচ্ছে। এ সংকট সমাধানের জন্য অন্তর্বর্তী সরকারকে তাই আরও সতর্ক হতে হবে। বিশেষত অস্থিতিশীলতা চিহ্নিত করে দ্রুত রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সম্মিলিত উদ্যোগে কাজ করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলো অন্তর্বর্তী সরকারকে রাজনৈতিক সরকারের ঘাটতি অনেকাংশে পূরণ করতে সহযোগিতা করতে পারে। রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা ও পারস্পরিক আস্থা গড়ে তোলার এ সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। আলোচনার টেবিল যখন সবার জন্য উন্মুক্ত হবে তখন সব কাজই সহজ হয়ে উঠবে।
সরকার ও রাজনীতি অধ্যয়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা তিন ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। এত দাবি ও আন্দোলনের পেছনে সমাজের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাই প্রকটভাবে দায়ী। রাষ্ট্রের কাছে যখনই কোনো দাবি করা হয় তখন তা অবধারিতভাবেই রাজনৈতিক হয়ে ওঠে। যদিও রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক এ শব্দদ্বয়ের ব্যবহারে অনেক সূক্ষ্ম পার্থক্য গড়ে ওঠে। কিন্তু যে মোড়কেই দাবি করা হোক, এসব দাবি রাজনৈতিক রূপই নেয়। বিশ্বব্যাংকের রাজনৈতিক সমীক্ষা বলে একটি শাখা রয়েছে। বৈশ্বিক আর্থিক এ প্রতিষ্ঠান এমন একটি শাখা খুলেছে যাতে তারা কোনো রাষ্ট্রে বিনিয়োগ করলে তাতে রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে কোনো ক্ষতি হবে কি না তা খতিয়ে দেখতে পারে।
বিশ্বব্যাংক রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বোঝার ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছেÑ রাজনৈতিক সহিংসতা এবং বিক্ষোভ কর্মসূচি। দেশে জননিরাপত্তা নানাভাবে বিঘ্নিত। আমরা দেখছি সম্প্রতি কিশোর গ্যাংয়ের দাপট বেড়েছে। অর্থাৎ তারা নিজেদের রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতায়িত করছে। আর এসবের ফলে তারা ছুরি, ছিনতাইসহ নানা অপরাধে যুক্ত হচ্ছে। রাষ্ট্রকে খতিয়ে দেখতে হবে, এসব গোষ্ঠীর পেছনে কোনো প্রভাবশালী বা রাজনৈতিক তৃতীয় পক্ষ রয়েছে কি না। হাত দিতে হবে শেকড়ে। না হলে উপরিতলের অবস্থা দেখে কিছুই বোঝা সম্ভব হবে না। দ্বিতীয়ত, দেশে এত দাবি ও বিক্ষোভ হচ্ছে যা অযৌক্তিক। অর্থাৎ রাষ্ট্রে সামাজিক পর্যায়ে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা প্রভাব ফেলছে।
রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে প্রশাসনসহ সরকারের কাঠামোতেও। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাকে আমরা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নীতিগতÑ এ তিন ভাগে ভাগ করতে পারি। এ তিনটি ক্ষেত্রে অস্থিতিশীলতা রাষ্ট্রের সক্ষমতা, কার্যক্ষমতা এবং জনসেবার পরিসর সংকুচিত করে তুলছে। যেহেতু অন্তর্বর্তী সরকার রাজনৈতিক সরকার নয়, তাই তাদের জন্য এ সংকোচন ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। এ সংকোচনের ক্ষেত্রে আমরা সরকার ও রাজনীতি অধ্যয়নে বারোটি প্রভাবক চলকের কথা বলতে পারি। এ বারোটি চলক হচ্ছে সরকারের স্থিতিশীলতার অবস্থা, আর্থসামাজিক পরিস্থিতি, দেশে বিনিয়োগের পরিমাণ বা অবস্থা, অভ্যন্তরীণ সংঘাত, দুর্নীতি, রাজনীতিতে সামরিক প্রভাব, ধর্মীয় অসন্তোষ ও সংঘাত, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, সংখ্যালঘু জাতিসত্তার নানা সংকট, গণতান্ত্রিক জবাবদিহি এবং আমলাতন্ত্রের স্বচ্ছতা।
আমরা যদি এ বারোটি বিষয় ধরে ধরে আমাদের দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রশাসনিকভাবে দেখতে চাই, তাহলে দেখব অন্তত ৯ থেকে ১০টি প্রভাবক চলক বিদ্যমান। আর্থসামাজিক অবস্থা মূল্যস্ফীতির কারণে বিপর্যস্ত। সরকারের স্থিতিশীলতা এত দাবির মুখে নড়বড়ে এবং বিশ্বদরবার এমনকি অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগকারীরাও এখনই নতুন কিছু গড়ার বিষয়ে আশ্বস্ত নন। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ক্রমেই নাজুক হচ্ছে। এখনও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাদের শক্তিমত্তা ও আইন প্রয়োগের সক্ষমতা ফিরে পায়নি।
গণতান্ত্রিক জবাবদিহির চর্চা রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নেই। ধর্মীয় অসন্তোষ এবং সংখ্যালঘুদের এক ধরনের সাংঘর্ষিক পরিস্থিতি আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতে আরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। সবার শেষে আমলাতন্ত্রের ভেতরেও কোথাও স্বচ্ছতার অভাবের অভিযোগ উঠছে। ক্ষমতার পালাবদলে দেশ পরিচালনার দায়িত্বে আসা অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কারের প্রতিশ্রুতির মধ্যে পদত্যাগের হিড়িক পড়েছিল; আন্দোলনকারীদের চাপের মুখে সরে যেতে হয়েছে প্রধান বিচারপতিকে, পদ ছেড়েছেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ আরও অনেকে। আবার প্রশাসনে আমরা অনেককে পুনর্বাসন এবং গণপদোন্নতি দিতে দেখেছি। এসবের ফলে প্রশাসনের পিরামিড কাঠামো গেছে উল্টে। আর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে প্রশাসনিক কার্যক্রমে।
অর্থাৎ অন্তর্বর্তী সরকারের সামনে এখন পাহাড়সম চ্যালেঞ্জ। এত দাবি সামলানোর দিকে তারা মনোযোগ দেবে, নাকি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের দিকে তাদের ঝুঁকতে হবে? তারা কি নির্বাচন আয়োজনের কাজটি সুসম্পন্ন করবে, নাকি তাদের সংস্কারের কাজ করবে? প্রতিটি বিষয়ই আলাদাভাবে মনোযোগের দাবি রাখে। ফলে অন্তর্বর্তী সরকারের সামনে এখনও অনেক কাজ বাকি। এসব কাজ করতে হবে দ্রুত। কারণ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা যত বাড়বে অন্তর্বর্তী সরকারের শত সদিচ্ছা থাকার পরও তা বাস্তবায়নের কাজ সম্পন্ন করার পথে অসংখ্য প্রতিবন্ধকতা তৈরি হবে।
কিন্তু দেশে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি সুসংগঠিত করার কাজটি যদি আন্তরিকভাবে করা যায় এবং রাজনৈতিক দলগুলোকে অবিশ্বাস ও অসহযোগিতামূলক আচরণ থেকে সরিয়ে এনে একটি স্থিতিশীল মঞ্চ গড়া যায় তাহলে উপকৃত হবে দেশ। একই সঙ্গে সামাজিক সচেতনতাও বাড়াতে হবে। সরকারের সক্ষমতা এবং তাদের অবস্থানের বিষয়টি মানুষকে বোঝাতে হবে। সব দাবি চাইলেই অন্তর্বর্তী সরকার পূরণ করতে পারবে না। এসব দাবি আদায়ের জন্য যে রাজনৈতিক সরকার জরুরি তা আনার জন্যও সময় প্রয়োজন। তাই অনেক ভেবেচিন্তে পা ফেলতে হবে অন্তর্বর্তী সরকারকে। আমরাও চাই তারা একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে উঠুক। কারণ অনেক প্রত্যাশা ও ত্যাগের মাধ্যমে একটি নিরপেক্ষ সরকারকাঠামো গড়ে উঠেছে। নানা অস্থিতিশীল চলকের কারণে তাদের কার্যক্রম যেন কোনোভাবেই বিঘ্নিত না হয়। সেজন্য রাজনৈতিক দলকেও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।
- রাজনীতি-বিশ্লেষক ও অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়