ট্রাম্পের শুল্ক আরোপে আমেরিকার ক্ষতি
ল্যারি এলিয়ট । সূত্র : সময়ের আলো, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
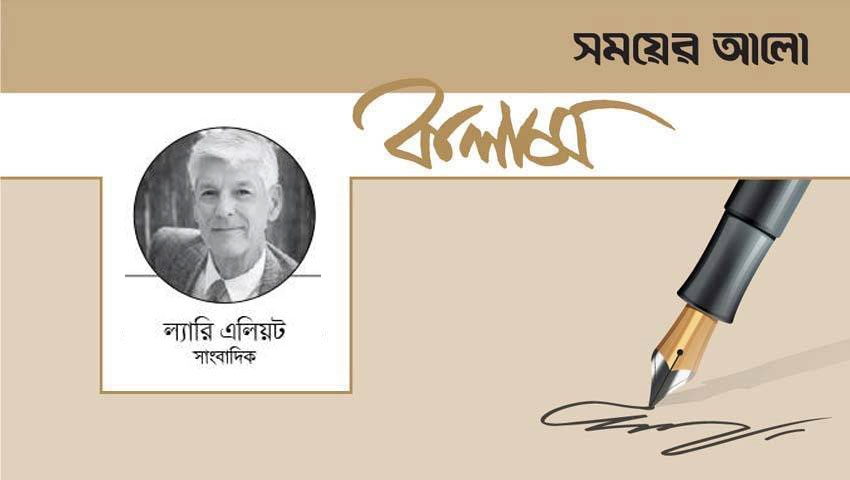
সম্প্রতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের বিভিন্ন দিক নিয়ে দ্য গার্ডিয়ান পত্রিকায় নিজের একটি মতামত প্রকাশ করেন ল্যারি এলিয়ট লেখক ও সাংবাদিক। সময়ের আলোর পাঠকের জন্য লেখাটি অনুবাদ করেছেন কৃপাসিন্ধু পাল। বাণিজ্য যুদ্ধের সূচনার ঘটনাগুলো ঘটা শুরু হয়ে গেছে। বহুপক্ষীয়তা তার শেষ পর্যায়ে রয়েছে। বিশ্বায়নকে পিছিয়ে নেওয়া হচ্ছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে ফিরে আসার এক মাসও হয়নি, আর তিনি তড়িঘড়ি শুরু করছেন। তিনি যেন সমগ্র বিশ্বে একটা যুদ্ধ ছড়িয়ে না দিয়ে থামবেন না।
প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেওয়ার পর থেকেই ট্রাম্প ব্যস্তভাবে বিশ্বব্যবস্থাকে নতুন করে গড়ে তুলছেন। প্রচলিতভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যেভাবে দেখা যায়, তাদের সেসব নীতি থেকে বের হতে শুরু করেছেন। মার্কিন বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে শুল্ক ব্যবহারের সিদ্ধান্তটি শিরোনাম কাড়লেও, সেটাই পুরো গল্পের অর্ধেক মাত্র। তিনি জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে বেরিয়ে গেছেন এবং মার্কিন সাহায্য বিভাগকে (ইউএসএইড) দুর্বল করে দিয়েছেন। এমনকি রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে এমন কথাও শোনা যাচ্ছে যে, তিনি হয়তো বিশ্বব্যাংক থেকেও যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে নিতে পারেন। বিশ্বব্যাংক হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় গঠিত হয়েছিল।
যদিও তিনি এত বড় পদক্ষেপ থেকে পিছু হটেন, তবু বৈশ্বিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লড়াইয়ের অনেক নিয়ম বদলে যাবে। কয়েক দশক ধরে, মার্কিন বাণিজ্য ঘাটতি বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তি ছিল। চীন ও জার্মানির মতো বড় রফতানিকারক দেশ যুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর পরিমাণে পণ্য বিক্রি করত; কিন্তু তাদের বিশাল বাণিজ্য উদ্বৃত্তের একটি বড় অংশ যুক্তরাষ্ট্রের সম্পদ, যেমন স্টক মার্কেটের শেয়ার, বন্ড ও সম্পত্তি কিনতে ব্যবহার করত। যুক্তরাষ্ট্রে মূলধনের প্রবাহ ডলারের অবস্থানকে দৃঢ় করেছিল, এসব কারণে আজও বিশ্বব্যাপী প্রধান সংরক্ষিত মুদ্রা হিসেবে ডলারের আশপাশে আর কোনো দেশের কোনো মুদ্রা নেই।
ট্রাম্প বলছেন, এই চিত্র বদলাতে হবে এবং তিনি আমদানি কমিয়ে মার্কিন বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস করতে শুল্ক প্রয়োগ করার পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত। তিনি এটিকে যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি প্রদর্শন হিসেবে দেখছেন, যদিও বাস্তবে এটি ওয়াশিংটন ডিসির উদ্বেগেরই প্রতিফলন যে, চীনের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ক্ষমতা মার্কিন আধিপত্যের জন্য হুমকি হয়ে উঠছে।
ট্রাম্প যা যা করেছেন, তার কিছুই আশ্চর্যজনক নয়। ‘আমেরিকাই সবার আগে’ নীতির ভিত্তিতে রক্ষণশীল প্রচারণা চালিয়ে তিনি তার ভোটারদের জন্য প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করেছেন। তার জনপ্রিয়তা এখনও উঁচুতে, সাম্প্রতিক এক জরিপে ৭০ শতাংশ মানুষ বলেছেন, তিনি নির্বাচনের আগে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেগুলোই এখন ক্ষমতায় গিয়ে পূরণ করছেন।
তবে এখনও ট্রাম্পের ক্ষমতায় আসার পর খুব কম সময় অতিবাহিত হয়েছে। একই জরিপে দেখা গেছে, আমেরিকার নাগরিকরা মনে করেন যে ট্রাম্পের নীতিগুলো খাদ্যের দাম কমানোর বদলে বাড়াবে এবং এ নিয়ে উদ্বেগ যথার্থ। নতুন প্রশাসনের বাণিজ্য নীতি উচ্চ আমদানি মূল্য, উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি এবং উচ্চ সুদের হারের দিকে নিয়ে যেতে পারে। মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চেয়ারম্যান জেরোম পাওয়েল স্পষ্ট করে জানিয়েছেন যে, ঋণের সুদহার কমানোর কোনো তাড়াহুড়োয় তারা নেই।
পাওয়েলের সুদের হার কমানোর বিষয়ে সতর্কতা অনিচ্ছাকৃত পরিণতির আইনের একটি উদাহরণ মাত্র। ট্রাম্প চান ডলার যেন বৈশ্বিক মুদ্রা হিসেবে তার প্রভাব ধরে রাখে; কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি ক্রিপ্টোকারেন্সি, যেমন- বিটকয়েনের ব্যবহারকে উৎসাহিত করবে। শুল্কের ব্যবহার, আর্থিক সহায়তা কমানো এবং বহুপক্ষীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি স্পষ্ট বিরাগ, এসবই এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোকে বেইজিংয়ের প্রস্তাবগুলোর প্রতি আরও গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারে। এক অর্থে বলা যায়, ট্রাম্প কেবল একটি প্রবণতাকে ত্বরান্বিত করছেন। ২০০৮ সালের বৈশ্বিক আর্থিক সংকটের পর থেকেই দেশগুলো চুপিসারে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাধা তৈরি করছে। বছরের পর বছর ধরে, চীনের রফতানিকারকদের জন্য প্রদত্ত ভর্তুকির কারণে যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদন খাতের চাকরি হারিয়ে যাচ্ছে। যদি কখনো বহুপক্ষীয় সহযোগিতার স্বর্ণযুগ থেকে থাকে, তবে তা অনেক আগেই শেষ হয়েছে।
গত মাসে এক বক্তৃতায় ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের গভর্নর অ্যান্ড্রু বেইলি বলেছিলেন, পরিস্থিতি সত্যিই ভয়াবহ হয়ে উঠলে, যেমনটা ২০০৮ সালে হয়েছিল, তবেই সম্মিলিতভাবে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার ইচ্ছা দেখা যায়। ‘ঝুঁকিগুলো বাড়ছে এবং প্রয়োজনীয় সমাধানগুলোর পরিসর বৈশ্বিক হলেও সেগুলো এখনও এত গভীর নয় যে, তা সংকটকালে বহুপক্ষীয় উদ্যোগের দিকে ঠেলে দেবে এবং আমরা সেটি চাই না।’ তা ছাড়া দেখা যায়, বড় কোনো সংকটের সামনে না পড়লে দেশগুলো একত্রিত হয়ে কাজ করতে রাজি নয়। বরং ছোটখাটো সমস্যা সব দেশ নিজে নিজে সমাধান করতে ইচ্ছুক।
তবে এটি খুব সহজেই ঘটতে পারে। মুক্তবাজার অর্থনীতির বিশেষজ্ঞরা যুক্তি দেন যে, ট্রাম্পের শুল্ক নীতির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত রফতানিকারক দেশগুলোর উচিত প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে সংযত থাকা। কারণ শুল্ক আসলে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ভোক্তাদের ওপর একটি কর, যা পণ্যের দাম আরও বাড়িয়ে দেবে। কোনো পণ্যের দাম বেশি হয়ে গেলে তার বিক্রি কমে যাবে এবং ক্ষতির মুখোমুখি হবে যুক্তরাষ্ট্রের বিক্রেতারা। তারা তখন নিজেদের বিক্রি তথা লাভ বৃদ্ধির জন্য একই মানের একই পণ্য কিনতে ছুটবে অন্য সেসব দেশের দিকে যাদের ওপর শুল্ক বসানো হয়নি।
তবে ট্রাম্পের সুনজরে থাকতে আগ্রহী যুক্তরাজ্যকে বাদ দিলে বাস্তবে বিশ্ব এমনভাবে চলে না। বাস্তবে এটি ‘চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত’ নীতির মতোই হতে পারে। ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ এবং চীনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং দুজনেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে তারা ট্রাম্পের চাপের কাছে নতিস্বীকার করবেন না। একটি পূর্ণাঙ্গ বাণিজ্যযুদ্ধ এখনও এড়ানো যেতে পারে। যদিও ট্রাম্প এই সপ্তাহের শুরুতে সব স্টিল ও অ্যালুমিনিয়াম আমদানির ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক ঘোষণা করেছেন, এ দুটি পণ্য বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের মাত্র একটি ক্ষুদ্র অংশ গঠন করে। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ, বিশেষ করে ট্রাম্প কি সব পণ্যের ওপর সর্বজনীন শুল্ক আরোপ করবেন, নাকি দেশভিত্তিক নীতি অনুসরণ করবেন। ধারণা করা হচ্ছে- কেবল কিছু দেশের জন্য শুল্ক বসানো হবে। দেশগুলো বড় অর্থনীতি ও তাদের অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল করার জন্য ট্রাম্প এসব করার কথা ভাবছেন।
পরবর্তী পদ্ধতিটি ট্রাম্পের পরিচিত কৌশলের সঙ্গে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি শুল্ক আরোপের হুমকি ব্যবহার করে চুক্তি করতে প্রস্তুত। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো- যদি শুল্কের প্রভাব স্থায়ীভাবে উচ্চ মূল্যস্ফীতির আশঙ্কা তৈরি করে, তবে তা আর্থিক বাজারে প্রভাব ফেলবে। মার্কিন শেয়ার বাজারের তীব্র পতন ট্রাম্পের পরিকল্পনার অংশ নয়, তা নিশ্চিত করে বলা যায়। তবে এই ধারণা যে সবকিছু ভালোভাবেই শেষ হবে, তা অতিমাত্রায় আশাবাদী বলে মনে হচ্ছে। ট্রাম্পের এই পদক্ষেপ ১৯৩০ সালের স্মুট-হাওলি শুল্ক আইনের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষামূলক বাণিজ্য নীতি, যা তখন মহামন্দার সময় মার্কিন বাণিজ্য অংশীদারদের পাল্টা প্রতিক্রিয়ার কারণ হয়েছিল। গত পাঁচ বছরে বিশ্ব অর্থনীতি একের পর এক ধাক্কা খেয়েছে- মহামারি, ইউক্রেন যুদ্ধ এবং মূল্যস্ফীতির প্রত্যাবর্তন। পরবর্তী সময়ে বড় চ্যালেঞ্জ কী হতে পারে, তা নিয়ে অনেক জল্পনা ছিল। এখন আর অপেক্ষার প্রয়োজন নেই।