ট্রাম্পের ট্যারিফ বোমা ও বাংলাদেশ
আমেরিকান গ্লোবাল প্রতিবেদনে বাংলাদেশের বাণিজ্য বিনিয়োগ পরিবেশের বিষয়ে যেসব অভিযোগ করা হয়েছে, তা একেবারে সমাধান অযোগ্য নয়। এর মধ্যে কৃষি বা রফতানির কিছু ক্ষেত্রে ভর্তুকির বিষয় অলোচনাযোগ্য নয়, তবে অন্য অনেক ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী সরকারের পদক্ষেপ গ্রহণের কথা রিপোর্টে উল্লেখ আছে- মাসুম খলিলী। সূত্র : নয়া দিগন্ত, ০৫ এপ্রিল ২০২৫
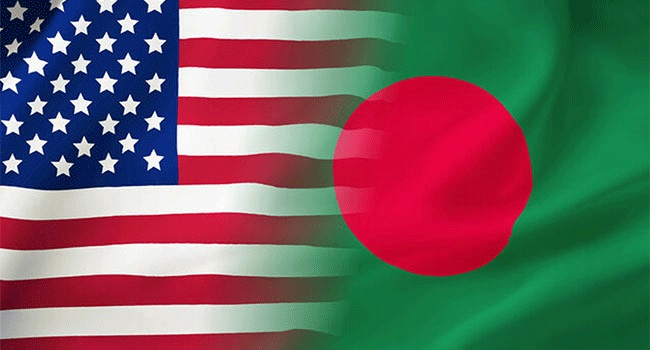
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দেশটির গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক অংশীদারদের ওপর পাল্টা ট্যারিফ আরোপের যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন তা বাংলাদেশসহ অনেক দেশের জন্য বোমাসদৃশ অ্যাটাক হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর থেকে ট্যারিফকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহারের কথা বলে আসছিলেন। কয়েকটি দেশের ওপর তিনি শুল্ক আরোপও করেন। কিন্তু গত বুধবার ট্যারিফ আরোপের ব্যাপারে যে ফর্মুলা তার প্রশাসন ঠিক করেছে; তার প্রভাব খুব নেতিবাচক হতে পারে বাংলাদেশের মতো দেশে। এটি এক দিকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা-ডব্লিউটিও বাণিজ্যের বিশ্বায়নের যে ধারা বেশ কয়েক দশক আগে শুরু করেছিল; সেটিকে উল্টোমুখী করতে পারে। আবার বাংলাদেশের মতো দেশগুলোকে এক ধরনের অর্থনৈতিক নৈরাজ্যের মধ্যেও ফেলে দিতে পারে। তবে এটি ঠিক যে, ট্রাম্পের এ পদক্ষেপ চ‚ড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত নাও হতে পারে। তিনি এর আগে কানাডাকে যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য করা, গ্রিনল্যান্ড দখলে নেয়া, পানামা খাল নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা এবং গাজার মালিকানা নিয়ে সেটাকে রিভারো ধরনের প্রমোদ নগরী বানানোর কথাও বলেছেন। চ‚ড়ান্তভাবে সেটি বাস্তবায়নে তিনি খুব বেশি দূর এগোতে পারছেন বলে মনে হয় না।
তবে বাংলাদেশের মতো দেশের জন্য পাল্টা ট্যারিফ আরোপের মার্কিন পদক্ষেপকে হাল্কাভাবে নেয়ার কোনো অবকাশ নেই। বিশেষত এ পদক্ষেপের আগে আমেরিকার বাণিজ্য দফতর থেকে প্রতিটা দেশের বাণিজ্য পরিস্থিতি বিবেচনা করে একটি গ্লোবাল রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশবিষয়ক প্রতিবেদনে এমন অনেক দিক নিয়ে আসা হয়েছে, যা এড্রেস করার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র অনেক দিন ধরে কথা বলে আসছিল।
প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ইউনূস বিষয়টি গুরুত্বসহকারে দেখছেন বলে মনে হয়েছে। তিনি থাইল্যান্ডে অবস্থানকালে বলেছেন, পরস্পর আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে এ বিষয়টি নিষ্পত্তির চেষ্টা করা হবে। প্রফেসর ইউনূস বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখলে এবং পেশাজীবী বিশেষজ্ঞদের এর সাথে যুক্ত করলে এর একটি সমাধান বের হতে পারে। সেটি না হলে বাংলাদেশে চীনা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের রি-অ্যালোকেশনের মতো যেসব বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছিল তা থেকে কোনো ফল মিলবে বলে মনে হয় না।
কিভাবে শুল্ক নির্ধারণ করা হলো?
শুল্ক নির্ধারণে বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশ যে অঙ্কের ট্যারিফ মার্কিন পণ্যে নির্ধারণ করেছে বলে বলা হচ্ছে বাস্তবে তেমন কিছু নেই। বাণিজ্য ঘাটতিকে মূল ভিত্তি বিবেচনায় এনে দেশের শুল্ক ও অশুল্কগত বাধাকে সামনে এনে শুল্কের একটি কল্পিত হারের কথা ট্রাম্পের সিদ্ধান্তে উল্লেখ করা হয়েছে। এ কল্পিত হারকে যুক্তরাষ্ট্রের অন্য দেশে পণ্য রফতানির আরোপিত শুল্ক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর আশা প্রকাশ করা হয়েছে, বর্ধিত শুল্ক কার্যকর হলে বাণিজ্য ঘাটতি কমে আসবে। অথচ বাণিজ্য ভারসাম্যের ক্ষেত্রে অপরিহার্য শর্তÑ দুই দেশের রফতানি ও আমদানিযোগ্য পণ্য রয়েছে কি না সেটি এবং অর্থনীতির দুই দেশের অর্থনীতির আকারের বাস্তবতার বিষয়টি উপেক্ষা করা হয়েছে।
ট্রাম্প আরোপিত নতুন শুল্ককে রেসিপ্রোক্যাল ট্যারিফ বা পাল্টাপাল্টি শুল্ক হিসাবে চিহ্নিত করছেন। কিন্তু বাস্তবে আমেরিকার পণ্য আমদানিতে বাংলাদেশের ৭৮%, ভিয়েতনামের ৯০%, চীনের ৬৭%, ইউরোপের ৩৯%, জাপানের ৪৬%, পাকিস্তানের ৭০%, ভারতের ৫২% অথবা শ্রীলঙ্কার ৮৮% শুল্ক হার নেই।
মূলত প্রতিটা রাষ্ট্রের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের যে বাণিজ্য ঘাটতি, সেইটাকে আমেরিকার আমদানির সাথে ভাগ করে তাকে ১.২ বা ১.৫ বা বিভিন্ন রকম কোয়ালিফায়ার দিয়ে গুণ করে এ শুল্ক হার নির্ধারণ করা হয়েছে।
শুল্ক নির্ধারণে ঠিক করা অধিকাংশ দেশের জন্য কোএফিশিয়েন্ট ধরা হয়েছে ০.৫। কিন্তু আমেরিকা যাকে শাস্তি দিতে চায়, তার জন্য কোএফিশিয়েন্টের হার বেশি রাখা হয়েছে। যেমন চীনের জন্য কোএফিশিয়েন্ট ০.৮ কিন্তু পাকিস্তানের জন্য ০.৪১। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কিছুটা আনফেভারেবল হারে ডিউটি নির্ধারণ করা হয়েছে ০.৫৪ হারে কোএফিশিয়েন্ট ধরে। ০.৫ কোএফিশিয়েন্ট হিসেবে ধরে ভারত বাংলাদেশের চেয়ে ০.৪ শতাংশ পয়েন্ট বেশি সুবিধা পাচ্ছে এবং পাকিস্তান বাংলাদেশের চেয়ে ১.৩ শতাংশ পয়েন্ট বেশি সুবিধা পাচ্ছে।
বাংলাদেশের জন্য হিসাবটা এভাবে হচ্ছে, আমেরিকার বাংলাদেশ থেকে ২০২৪ সালে রফতানি ছিল ২.৩ বিলিয়ন ডলার এবং আমদানি ছিল ৭.৪ বিলিয়ন ডলার, যার ফলে ট্রেড ডেফিসিট ভাগ আমদানি দাঁড়িয়েছে ৬৯%, কিন্তু বাংলাদেশের ডিউটি নির্ধারিত হয়েছে ৩৭% কারণ ০.৫৪ কোএফিশিয়েন্ট দিয়ে গুণ করা হয়েছে।
এই কোএফিশিয়েন্ট হিসাবটা ঠিক কিভাবে করা হয়েছে সেটা কেউ জানে না। তবে ধরে নেয়া যেতে পারে যে, আমেরিকার ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভ অফিস আমেরিকার ট্রেড ব্যারিয়ার নিয়ে দুই দিন আগে যে গ্লোবাল রিপোর্ট প্রকাশ করেছে, সেখানে বিভিন্ন দেশের ব্যারিয়ারগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। ধরে নেয়া যায় যে, সেই রিপোর্টের মূল ইস্যু এবং আমেরিকার জিও-সিকিউরিটি মাথায় রেখে এই কোএফিশিয়েন্ট নির্ধারণ করা হয়েছে।
গ্লোবাল রিপোর্টে কী আছে
যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা ফোরাম চুক্তি (টিআইসিএফএ) স্বাক্ষর করেছে নভেম্বর ২৫, ২০১৩। এই চুক্তি হলো যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে সমস্যা নিরসনে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের আলোচনার প্রাথমিক প্রক্রিয়া। আমেরিকান বাণিজ্য দফতরের গ্লোবাল রিপোর্ট অনুসারে- বাংলাদেশের গড় মোস্ট-ফেভারড-নেশন (এমএফএন) প্রয়োগকৃত শুল্কের হার ২০২৩ সালে ছিল ১৪.১ শতাংশ। ২০২৩ সালে বাংলাদেশের গড় এমএফএন প্রয়োগকৃত শুল্কের হার ছিল কৃষিপণ্যে ১৭.৭ শতাংশ এবং অকৃষি পণ্যে ১৩.৫ শতাংশ। বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) শুল্ক লাইনের ১৭.৬ শতাংশ মেনে নিতে আবদ্ধ।
বাংলাদেশ সেপ্টেম্বর ২০১৬-এ ডব্লিউটিওর ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন অ্যাগ্রিমেন্ট (টিএফএ) অনুমোদন করেছে। তবে এখনো আমদানি, রফতানি ও ট্রানজিট প্রবিধান সম্পর্কিত স্বচ্ছতা বিজ্ঞপ্তি জমা দেয়নি। বাংলাদেশের স্বনির্ধারিত টিএফএ অনুসারে, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে ডব্লিউটিওর বিজ্ঞপ্তিগুলো জমা দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু বাংলাদেশ তার শুল্ক মূল্যায়ন আইন ডব্লিউটিওকে অবহিত করেনি এবং এখনো ডব্লিউটিও কাস্টমস মূল্যায়ন চুক্তি কিভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে তা বর্ণনা করে সমস্যার চেকলিস্ট সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানায়নি।
যুক্তরাষ্ট্রের গ্লোবাল প্রতিবেদনে বলা হয়, সরকারি ক্রয় প্রাথমিকভাবে ২০০৬ এর পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইনের অধীনে পাবলিক টেন্ডারের মাধ্যমে করা হয়। সেই সাথে সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট দ্বারা পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ প্রকাশ্যে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক বিডিংয়ের নীতি সাবস্ক্রাইব করে; তবে দুর্নীতির অভিযোগ সেখানে খুব সাধারণ বিষয়। বাংলাদেশ একটি জাতীয় ইলেকট্রনিক সরকারি ক্রয় পোর্টাল চালু করেছে, কিন্তু মার্কিন স্টেকহোল্ডারদের আছে পুরনো প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য ব্যবহার সম্পর্কে উদ্বেগ উত্থাপিত হয়েছে। অনুক‚ল বৈশিষ্ট্যের স্পেসিফিকেশন গঠন এবং পাবলিক টেন্ডারে সামগ্রিক স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে বাংলাদেশে। বেশ কিছু মার্কিন কোম্পানি আছে দাবি করেছে যে তাদের বিদেশী প্রতিযোগীরা প্রায়ই তাদের স্থানীয় অংশীদারদের ব্যবহার করে ক্রয়প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।
আমেরিকান প্রতিবেদনে সরকারি দরপত্রে মার্কিন কোম্পানির বিডিংয়ের অসুবিধার কথা উল্লেখ করে বলা হয়, ২০২৪ সালের আগস্টে গঠিত এবং ২০২৫ সালের শেষের দিকে অথবা ২০২৬ সালের প্রথম দিকে সাধারণ নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকা বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার সংস্কার করার প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত করেছে যা উন্মুক্ত দরপত্র এবং স্বচ্ছতা সহজতর করবে।
বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি সুরক্ষা যুক্তরাষ্ট্রের অগ্রাধিকার। এ প্রসঙ্গে প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে পর্যাপ্ত মেধা সম্পত্তি (আইপি) সুরক্ষা এবং প্রয়োগের অভাব রয়েছে এবং এখানে জাল ও পাইরেটেড পণ্য সহজলভ্য। স্টেকহোল্ডাররা নকলের উৎস দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান প্রবণতার কথাও উল্লেখ করেছে। এ বিষয়ে পুলিশের অনুসন্ধানী সংস্থান ও দক্ষতার অভাব রয়েছে।
তবে প্রতিবেদনে এও উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আইনি সংস্কারের মাধ্যমে আইপি সুরক্ষা উন্নত করতে কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। ২০২২ সালের এপ্রিলে একটি নতুন পেটেন্ট আইন পাস করার পর ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে তা আরো সংশোধন করা হয়। এরপর অক্টোবর ২০২৩ সালে কপিরাইট সংশোধনী এবং জুলাই মাসে শিল্প নকশা আইন ২০২৩ প্রণয়ন করা হয়। তবে এ পরিবর্তনগুলোর কার্যকারিতা অনিশ্চিত রয়ে গেছে। এ জন্য বাংলাদেশের আইপি শাসন, প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে আরো ভালো সমন্বয় গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে রয়েছে কাস্টমস, অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়, কপিরাইট অফিস, বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (বিডা) এবং বিভাগ পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক (ডিপিডিটি)।
প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৩ সালে সংশোধিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬, অনুমোদন করার পর বাংলাদেশ সরকার যেকোনো তথ্যপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে যেকোনো কম্পিউটার সিস্টেমে প্রবেশ করতে পারে অথবা কোনো কম্পিউটার সম্পদের মাধ্যমে প্রেরিত তথ্য আটকাতে পারে। এ আইনের আওতায় বাংলাদেশ যেকোনো ডেটা বা ভয়েস কলের সংক্রমণ নিষিদ্ধ করতে পারে। এ ছাড়া অনলাইন যোগাযোগ সেন্সর করতে পারে।
সাইবার নিরাপত্তা প্রসঙ্গে প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৮ এর ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রতিস্থাপন করে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে, বাংলাদেশ সংসদ সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট অফ ২০২৩ পাস করে। ৩ ডিসেম্বর, ২০২৪-এ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সাইবার সিকিউরিটি আইন প্রতিস্থাপনে একটি খসড়া সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ অনুমোদন করেছে। অধ্যাদেশ পরবর্তী সংসদ অনুমোদন দিলে তা আইন হিসেবে কার্যকর হবে।
রফতানি বিনিয়োগ বাধা প্রসঙ্গে প্রতিবেদনে বলা হয় বাংলাদেশ সাধারণত বেশির ভাগ সেক্টরে শতভাগ বিদেশী মালিকানার অনুমতি দেয়, তবে বিদেশী মালিকানা রয়েছে পেট্রোলিয়াম বিপণন, গ্যাস বিতরণসহ নির্দিষ্ট সেক্টরে ইকুইটি ক্যাপ সাপেক্ষে টেলিযোগাযোগ বিদেশী বিনিয়োগকারীদের অবশ্যই প্রাসঙ্গিক থেকে একটি অনাপত্তি প্রশংসাপত্র গ্রহণ করতে হয়।
বৈদেশিক বাণিজ্যে বাধা নিয়ে বলা হয়, বাংলাদেশ থেকে বিনিয়োগ-সম্পর্কিত মূলধন জটিল থেকে যায়, স্বচ্ছতার অভাব দেখা যায় এবং প্রায়ই ফল হয় উল্লেখযোগ্য বিলম্ব। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার মার্কিন কোম্পানিগুলোর সাথে আনুষ্ঠানিক ঋণ পরিশোধের চুক্তিতে প্রবেশ করতে সম্মত হয়েছে, যাতে বকেয়া ও প্রত্যাবাসন অনুমোদনে আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতির উন্নতি হয়।
ভর্তুকি প্রসঙ্গে বলা হয়, বাংলাদেশ কৃষি ভর্তুকির একটি পরিসীমা বজায় রাখে। ভর্তুকি একটি সমর্থন মূল্যে শস্য কেনার সুযোগ দেয়। ভর্তুকিযুক্ত সার, অ-পণ্য-নির্দিষ্ট সহায়তাসহ উৎপাদকদের জন্য উৎপাদন ইনপুট, ডিজেল জ্বালানি, সেচের জন্য বিদ্যুৎ ও কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবস্থার মাধ্যমে দাম কমাতে সাহায্য করে। ৪৩টি সেক্টরে রফতানিকারকরা রফতানি মূল্যের ১ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ পর্যন্ত নগদ প্রণোদনা পায়।
প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৩ সালে, যুক্তরাষ্ট্র জেনারেলাইজড সিস্টেমের অধীনে বাংলাদেশের সব শুল্ক সুবিধা স্থগিত করে। শ্রমিকের অধিকার, আগুন এবং বিল্ডিং নিরাপত্তা ও সমাবেশের স্বাধীনতাসহ বিধিবদ্ধ শর্ত পূরণে ব্যর্থতায় পছন্দ জিএসপি সুবিধা স্থগিত রয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ এর বিবেচনা অনুযায়ী, বাংলাদেশ জিএসপির অধীনে শুল্কমুক্ত সুবিধার জন্য অযোগ্য রয়ে গেছে।
২০২৪ সালে, যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশের জন্য একটি ১১ দফা শ্রম কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করেছে। এটি অনুসারে বাংলাদেশ সরকার জিএসপির শর্ত পূরণে যে পদক্ষেপ নিচ্ছে তা দেখাতে বিশদ কাজ করতে হবে। যার মধ্যে রয়েছে, শ্রম কর্ম পরিকল্পনা ফোকাস করে শ্রমিকদের স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও যোগদানের ক্ষমতা উন্নত করা, জবাবদিহি বাড়ানো, কর্মীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধ করা এবং উন্নত শ্রম পরিদর্শনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিধি প্রয়োগ করা।
আমেরিকান প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে দুর্নীতি একটি ব্যাপক এবং দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা এবং দুর্নীতি দমন আইন অপর্যাপ্তভাবে বলবৎ রয়েছে। ফৌজদারি কার্যবিধি, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, দণ্ডবিধি এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় ঘুষের চেষ্টার অভিযোগ রয়েছে। দুদক ক্রমবর্ধমানভাবে সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মামলা চালালেও তা প্রধানত নিম্নস্তরের কর্মকর্তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিছু উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তার ক্ষেত্রে মামলার একটি বড় ব্যাকলগ রয়ে গেছে।
আমেরিকান গ্লোবাল প্রতিবেদনে বাংলাদেশের বাণিজ্য বিনিয়োগ পরিবেশের বিষয়ে যেসব অভিযোগ করা হয়েছে, তা একেবারে সমাধান অযোগ্য নয়। এর মধ্যে কৃষি বা রফতানির কিছু ক্ষেত্রে ভর্তুকির বিষয় অলোচনাযোগ্য নয়, তবে অন্য অনেক ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী সরকারের পদক্ষেপ গ্রহণের কথা রিপোর্টে উল্লেখ আছে। এ সরকার যেহেতু অনেক ক্ষেত্রে মৌলিক সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নে অগ্রসর হচ্ছে সেহেতু অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পদক্ষেপ শুল্কারোপ নিয়ে সৃষ্ট সমস্যা সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসা যেতে পারে।