ভূমিকম্প : বাংলাদেশের ভাবনার এখনই সময়
ড. মিহির কুমার রায় । সূত্র : ভোরের কাগজ
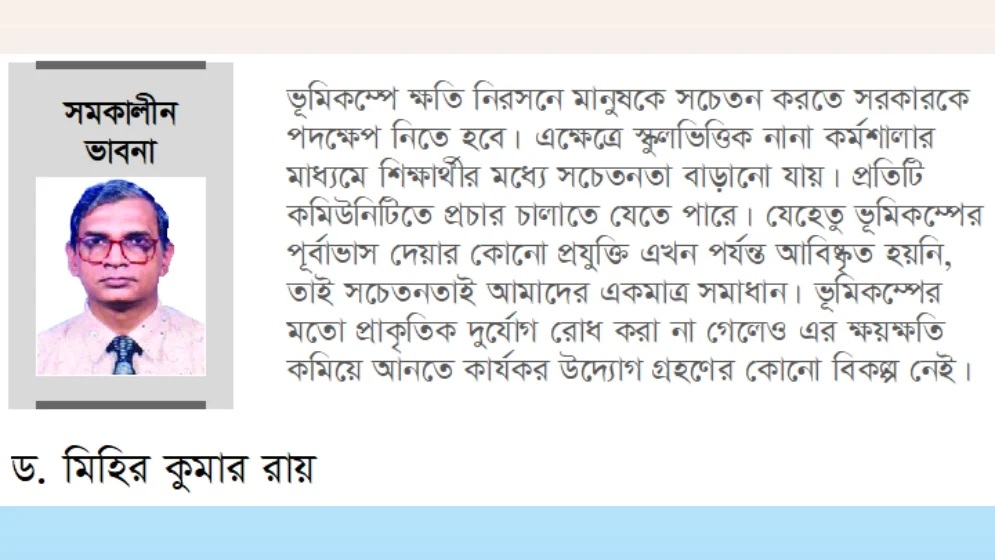
ভূমিকা : ভূমিকম্প সাধারণ অর্থে ভূমির কম্পনকে বোঝায়, যা ভূ-তত্ত্ব বা জিওলজি বিষয়ের অন্তর্গত, বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পাঠপঠনে ও গবেষণায়। এই বিষয়টির একটি টেকনিক্যাল রূপ রয়েছে, যা সাধারণের কাছে একটি আতঙ্কের বিষয় হিসেবেই বেশি পরিচিত, যা আমাদের সমাজ জীবনকে অনেক ভাবনার মধ্যে আরো একটি ভাবনায় সংযোজিত করে থাকে, যা কাম্য নয়। বৈজ্ঞানিক ভিত্তি অনুযায়ী, ভূমিকম্প হয় প্লেট টেকটোনিকের সংঘর্ষের ফলে।
পাশাপাশি দুটি মহাদেশীয় প্লেটের সীমান্ত অঞ্চলে যে প্রবল পীড়নের সৃষ্টি হয়, সেই পীড়ন যখন বড়সড় চ্যুতির সৃষ্টি করে এবং তার অন্তর্নিহিত শক্তি বের করে দেয়, তখন ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। ভূপৃষ্ঠে বা ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি গভীরতায় বড় মাত্রার বিস্ফোরণ ঘটলে মৃদু থেকে মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্পের উৎপত্তি হতে পারে। ১০০ বছরের ভূমিকম্পের ইতিহাসে ছোট-বড় অনেক ভূমিকম্প বাংলাদেশে আঘাত হেনেছে, যা ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক সংকেত হিসেবে কাজ করা উচিত।
ভৌগোলিক বিবেচনা : ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ ভূমিকম্পের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। বিশেষ করে সিলেট, চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল ভূমিকম্পের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এসব অঞ্চলের মাটির গঠন এবং পাহাড়ি এলাকার ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ভূমিকম্পের সময় ভূমিধসের ঝুঁকি তৈরি করে। ঢাকা শহরও এই ঝুঁকির বাইরে নয়। কারণ এটি একটি সিল্টি বেসিনের ওপর অবস্থিত।
ভূমিকম্প হলে এই এলাকার মাটি সহজেই কম্পনের তীব্রতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। গত ১০০ বছরে বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকম্প হয়েছে। এগুলোর মধ্যে কয়েকটি ছোট পরিসরে হলেও বড় ভূমিকম্পের আশঙ্কা বাড়িয়ে তুলেছে। সম্প্রতি বেশকিছু হালকা ও মাঝারি ধরনের ভূকম্পন এ ঝুঁকির মাত্রা বাড়িয়ে তুলেছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশে বড় মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানতে পারে। গত ৭ জানুয়ারি সকাল ৭টা ৫ মিনিটে ৭ দশমিক ১ মাত্রার ভূমিকম্পে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। কম্পনের উৎপত্তিস্থল ঢাকা থেকে ৬১৮ কিলোমিটার দূরে চীনের জিজাং।
এর আগে গত ৩ জানুয়ারি ৫ মাত্রার ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল ঢাকা থেকে ৪৮২ কিলোমিটার দূরে মিয়ানমারের হোমালিনে। এক সপ্তাহে দেশে দুবার ভূমিকম্প অনুভূত হলেও উৎপত্তিস্থল দূরে হওয়ায় বাংলাদেশে খুব বেশি প্রভাব পড়েনি। তবে এ পটভূমিতে মানুষের মনে ভূমিকম্পের প্রস্তুতি ও পূর্বাভাস ঘিরে নতুন করে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা ছোট ছোট এই ভূমিকম্পে বড় বিপর্যয়ের আভাস দেখতে পাচ্ছেন। ২০২৩ সালের ২ ডিসেম্বর সকালে সারাদেশে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ল²ীপুর জেলার রামগঞ্জ থেকে আট কিলোমিটার পূর্ব-উত্তর-পূর্বে যার মাত্রা ছিল রিখটার স্কেলে ৫ দশমিক ৬, যা বিগত ২৫ বছরের মধ্যে ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী।
এই ভূমিকম্পে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আবাসিক হল ও কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে একটি পোশাক কারখানায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। গত বছরের ২৫ এপ্রিল নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে ৩ দশমিক ৯ মাত্রার ভূমিকম্প হয়। ৫ মে ঢাকা থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে দোহারে উৎপত্তি হওয়া ৪ দশমিক ৩ মাত্রার ভূমিকম্পটি বেশ আতঙ্ক তৈরি করে মানুষের মধ্যে। একই মাসের ১৭ তারিখে ৩ দশমিক ৩ মাত্রার আরেকটি ভূকম্পন অনুভূত হয়, যার উৎপত্তিস্থল ছিল ঢাকা থেকে ১২৫ কিলোমিটার দূরে নেত্রকোনায়। এ ছাড়া গত ২০২১ সালের ২৯ ও ৩০ মে সিলেট শহর এলাকায় ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে ৪ দশমিক ১ রিখটার স্কেলে ভূমিকম্প অনুভূত হয়ে ছিল। পরবর্তী সময়ে ৭ জুন সিলেট শহরে মৃদু মাত্রার ভূমিকম্প হয়।
এর কিছু সময় পরেই ৭ জুলাই সিলেট, ঢাকা ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে, ৮ আগস্ট চট্টগ্রাম ও আশপাশে, ১০ আগস্ট মিয়ানমারে ৫ দশমিক ৬ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এর আগে ১৯৯৮ সালের মে-তে সিলেটের বড়লেখায় ৫ দশমিক ৮ মাত্রার একটি ভূকম্পন সৃষ্টি হয়েছিল। রাজধানীর বাইরে রায়পুরা, ভোলা, খুলনা, কোটালীপাড়া, চট্টগ্রাম, দেবিদ্বার, ঝালকাঠি, বরগুনা, রাজশাহী, সিলেট, রংপুর, চুয়াডাঙ্গা, নোয়াখালী, কুষ্টিয়ায় তীব্র ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। এর কারণ হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে জলাধার নির্মাণ, পারমাণবিক পরীক্ষা, খনিজ উত্তোলন ইত্যাদি। কোনো স্থানে অতিরিক্ত খনিজ (গ্যাস, তেল ইত্যাদি) উত্তোলনের কারণে শিলার স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হয়ে ধ্বংসের সৃষ্টি হয়ে ভূমিকম্প দেখা দিতে পারে, যা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অহরহ ঘটে চলছে বলে প্রতীয়মান।
ইতিহাসে ভূমিকম্প : ১৮৯৭ সালের শিলং ভূমিকম্প (ম্যাগনিটিউড ৮.৭) : এটি ভারতের শিলং অঞ্চলে উৎপত্তি হয়, কিন্তু বাংলাদেশে এর ব্যাপক প্রভাব পড়ে। বিশেষত সিলেট অঞ্চলে এই ভূমিকম্পের ফলে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়। এটি বাংলাদেশের ভূমিকম্প প্রবণতার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯১৮ সালের আসাম ভূমিকম্প (ম্যাগনিটিউড ৭.৬) : উত্তর-পূর্ব ভারতে উৎপন্ন এই ভূমিকম্প সিলেটসহ বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়। ১৯৫০ সালের আসাম-তিব্বত ভূমিকম্প (ম্যাগনিটিউড ৮.৬) : সিলেট এবং চট্টগ্রামে এই ভূমিকম্প ব্যাপক তীব্রতা নিয়ে আঘাত হানে। যদিও বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।
কিন্তু এটি বড় ধরনের বিপর্যয়ের সতর্ক সংকেত দেয়। ১৯৮৮ সালের চট্টগ্রাম ভূমিকম্প (ম্যাগনিটিউড ৭.৫) : পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে এই ভূমিকম্প বড় ধরনের ক্ষতি করে। অনেক ভবন ধসে পড়ে এবং বহু মানুষ হতাহত হয়। ২০০৪ সালের সুমাত্রা-আন্দামান ভূমিকম্প (ম্যাগনিটিউড ৯.১) : এটি বাংলাদেশে সরাসরি আঘাত না করলেও উপকূলীয় এলাকাগুলোতে সুনামির ঝুঁকি তৈরি করে। ২০১৬ সালের মিয়ানমার ভূমিকম্প (ম্যাগনিটিউড ৬.৮) : এই ভূমিকম্প ঢাকাসহ সারাদেশে অনুভূত হয়। এটি মানুষের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক সৃষ্টি করে এবং ভবনের ক্ষয়ক্ষতি হয়।
বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে ঘন ঘন ভূমিকম্পের ঘটনা টেকটোনিক প্লেটগুলোর চলাচল এবং তাদের মধ্যে শক্তি সঞ্চয়ের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত। প্লেটগুলোর মধ্যকার চাপ বাড়লে ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটার আশঙ্কা থাকে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে বড় ভূমিকম্প হয়নি। এটি ‘সিসমিক গ্যাপ’ তৈরি করেছে, যা বিপুল শক্তি জমা করছে। ভবিষ্যতে এটি বড় ধরনের ভূমিকম্পের আকারে প্রকাশ পেতে পারে।
ভূমিকম্পবিষয়ক গবেষণা : বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক মেহেদী আহমেদ আনসারী বলেন, ১৮৬৯ সালে সিলেটের কাছার এলাকায় ৭ দশমিক ৬ মাত্রার ভূমিকম্প হয়। ১৯১৮ সালে শ্রীমঙ্গলে ও ১৯২৩ সালে দুর্গাপুরেও বড় ধরনের ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ফলে সেখানে বড় ধরনের ফাটলের সৃষ্টি হয়, যা সুপ্ত অবস্থায় আছে। ছোট ছোট ভূমিকম্প সেটিকে নাড়াচাড়া দিতে পারে। সম্প্রতি বড় মাত্রার ভূমিকম্প হয়নি; তার মানে এই নয় যে আর বড় ভূমিকম্প হবে না। তাই এখনই প্রস্তুতি নিতে হবে।
৭ মাত্রার কাছাকাছি ভূমিকম্প ১০০ থেকে ১৫০ বছর পরপর হতে পারে। সে হিসাবে ৭ মাত্রার ভূমিকম্প বাংলাদেশে যে কোনো সময় হওয়ার শঙ্কা আছে। ঢাকা শহরের ২৫ শতাংশ ভবন ভূমিকম্প সহনশীল করে তৈরি হয়নি। গত জুনে ‘আরবান রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট : রাজউক অংশ’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত গবেষণায় বলা হয়েছে, ১৮৮৫ সালে ৭ দশমিক ৫ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছিল টাঙ্গাইলের মধুপুরের ভূগর্ভের চ্যুতি বা ফাটল রেখায় (ফল্ট)। এরপর ১৩৯ বছর পার হলেও এত বড় ভূমিকম্প ওই ফাটল রেখায় আর হয়নি। মধুপুরের ওই ফাটল রেখায় যদি রিখটার স্কেলে ৬ দশমিক ৯ মাত্রার ভূমিকম্পও হয়, তাহলে ঢাকায় কমপক্ষে ৮ লাখ ৬৪ হাজার ভবন ধসে পড়বে, যা ঢাকার মোট ভবনের ৪০ শতাংশ।
ওই মাত্রার ভূমিকম্প দিনে হলে কমপক্ষে ২ লাখ ১০ হাজার মানুষের মৃত্যু হবে। আর রাতে হলে কমপক্ষে ৩ লাখ ২০ হাজার মানুষ মারা যাবে। ইন্ডিয়ান, ইউরেশিয়ান এবং মিয়ানমার এই তিনটি টেকটোনিক প্লেটের সংযোগস্থলে বাংলাদেশের অবস্থান। গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের ভূ-ত্বক যে তিনটি প্লেটের ওপর অবস্থিত তার মধ্যে ভারতের প্লেট, মিয়ানমার প্লেটের নিচে আটকে আছে প্রায় ৪০০ বছর ধরে এবং এদের মধ্যে সঞ্চিত হচ্ছে প্রবল শক্তি, যা ৮-৯ মাত্রার ভূমিকম্প সৃষ্টি করতে পারে।
বাংলাদেশ সরকারের নীতিমালা ও কার্যক্রম : গৃহায়ণ ও গণপূর্ত উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান বলেন, ভূমিকম্পের ঝুঁকি মোকাবিলায় সমন্বিত জাতীয় নীতি নেই। যদিও একটি ঝুঁকিমুক্ত ও নিরাপদ শহর নির্মাণে এ ধরনের একটি সমন্বিত জাতীয় নীতি প্রণয়ন আবশ্যক। ভূমিকম্প সহনীয় স্থাপনা নির্মাণ এবং ভূমিকম্প সহনশীল নগরায়ণে সরকার কাজ করছে। ভূমিকম্পের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ইতোমধ্যে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভূমিকম্পসহ সব দুর্যোগের সময় সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের করণীয় নির্ধারণ ও দুর্যোগবিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। এর অধীন দুর্যোগকালীন কার কী করণীয় তা নিরূপণ করা হয়েছে।
উক্ত নীতিমালার অধীন উপদেষ্টার সভাপতিত্বে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে। উক্ত স্থায়ী আদেশাবলির অধীন মাঠ পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড পর্যন্ত অংশীজনের করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সে মোতাবেক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অধিকন্তু ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের সমন্বয়ে জরুরি প্রতিক্রিয়া সংস্থাগুলোর জন্য জাতীয় কন্টিনজেন্সি প্ল্যান প্রস্তুত করা হয়েছে। তা ছাড়া বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড অনুমোদন লাভ করেছে। ইতোমধ্যে ভূমিকম্পপরবর্তী অনুসন্ধান ও উদ্ধারন্ত সরঞ্জাম ক্রয়পূর্বক সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর কাছে হন্তান্তর করা হয়েছে।
বড় ভূমিকম্প হলে বাংলাদেশের প্রস্তুতি কতটুকু?
বড় ভূমিকম্প মোকাবিলায় বাংলাদেশের প্রস্তুতি অত্যন্ত দুর্বল। এর পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ হলো- অবকাঠামোগত দুর্বলতা, জনসংখ্যার ঘনত্ব, জরুরি সেবার দুর্বলতা, সচেতনতার অভাব ইত্যাদি। এর জন্য দরকার বিল্ডিং কোডের কঠোর প্রয়োগ, সিসমিক ম্যাপিং, উদ্ধার কর্মীদের প্রশিক্ষণ, জরুরি পরিকল্পনা ইত্যাদি। বাংলাদেশে বড় ভূমিকম্প হলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে রাজধানী ঢাকা। ঢাকার অধিকাংশ ভবন রাজউক ও সিটি করপোরেশনের নিয়মানুযায়ী নির্মিত নয়।
এর ফলে এসব ভবন বড় ভূমিকম্পের সম্মুখীন হলে সহজেই ধসে পড়বে। মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্পও অনেক ভবন সহ্য করতে পারবে না। যার ফলে ব্যাপক বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া ঢাকায় অনেক পুরনো ভবন রয়েছে, যেগুলোর নির্মাণকাল অনেক আগের। এ ধরনের ভবনগুলো ভূমিকম্প সহনে অত্যন্ত অযোগ্য হয়ে পড়েছে এবং কোনো শক্তিশালী কম্পনে ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা বেশি। আমাদের দেশের ভূমিকম্প বিষয়ে জনসচেতনতার অভাবও ব্যাপক।
শেষ কথা : ভূমিকম্পে ক্ষতি নিরসনে মানুষকে সচেতন করতে সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হবে। এক্ষেত্রে স্কুলভিত্তিক নানা কর্মশালার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো যায়। প্রতিটি কমিউনিটিতে প্রচার চালাতে যেতে পারে। যেহেতু ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেয়ার কোনো প্রযুক্তি এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি, তাই সচেতনতাই আমাদের একমাত্র সমাধান। ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ রোধ করা না গেলেও এর ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের কোনো বিকল্প নেই। ভূমিকম্প ও তৎসংশ্লিষ্ট ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় বাংলাদেশ তার সক্ষমতা প্রমাণ করবে- সেটাই আশা।
ড. মিহির কুমার রায় : কৃষি অর্থনীতিবিদ ও গবেষক।