ভ্যাটের আইওয়াশ ও সরকারের আস্থা
ড. মো. আইনুল ইসলাম । সূত্র : জনকণ্ঠ, ১৮ জানুয়ারি ২০২৫
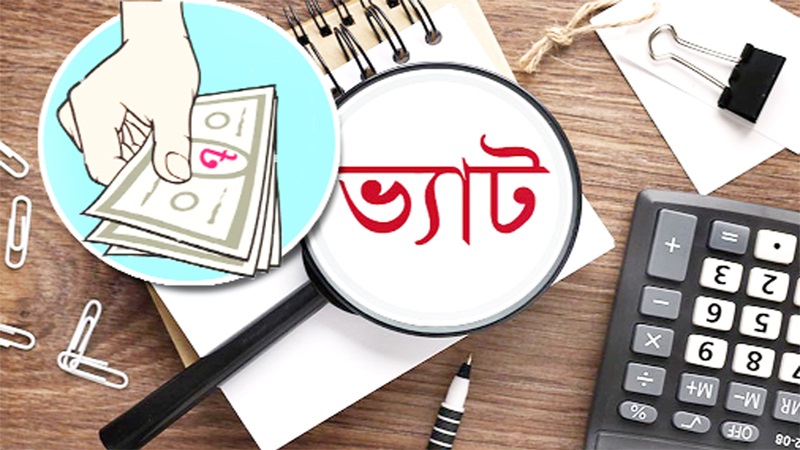
উচ্চ মূল্যস্ফীতির পরিবেশে প্রবল সমালোচনার মুখে সরকার কেবল রেস্তোরাঁর খাবারের বিলের ওপর ভ্যাট আগের অবস্থায় রেখে তৈরি পোশাক, নিজস্ব ব্র্যান্ডের পোশাক বিপণন, মোটরগাড়ির গ্যারেজ-ওয়ার্কশপ, নন-এসি হোটেল খাতে ভ্যাট কিছুটা কমিয়ে পুনর্বিন্যাস করেছে। অর্থাৎ পূর্বঘোষিত ভ্যাট বৃদ্ধির সিদ্ধান্তে খুব একটা হেরফের হয়নি। পুরনো হারের বেশি ভ্যাটই দিতে হবে ভোক্তাদের।
সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ওষুধ ও মোবাইল ফোনে কথা বলায় বর্ধিত ভ্যাট নিয়েও চিন্তাভাবনা হচ্ছে। গণমাধ্যমের খবর পরিবেশনের ধরনে মনে হচ্ছে, সমালোচনার তোড় সামাল দিতেই অর্থ মন্ত্রণালয়ের আমলারা এনবিআরের খোলসে প্রয়োগ করেছে ‘আইওয়াশ দাওয়াই’। উপরন্তু ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার বদনামের ঝুঁকি থাকায় হজযাত্রীদের বিমান টিকিটের ওপর আবগারি শুল্কও প্রত্যাহার করা হয়েছে। সরকার আসলে এসব করে নিজেকে ‘বলহীন’ই প্রতীয়মান করছে, যা সাধারণ মানুষের ভালো লাগার কথা নয়। কারণ, তারা এটুকু অন্তত বোঝে যে, মানবসমাজে থাকতে হলে ব্যক্তিমানুষকে খরচাপাতি করতেই হবে। সামাজিক সুবিধা পেতে কর-ট্যাক্স দিতেই হবে। সমাজ পরিচালকেরা তো আর নিজেরা অর্থকড়ি তৈরি করেন না, তারা জনমানুষের অর্থ দিয়েই সামগ্রিক ব্যবস্থা সমন্বয় করেন।
বিগত দেড় দশকে রাজনীতিবিদ-আমলা-ব্যবসায়ীদের ত্রি-চক্র ত্রিবেণীতে বসে আইএমএফ-বিশ^ব্যাংকের ঋণ নিয়ে সরকারের নামে কর-ট্যাক্সসহ নানা খাতে অপকর্ম করেছে। জনগণ তেড়িবেড়ি করলে বেদম মার দিয়েছে। বলা যায় ‘ভরপেট না-ও খাই, রাজকর দেওয়া চাই’ শাসন চালিয়েছে। ফলে আমলা সন্তান ১৫ লাখ টাকায় ছাগল কিনেছে, ত্রি-চক্র অভিজাত দেশে যেন পাড়া প্রতিষ্ঠা করেছে। একসময় মানুষের সহ্যের বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ায় দলবলসহ পালাতে হয়েছে। অপরদিকে, বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের দুয়েকজন ছাড়া অধিকাংশ উপদেষ্টাই সরকার পরিচালনের অভিজ্ঞতা নেই।
সমাজে তাঁরা নির্মোহ হিসেবে পরিচিত। এই সুযোগে কারা অল্পসময়েই তাঁদের বারবার হঠকারী বুদ্ধি দিয়ে সামনে ঠেলে দিচ্ছে; ‘যদি সেই নথ খসালি, তবে কেন লোক হাসালি’ পরিস্থিতিতে ফেলছেÑ এটি উপদেষ্টাদের মাথায় নিতে হবে। উপদেষ্টাদের প্রতি এখনো জনগণের আস্থা আছে। কিন্তু যার নিজের ওপর আস্থা নেই, তাকে জনগণ কতদিন আর আস্থায় রাখবে!
শান্তিতে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার সংকটময় এক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে সর্বোচ্চ প্রত্যাশা ও সমর্থন নিয়ে শাসন ক্ষমতায় বসা এই সরকার এ পর্যন্ত লক্ষ্যযোগ্য কোনো পরিবর্তন আনতে না পারলেও, দেশকে খাদের কিনারা থেকে খুব বেশি ওপরে তুলতে না পারলেও ছোটখাটো বেশকিছু সাফল্য দেখিয়েছে। এমন এক প্রেক্ষাপটে অর্থবছরের মাঝপথে এসে তীব্র মূল্যস্ফীতির মধ্যেই শতাধিক পণ্য ও সেবায় ভ্যাট বৃদ্ধির মতো অনায্য একটি সিদ্ধান্ত কেন নিতে হয়েছে, সেটাই অনেকের মাথায় আসছে না। আইএমএফসহ দাতাসংস্থা পরিচয় দেওয়া উন্নয়ন সহযোগীদের শর্ত অনুযায়ী সরকারের কর-জিডিপি অনুপাত বাড়ানোর প্রয়োজন, যা বিগত কোনো রাজনৈতিক সরকারই করেনি। তাই নিরূপায় হয়ে অন্তর্বর্তী সরকার সহজ পথ হিসেবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভ্যাট বাড়ানোর।
কিন্তু এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সরকারের স্মরণ করা উচিত ছিল যে, আয়বৈষম্য, ধন-সম্পদ বৈষম্য, স্বাস্থ্য বৈষম্য, শিক্ষা বৈষম্যসহ সবধরনের বৈষম্য প্রকটতর হতে হতে অতিমাত্রায় বিপজ্জনক অবস্থায় পৌঁছে গেছে। দেশে উচ্চ মূল্যস্ফীতিও চলছে। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতেই বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে বিশ^খ্যাত এক গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে, যার মূল উপজীব্যই ছিল বৈষম্য নিরসন। শত শত শিশু-কিশোর-তরুণের বৈষম্যবিরোধী এক আন্দোলনে নিহত হওয়ার ওই ঘটনার প্রভাবে প্রবল প্রতাপশালী একটি রাজনৈতিক দল প্রায় ঝারেবংশে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।
বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ০.৭৪ শতাংশ প্রতিনিধিত্বকারী সরকারি চাকরিতে কোটা প্রথাকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া ছোট্ট একটি আন্দোলন স্ফূলিঙ্গের মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে দ্রুতই গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেওয়ায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নির্মম-নির্দয় আচরণ বড় ভূমিকা রাখলেও জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অর্থাৎ অতি সাধারণ মানুষজন যে পিলপিল করে রাস্তায় নেমে এসে অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে, তাতে শত শত মানুষের মৃত্যু ও সরকারি চাকরিতে কোটা পদ্ধতির ভূমিকা ছিল খুব নগণ্য। প্রকৃত অর্থে সবচেয়ে বড় বড় ভূমিকা রেখেছে মানুষের মনে চাপা ক্ষোভ হয়ে বিরাজ করা বহুমাত্রিক ও সর্বব্যাপী বৈষম্যের চিত্র।
কিন্তু খুবই আশ্চর্যের বিষয়, বৈষম্যবিরোধী মর্যাদা নিয়ে সরকার ক্ষমতায় বসা পরিচালকেরা ঔপনিবেশিক মানসিকতার আমলাদের মন্ত্রণায় পড়ে দেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামোগত দুর্বলতা কাটানোর পথে না গিয়ে বৈষম্য-অসমতা বৃদ্ধিকারী ভ্যাটকেই অর্থনীতি কর-জিডিপি-প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছেন। এ কারণেই অনেকেই আশঙ্কা করছে, ২০২৬-২৭ অর্থবছরে সবধরনের পণ্য ও সেবার ওপর বিশেষত দৈনন্দিন ব্যবহার্য ৬৫টি পণ্যের ওপর একক ভ্যাট হার ১০-১২-১৫ শতাংশ করার ড্রেস রিহার্সাল হিসেবে অন্তর্বর্তী সরকার শতাধিক পণ্য ও সেবায় আগেভাগেই ভ্যাট বৃদ্ধি করেছে।
এ কথা অনস্বীকার্য, ভীষণ সংকটে থাকা অর্থনীতিকে ভালো করতে সরকারের তহবিলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। কারণ, বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ টাকা বিদেশে পাচার হওয়ায় বাংলাদেশের টাকশাল খুবই দৈন্য দশায় পৌঁছে গেছে। এ কথাও অনস্বীকার্য যে, আইএমএফের চতুর্থ কিস্তির অর্থের দ্রুত ছাড় ও বাড়তি ঋণ পাওয়ার শর্ত হিসেবে শুল্ক-কর বাড়ানোর মতো অজনপ্রিয় সিদ্ধান্ত সরকারকে নিতে হয়েছে। আইএমএফের অর্থ পেলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়বে, বিনিময় হারের চাপও কমবে। এসব বিবেচনায় সরকার বেজার মন নিয়েই এই পথ নিয়েছে। কিন্তু সরকারের বিজ্ঞ পরিচালকেরা কি বোঝেন না যে, কর ব্যবস্থায় যত রকম কর আছে, তার মধ্যে ভ্যাট বা মূল্য সংযোজন করই সবচেয়ে অন্যায্য ও অন্যায় কর।
পরোক্ষ এই কর এমন সব পণ্য ও সেবার ওপর আরোপিত হয়, যা ধনী-গরিব উভয়কে এক পাল্লায় ফেলে একই হারে গলা কাটে। সিগারেট, মদের বিল, বাদাম, আম, কমলালেবু, আঙুর, আপেল, নাশপাতি, মিষ্টি, ফলের রস, ড্রিংক, যেকোনো ধরনের তাজা ফল, বিস্কুট, পটেটো স্ন্যাকস, চশমার প্লাস্টিক ও মেটাল ফ্রেম, রিডিং গ্লাস, সানগ্লাস, বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার ও এতে ব্যবহৃত তেল, বিদ্যুতের খুঁটি, সিআর কয়েল, জিআই তার ইত্যাদি অর্থশালীদের পণ্য হলেও ওষুধ, ডিটারজেন্ট, এলপি গ্যাস, টয়লেট টিস্যুসহ সব ধরনের খাবারের রেস্তোরাঁ ও ইন্টারনেট সুবিধার বাইরে থাকা নিম্ন আয়ের মানুষের মোবাইলে ন্যূনতম কথা বলার ওপর বর্ধিত ভ্যাটের প্রভাব স্বল্প আয়ের মানুষকে উচ্চ মূল্যস্ফীতির মধ্যে আরও বেশি নাজেহাল করবে।
এর চেয়েও বড় কথা হচ্ছে, সরকারের রাজস্ব সংগ্রহে ভ্যাট গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলেও সবসময় এটি সাধারণ মানুষের জীবনকেই সর্বাধিক প্রভাবিত করে এবং বৃদ্ধি করে বৈষম্য-অসমতা। এ ছাড়া বাংলাদেশের বাজার ব্যবস্থায় প্রচণ্ড দুর্বলতায় একটি-দুটি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রভাবে আনুষঙ্গিক ও সম্পর্কিত অনেক পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। ব্যবসায়ীরা পণ্যের বিক্রয়মূল্যে ভ্যাট যোগ করার পাশাপাশি তার সঙ্গে নতুন করে দোকান ভাড়া, কর্মচারী খরচসহ আরও অনেক হিসাব যোগ করে, যা সাধারণ ভোক্তাদেরই বহন করতে হয়। প্যাকেটের গায়ে খুচরা পয়সার হিসাবও ব্যবসায়ীরা ক্রেতাদের ওপরই আরোপ করে।
এ কারণে যেকোনো নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বাড়লে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যায় কয়েক গুণ। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের আয় অনেক দিন ধরেই স্থির আছে। টাকার মান বিবেচনায় নিলে বলা যায় আয় বৃদ্ধির চেয়ে আরও অনেক কমে গেছে, বিনিয়োগে স্থবিরতার কারণে কর্মসংস্থান খাতও বিপর্যস্ত অবস্থায় রয়েছে। বিশাল একটি জনগোষ্ঠী ধার-কর্জ-বাকিতে জীবন চালাচ্ছে। এখন ধনীদের পণ্যের ওপর আরোপিত পণ্যের উচ্চমূল্যের প্রভাবে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান আরও নিচে নেমে যাবে। কারণ, অর্থনীতিতে একের ব্যয় মানে অপরের আয়।
এমনিতেই সাধারণ মানুষকে ২০২০ সালের করোনা ভাইরাসের পর থেকেই আয়ের বড় একটি অংশই উচ্চমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনতেই ব্যয় করতে হচ্ছে। কয়েক কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে গেছে, কয়েক মাস ধরেই মূল্যস্ফীতি দুই অঙ্কের ঘরে বিরাজ করছে। অন্তর্বর্তী সরকার বেশকিছু পদক্ষেপ নিলেও মূল্যস্ফীতি কমার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এই অবস্থায় সাধারণ মানুষ বছরের শুরুতে সরকারের কর-শুল্ক বৃদ্ধির এমন সিদ্ধান্তকে অত্যন্ত নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখছে। তারা মনে করছে, এমনিতেই যেখানে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট হিসেবে তাদের আয়ে যেটুক বাড়তি টাকা যোগ হয়েছে, বাড়ির মালিকরা তার প্রায় পুরোটাই ভাড়া হিসেবে দিয়ে দিতে আগেইভাগেই নোটিস দিয়ে রেখেছে; সেখানে বাড়তি কর-শুল্ক আরোপ সত্যিই বেদনার কথা।
তাদের মতে ব্যবসায়ীরা ভ্যাট দেওয়া এড়ানোর জন্য পণ্যের মান কমিয়ে সস্তা বিকল্প সরবরাহ করে, না হয় বাতাস বেশি ঢুকিয়ে বড় প্যাকেটে কম পণ্য বিক্রি করে। ফলে ভোক্তারা তাদের টাকার পূর্ণ মূল্য পায় না। একইসঙ্গে বাংলাদেশের কর প্রশাসনে চাকরিরতরা কর আদায়ে ছলচাতুরির পাশাপাশি চূড়ান্ত রকম দুর্নীতিবাজ, তা প্রতিবছর কর আদায়ে ব্যর্থতা এবং ১৫ লাখ টাকায় ছাগল কেনার মাধ্যমে অনেক আগেই প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ ভ্যাট সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় এসব ঘাটতি ও অসততার প্রভাব তাদের ওপর গিয়ে পড়ে। আবার অনেক ব্যবসায়ী ভুলভাল ভ্যাট ও অতিরিক্ত চার্জ আদায় করে, যা ভোক্তাদের জন্য বোঝার ওপর শাকের আঁটি। সাধারণ মানুষের এমন মনোভাবের মধ্যেই মনে রাখা দরকার, ভ্যাট শুধু সরাসরি কেনাকাটার ওপর নয় পরোক্ষভাবে পরিবহন খরচ, কাঁচামাল ও উৎপাদন খরচও বাড়িয়ে দেয়। এসব প্রভাব একত্রে পণ্যের চূড়ান্ত মূল্যে প্রতিফলিত হয়।
ফলে পুরো অর্থনীতি সমস্যার মধ্যে পড়ে যায়, যার সবচেয়ে বড় শিকার হয় সাধারণ মানুষ। এই অবস্থায় সরকারের শাসনক্ষমতা ও দেশ পরিচালনার অর্থায়নের উৎস নির্ধারণে দরিদ্র, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও মধ্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণির ওপর কোনো ধরনের উপড়ে কর আরোপ না করা যেখানে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছ থেকে সাধারণ মানুষের সবচেয়ে বড় প্রত্যাশা, সেখানে অর্থবছরেরর মাঝপথে এসে ভ্যাটের মতো পরোক্ষ কর বৃদ্ধি এবং নতুন বাজেটে একক ভ্যাট প্রচলনের আশঙ্কা সৃষ্টি করা সত্যিই সরকারের ব্যর্থতা। সরকার সাময়িক সময়ের জন্য এই সিদ্ধান্ত নিলে, তা সময় ও প্রেক্ষাপট বিবেচনায় মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে ধনী-সম্পদশালীদের সম্পদ পুনর্বণ্টন করে তা শ্রেণি মইয়ের নিচের দিকে প্রবাহিত করা সরকারের মূল লক্ষ্য হতে হবে।
এই কাজে প্রধানতম পথ-পদ্ধতি হবে যথেষ্ট বেশি হারে সম্পদ কর আরোপ, অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর আরোপ, পাচারকৃত অর্থ উদ্ধার, কালোটাকা উদ্ধার। সরকার কি সেটা করবে, তা আগামী বাজেটেই পরিষ্কার হবে। কিন্তু উঠন্তি মূলো যেমন পত্তনেই চেনা যায় তেমনি আকস্মিক ভ্যাট বাড়ানোর সিদ্ধান্তে সরকার কী করতে পারে, তা হয়তো অনুমান করাই যেতে পারে।
পরিশেষে বলতে হয়, বাংলাদেশের মতো দারিদ্র্যনির্ভর হতভাগ্য দেশগুলোর শাসকগোষ্ঠী, তা সে জনপ্রত্যাশা ধারণকারী হোক আর না-ই হোক বিশ^ব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের মতো ঋণের কারবারিদের পছন্দমতো মূল্য সংযোজনকারী করের মতো পরোক্ষ কর বেশি হারে প্রচলনকেই বেশি পছন্দ করে। কারণ, ধনী-দরিদ্রনির্বিশেষে সবাইকেই একই দ্রব্যের ওপর একই হারে করটা দিতে হয়। ভ্যাট সবাইকেই একই হারে দিতে হয় বলে রাষ্ট্রের করের ভিত্তি চিত্রটাও প্রশস্ত হয়। অর্থ কামাই হয় সহজে। আর বিশ^ব্যাংক-আইএমএফের এই কর পছন্দের মূূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, বেশি আহরণ হলে তাদের ঋণের ব্যবসা ভালো চলে। আরও ঋণ দেওয়া সহজ হয় ফেরত পাওয়া যায় বলে। শাসনক্ষমতায় অযাচিত হস্তক্ষেপ করা তাদের উপরি আয়।
কিন্তু দিনশেষে এই কর তো বৈষম্যই বাড়ায়, যাতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিত্তশালী ধনী ছাড়া আর সবাই। ধনীদের পরোক্ষ কর বা ভ্যাট বৃদ্ধিতে লাভ হলো, নতুন সৃষ্ট বৈষম্যমাত্রা-উদ্ভূত সম্পদের ভাগ তারাই সবার আগে পায়। এ কারণেই প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ করকে যথাক্রমে একই মায়ের সৎ ও অসৎ সন্তান অভিহিত করা হয়। প্রত্যক্ষ কর যার ওপর ধার্য হয়, সে-ই কেবল দেয়। অন্যদিকে, ভ্যাটের মতো বদ বা পরোক্ষ কর যার ওপর চাপানো হয়, সে তা নিরীহ অন্য কারও ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়।
বিক্রয় কর, উৎপাদন কর, আমদানি শুল্কের মতো পরোক্ষ করের কিছু ন্যায্যতা থাকলেও ভ্যাট বা মূল্য সংযোজন কর যে খুবই অন্যায্য-অন্যায় কর, তা কলাগাছকে নিন্মোক্ত হিসাবটা দেখালেও বুঝবে। যেমন ‘ক’-এর আয় মাসে ২০,০০০ টাকা, আর ‘খ’-এর আয় মাসে ১ লক্ষ টাকা। কিন্তু বাজারে গিয়ে ‘ক’ ও ‘খ’ কোনো একটি জিনিস কিনে যদি ১০০০ টাকা ভ্যাট দেয়, তাহলে সেটা হবে ‘ক’-এর আয়ের আয়ের ৯ শতাংশ আর ‘খ’-এর আয়ের ১ শতাংশ। অর্থাৎ ক খ-এর চেয়ে ৫ গুণ কম আয় করলেও ভ্যাট দিচ্ছে সমানে সমান। এর আরও সহজ মানে হচ্ছে দুজনের মধ্যে আয়বৈষম্য ছিল ৫ গুণ, আর ভ্যাটের মাধ্যমে দুজনকে সমান কর দেওয়ায় বৈষম্য আগের আরও চেয়ে বাড়ল।
লেখক : অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়